- সেলিম রেজা নিউটন
সম্পাদকীয় নোট: এই প্রবন্ধ মানুষ নেটওয়ার্ক আয়োজিত বিশেষ আলোচনা সভার অডিও-অনুলিপি। বিষয়: ‘শিক্ষায়তনিক স্বাধীনতা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার এবং শিক্ষক ও ছাত্র-রাজনীতি প্রসঙ্গ’। তারিখ: ২০ মে, ২০০৭, রবিবার, বিকাল সাড়ে ৫টা। স্থান: ১২৩ গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রবীন্দ্রভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল যোগাযোগ, (সম্পাদক: ফাহমিদুল হক, আ-আল মামুন) সংখ্যা ১০, জানুয়ারি ২০১১-তে। যোগাযোগ এর পিডিএফ সংস্করণ যোগাড় করে দেয়ার জন্য ইস্ক্রার প্রতি কৃতজ্ঞতা।
বিশেষ পরিস্থিতি: মহা জরুরি অবস্থা
সমবেত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর, আমাদের ‘মানুষ অধ্যয়ন ক্লাস’-এর কাজ শুরু করতে যে একটু দেরি হলো, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। অনেক দিন আমাদের অভ্যাস নাই তো, অনভ্যাসের কারণেই মনে হয় আজকে একটু দেরি হয়ে গেল। চাবির জন্য,১ আর কোনো কারণে নয়। আমরা সবাই যথাসময়ে উপস্থিত ছিলাম, এবং আপনারাও অনেকেই যথাসময়ে উপস্থিত ছিলেন, এবং আমরা ঠিক পাঁচটা তিরিশেই শুরু করে দিতাম। সেটা আর বলে কী লাভ? আমাদের তো কিছুক্ষণ দেরিই হলো। দেরি হলেও আমরা শুরু করতে পারলাম, এবং ‘অন্য কোনোরকম বিঘ্ন’২ যে ঘটল না, এখনও পর্যন্ত যে ঘটে নাই, তার জন্য বহুৎ শুকরিয়া।
আমরা এখন আমাদের দেশে নানান রকম জায়গা থেকে যে কথাটা ঘনঘনই শুনছি এবং নিজেরাও হাড়ে-হাড়ে, অন্তরে-অন্তরে টের পাচ্ছি, সেটা হলো: ‘দেশ এশটি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে’। আমাদেরকে বারবারই মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে আমরা একটা ‘বিশেষ পরিস্থিতি’র মধ্যে আছি। তো, এরকম ‘বিশেষ’ পরিস্থিতির মধ্যে অনেক কিছুই আমাদের ‘বিশেষ’ মনোযোগে আসা দরকার এবং সেই জায়গা থেকে আমরা দীর্ঘ দিন ধরেই, গত কয়েক মাস ধরেই, ক্রমাগত তাগিদ বোধ করে যাচ্ছি যে আমাদের কথাবার্তা বলা দরকার।

বকেয়া আলোচনা
আজকে যে বিষয় আমরা ঠিক করেছি, ‘পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার: শিক্ষক আর ছাত্র-রাজনীতি প্রসঙ্গ’, এই বিষয়ে কথা বলাটা আমাদের আসলে বকেয়া হয়ে আছে। আমার বিবেচনা তাই। এট দীর্ঘ দিন ধরে ‘ডিউ’ হয়ে আছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কারের প্রশ্ন শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার বা সামগ্রিকভাবে সংস্কার-কর্মসূচির অংশ হিসেবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের কথা বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই জায়গা থেকেই যে আমরা আজকের আলোচ্য বিষয় ঠিক করেছি, তা কিন্তু না। আমাদের দিক থেকে বরঞ্চ এটা দীর্ঘ দিনের বকেয়া আলোচনা। এরকম আরও অনেক বকেয়া আমাদের আছে, যে বকেয়াগুলো সামনে আমাদের ধীরে ধীরে, অন্তত আমার দিকে থেকে, শোধ করতে হবে। প্রচুর বকেয়া আলোচনা, বকেয়া প্রবন্ধ- এগুলো আমাকে খালাস করতে হবে। তারই অংশ হচ্ছে এইটা।
অনেক দিন ধরেই ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ভালো না’, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান কিছু নিয়ে ভাবা দরকার’, ‘ছাত্র-রাজনীতি এবং অনেক রকম কর্থাবার্তা আমরা শুনে আসছি। আমাদের নিজেদের দিক থেকেও অনেক রকমের চিন্তা-আমাদের পুরানো অভিজ্ঞতা থেকেও- সেগুলোও ছিল। যে কারণে, আমাদের দিক থেকে আমরা এই নিয়ে কথাবার্তা বলব আবার অনেক বিষয়ের পাশাপাশি-আরও অনেক বিষয়ের মতোই-এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, স্বাভাবিক হলেও আমার দিক থেকে বলতে পারি যে আমার নিজের পারিবারিক/ব্যক্তিগত বিভিন্ন রকমের কারণে আমি আলোচনাগুলো তুলে ধরতে পারি নি। বা, আমাদের বন্ধুবান্ধব যাঁরা, আমরা যারা অনেক দিন ধরেই নানান অর্থে এক সঙ্গে চলাফেরা করি, এক সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি, কাজকর্ম করি, বা চেষ্টা করি করার, তারা নানান কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে পেরে উঠি নি। আমার মনে হচ্ছে যে আমরা হয়তো এই পেরে ওঠা শুরু করলাম। কে জানে? দেখা যাক, সামনের দিনগুলোতে আমরা এটা চালিয়ে যেতে পারি কিনা।
মানুষ নেটওয়ার্ক
আমরা যারা আজকে আলোচনা শুরু করছি- ‘মানুষ নেটওয়ার্ক’ – এটা কোনো সংগঠন না। এটা কোনো দল না। এটা কোনো পলিটিক্যাল পার্টি না। এটা কোনো সংস্থা না। এটা কোনো অর্থেই কোনো সংগঠন না। এটা অনেকগুলো লোকের একটা নেটওয়ার্ক মাত্র: যোগাযোগ, স্রেফ যোগাযোগ, আর কিছু না। আমাদের কোনো মেনিফেস্টো নাই, আমাদের কোনো ঘোষণাপত্র নাই। কিন্তু, আমাদের নানান রকম সমঝোতা আছে। বোঝপড়া আছে। এবং সবচাইতে বেশি আছে বৈচিত্র্য। আলাদা আলাদা রকমরে চিন্তুা, মত-পার্থক্য। এবং সেগুলো নিয়েও এক সঙ্গে কাজ করা যে যায়- এইটা চর্চা করাটা আমদের প্রধান চ্যালেঞ্জ। এবং সেখানে আমাদের আলাদা আলাদা মত যত বেশি করে আসবে, তত বেশি করে আমরা সবাই উপকৃত হব। সুতরাং, এইটাকে কোনোভাবেই কোনো পলিটিকাল/নন-পলিটিকাল পার্টি হিসেবে বা অর্গানাইজেশন হিসেবে দেখার কোনো সুযোগ নাই। এরকম কোনো সংগঠন করা যে ভালো বা খারাপ- সে জায়গা থেকে কথাটা বলছি না। আমরা যেটা না, আমরা সেটা বলে রাখলাম। আমরা যদি ভবিষ্যতে অন্য কিছু হই কখনও (‘মানুষ নেটওয়ার্ক’ নামে কিনা বা অন্য নামে কিনা, সেটা অন্য কথা, কাল্পনিক কথা) সেটা তখন দেখা যাবে, সেটা তখন বলা যাবে।

আলোচনার পদ্ধতি: প্রকাশ্যতা এবং স্বাধীনতা
তো, বকেয়া আলোচনা আমরা আজকে শোধ করতে নেমেছি, এটা যেমন ঠিক, আবার সাম্প্রতিক পরিস্থিতির একটা উসিলা আছে, এটাও ঠিক। অজুহাত হিসেবে এই মুহূর্তে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা না বলাটা অন্যায় হবে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি হয়তো আমাদেরকে দ্রুত এ ধরনের একটা আলাপ করতে বাধ্য করল।
আজকের আলোচনা একটু তাড়াহুড়ো করে আয়োজন করা- আমার দিক থেকেও এবং আয়োজকদের সবার দিক থেকেও। তার কারণ হচ্ছে ২৩ তারিখে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হবে [গরমের ছুটির জন্য]। তো, বন্ধ হওয়ার আগেই আমরা একটা কিছু আলোচনা করি। কোনটা নিয়ে করা যায়, কোনটা নিয়ে এক্ষুণি কথা বলা যায়, কোনটা নিয়ে কথা বলাটা সহজ, অনেক প্রস্তুতি লাগে না- সেই রকম জায়গা থেকে আমরা এই তারিখ, আজকের তারিখ, তাড়াহুড়ো করে ঠিক করেছি, এবং আজকের আলোচ্য বিষয় তাড়াহুড়ো করে ঠিক করেছি। সেটাও হয়তো একটা কারণ, যে কারণে আজকে হয়তো সামান্য বিঘ্ন ঘটল, টেকনিকাল বিঘ্ন ঘটল, শুরু করতে।
আমার দিক থেকে আলোচনাটা হয়ে যাবার পরে আপনারা যে কেউ, যাঁরা এখানে আছেন, প্রশ্ন করবেন, বা যদি কিছু বলার থাকে, বলবেন। এখানে [মঞ্চে] এসেই বলবেন। প্রশ্নটাও এখানে এসেই করবেন। কারণ, আমাদের সমস্ত আলোচনাই, আমার এবং আপনাদের, প্রশ্ন এবং আলোচনাই রেকর্ডেড থাকবে। এখানে [ডায়াসে] তিনটা রেকর্ডিং মেশিন কাজ করছে। সাংবাদিকরা যদি কেউ থাকেন, কিংবা অন্য কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ৩ যদি থাকেন, তাঁদের কাছেও অনুরোধ যে আমাদের এই আলোচনাকে ‘রেফার’ করার জন্য দরকার যদি পড়ে, যেকোনোরকমভাবে আমাদের আলোচনার বরাত দিয়ে যদি কিছু বলা লাগে, তো দয়া করে আমাদের কাছে চাইবেন। আমরা আমাদের গোটা আলোচনার সিডি দিয়ে দিব। গোটাটাই উন্মুক্ত। এখানে লুকানোর কিছু নাই এবং আড়াল করার কিছু নাই। যে কারও যেকোনো প্রয়োজনে যদি আজকের আলোচনার প্রয়োজন পড়ে, এর বরাত দিয়ে কিছু বলার, কিছু লেখার, কোথাও কোনো প্রতিবেদন জমা দেওয়ার দরকার যদি পড়ে, তাহলে আমাদের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ সিডিটা নেবেন। দয়া করে আমাদের নাম দিয়ে নিজেদের মতো করে কোনো রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবেন না।
একই সঙ্গে, একদম শুরুতেই বলে নেওয়া দরকার আমার দিক থেকে: কি বর্তমান সরকার, কি আমাদের সুশীল সমাজ, কি তাঁদের মিডিয়া-পার্টনারগণ কিংবা রাজনৈতিক মহল (তার মানে, রাজনৈতিক দল এবং শিক্ষার্থী-সংগঠনগুলো এবং শিক্ষক-রাজনীতির নেতৃবৃন্দ বা তাঁদের দলীয় অবস্থান)- এই সব কোনো কিছুর সঙ্গেই আমার এবং আমাদের অবস্থান মিলবে না। কারণ, কোনো দলীয় অবস্থান থেকে বা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীগত অবস্থান থেকে আমরা এখানে কথা বলছি না। নিজেদের মতো করে চিন্তা করেই এখানে আমরা কথা তুলছি।
এই ‘বিশেষ অবস্থায়’, এই বিশেষ সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে, এখানে একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যে বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীন চিন্তাভাবনা করার জায়গা। [বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাই পারেন সত্যিকারের স্বাধীন অবস্থান নিতে: সমাজ এটা আমাকে দিয়েছে।] হাজারটা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমার সমাজ এবং বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার ষোলআনা সুযোগ ও অধিকার দিয়েছে, যে স্বাধীনতার চর্চা আমরা খুব কমই করে থাকি। আজকে আমার অবস্থান ঐ স্বাধীন অবস্থান থেকেই কথা বলার। অর্থাৎ, চিন্তা, মতামত আর প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে, স্বাধীন অবস্থান থেকে, নিজের কথা প্রকাশ করা। [স্বাধীনতা ছাড়া, স্বাধীন চিন্তা ছাড়া আজকে আমার আর কোনো চিন্তা নাই।]

ঢালাও বিবৃতি এবং ধামাধরার অভ্যাস
আজকেই প্রথম আলো পত্রিকায় একটি লেখা বেরিয়েছে। তকদির হোসেন মনে হয় তাঁর নাম। পরিচয় দেওয়া আছে : ‘কলাম লেখক’। তকদির সাহেব বলেছেন, যে নির্মম সত্য প্রধান বিচারপতি মহোদয় বিচারবিভাগ সম্পর্কে উচ্চারণ করেছেন, শিক্ষা সম্পর্কে সেই নির্মম সত্য উচ্চারণ করবেন কে? (তকদির হোসেন, ২০০৭) নোয়াখালির আইনজীবী সমিতিতে আমাদের মহাপ্রলয় ঘটেছে সেটা তাঁরাই ভালো জানবেন। সেটা আমি অন্ততপক্ষে খুব ভালো জানি না। কিন্তু আমাদের বিচারবিভাগ কিভাবে চলে সেই খসড়া আন্দাজ বাংলাদেশে প্রত্যেক মানুষেরই আছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মূর্খ-অমূর্খ সবার দিক থেকেই সেই আন্দাজ ষোলআনাই (আমার ধারণা) কাজ করে। এবং সে আন্দাজ খুব ভুল না। আলাদা করে মাইক দিয়ে বড় একজন কর্তাব্যক্তি যখন বলেছেন মহাপ্রলয় ঘটেছে, তখন সেটার বরাত দিয়ে কথা বলাটা হয়তো অনেকের জন্য সহজ হচ্ছে, কিন্তু এ ছাড়া ঐ কথার গুরুত্ব আমার কাছে কমই আছে বলে মনে হয়।
তারপর তকদির সাহেব আহাজারি করেছেন, আক্ষেপ করেছেন: আমাদের শিক্ষার অবস্থা এই, শিক্ষার অবস্থা সেই, কে এখানে হাল ধরবে, কে এখানে পরিবর্তন আনবে, কে এখানে সংস্কার করবে, কিভাবে কী হবে? এর মধ্যে যেটা লক্ষণীয় (প্রধান বিচারপতি সাহেবের বেলাতেও বটে, তকদির সাহেবের বেলাতেও বটে, এবং আরও অনেকেরই আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা এই বৈশিষ্ট্যই প্রধানত দেখি), সেটা হলে, ঢালাও একটা বিবৃতি দেওয়া: ‘মহাপ্রলয় ঘটে গেছে’। [পত্রিকার শিরোনামেরও স্বভাবই এইটা, এরকম ঢালও বিবৃতি]। আর তকদির সাহেব চাচ্ছেন, আমরা কেউ একজন মহাকর্তাব্যক্তি শিক্ষপ্রতিষ্ঠান থেকে বলি যে এখানেও মহাপ্রলয় ঘটেছে। এটা আর বলার কী অপেক্ষা রাখে? এখন সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় মিলে যদি একজন ভিসি থাকতেন (প্রধান বিচারপতির মতো), বা একজন চ্যান্সেলর যদি নিয়মিত কথা বলার অভ্যেস রাখতেন, তাহলে তিনি বললে হয়তো বলতেন। কিন্তু কথা তো বলার কিছু অপেক্ষা রাখে না। আমরা জানি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা কী! শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা ভালো না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা খুবই বেকায়দা।
কিন্তু মহাপ্রলয় ঘটেছে বললে মনে হয়, আচমকা এক দিন কোনো প্রলয় ঘটেছে। তো আচমকা, এক দিন, কোন প্রলয় বিচারবিভাগে ঘটেছে কিনা জানি না। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক দিনে কোন প্রলয় ঘটে নি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গত চল্লিশ বছর ধরে, আরও অনেক আগে থেকে আসলে, ক্রমাগত প্রলয়াকারে প্রক্রিয়া তিল তিল করে ঘটে চলেছে। সুখের কথা যে অনেক দিন পরে হলেও এখন এসে অনেক মানুষ এ সমস্ত সমস্যা নিয়ে কথা বলছেন। খুবই ভালো। কথা বলা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার প্রয়োজন। কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু ঢালাও বিবৃতি প্রয়োজন না। ঢালাও বিবৃতি আমাদেরকে সমস্যা বুঝতে সাহায্য করে না।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাটা কোথায়? ঠিক কোন কোন জায়গায়? সেগুলি যদি আমরা সুনির্দিষ্ট করে বলা অভ্যাস না করি তাহলে ‘প্রলয় ঘটে গেছে’ বলা, আর ‘হায় হোসেন, হা হোসেন’ করা, হা-হুতাশ করা- এর কোনো মানে নাই। আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে বলা শুরু করতে যে কোন কোন জায়গাতে আমাদের সমস্যা আছে, এবং সেইখানে কী করলে পরে সমস্যাগুলোর সমাধান আশা করা যায়। ফলে, এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যদি কোনো উদ্যোগ থাকে, আমরা সাধুবাদ জানাই, স্বাগত জানাই। এবং যাঁরাই সংস্কারে ধাবিত, তাঁদেরকেও স্বাগত জানাই। সংস্কার এখানে হোক। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কথা বলাটা আমাদের শুরু করা দরকার।
আমি চেষ্টা করব আজকে সুনির্দিষ্টভাবে কতকগুলো পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে। এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট ছুটে যাবে। আমার আলোচনা থেকে বাদ পড়ে যাবে। তার একটা কারণ হচ্ছে যে আলোচনাটা অতখানি গুছানো সম্ভবত হচ্ছে না। যেগুলো ছুটে যাবে সেগুলো আপনারা বলবেন। যেগুলো ছুটে যাবে সেগুলো সামনের দিনে আমি আরও গুছাবো। আলোচনা তো আর শেষ হয়ে যাচ্ছে না। ফলে, আরও গোছগাছ করে কথা বলা, আমাদের সামনের দিনগুলোতে, যাবে হয়তো। এবং দরকার পড়বে। যতই দিন যাবে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কথা বলা আমাদের দরকার পড়বে।
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তকদির সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই এই পয়েন্টে যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরাই কথা বলুন বেশি। শুধু যদি বাইরের লোকেরা কথা বেশি করে বলেন সেটা ভালো নয়। আর, বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা, শিক্ষকেরা- ধামাধরাটা তাঁদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। এখনও বোঝা যাচ্ছে না, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সরকারের ধামাটা কোথায়। যদি ভালো করে বোঝা যায়, তাহলে অনেকেই ধামাটা ধরে ফেলার জন্য এই মুহূর্তেই রেডি আছেন। তো, তাঁরা যদি ধামাধরার জন্য তক্কে তক্কে থাকে (‘ধামাটা কোন জায়গায়, খুঁজে পেলেই ধরে ফেলব’), তাহলে আমাদেরকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না কেউ।
ধামাধরার অভ্যাসটা আমাদেরকে, বিশ্ববিদ্যালয়কে, বাদ দিতে হবে। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের দিক থেকেই কথা বলাটা অনেক বেশি করে দরকার। তাহলে গোটা সংস্কার কার্যক্রম যদি কিছু থাকে, যদি কিছু শুরু হয়, সেখানে আমরা আমাদের অবস্থানটাকে অনেক পরিষ্কার করতে পারব। আমাদের অবস্থান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটির অবস্থান। শিক্ষকদের কমিউনিটি। শিক্ষার্থীদের কমিউনিটি। আমি যেমন শিক্ষকদের মেম্বার গত ১২ বছর ধরে, এটা আমার সত্তার অংশ হয়ে গিয়েছে, সেরকমই তার আগের ১২ বছর আমি শিক্ষার্থী-কমিউনিটির মেম্বার ছিলাম। এবং সেই স্মৃতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীজীবনের স্মৃতি আমার মনে হয় আমার এই শিক্ষক-সত্তার চাইতে আরও বেশি পাওয়ারফুল। ফলে, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয় সত্তার জায়গা থেকে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রদায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবার, তার স্বার্থ, তার মঙ্গল, তার ভালোমন্দ, সেই জায়গা থেকে আমার সীমিত অভিজ্ঞতায়, সীমিত বুদ্ধি বিবেচনায় যা বুঝি সেই কথাগুলিই বলার চেষ্টা করব। ভুল হলে, বাদ পড়লে আপনারা বলবেন।

উপাচার্য, আমলাতন্ত্র, রাষ্ট্রের শুঁড়
একদম প্রথমেই যদি বলতে চাই, বলতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসন নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলাতন্ত্র। এটা হচ্ছে নাটের গুরু। এবং সেই আমলাতন্ত্রেও গুরুদের গুরু হচ্ছেন ভাইস-চ্যান্সেলর। তাঁর সই ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুই হয় না। তাঁর সই ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো প্রকাশনা বের হয় না। এবং তাঁর প্রধান অতিথিগিরি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো অনুষ্ঠান হয় না। এবং এই আমলাতন্ত্রের পিঠে হাত না বুলিয়ে ঝটপট কাজ হতে চায় না। অত তলায়, তত তলায় গিয়ে প্রশাসনিক ভবনের আমলাদের, কেরানিদের পিঠে হাত বুলাতে হয়। পূর্ণাঙ্গ প্রফেসর- তাঁকে কেরানির পিঠে হাত বুলাতে হয়: ‘ভাই, আমার ফাইলটা’, ‘ভাই, আমার ঐ কাজটা’, ‘ভাই, আমার দরখাস্তটা’, ‘একটু ঠেলেন’, ‘একটু আগান’, ‘একটু পাস করেন’। এবং ঐ আলটিমেটলি ভাইস-চ্যান্সেলরের সই লাগবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোনো কাজ সম্ভব না (কল্পনীয় এবং অকল্পনীয়) যেটা ভাইস চ্যান্সেলরের, আমি রিপিট করছি, ভাইস চ্যান্সেলরের সিগনেচার ছাড়া হয়।
এই হলো বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসন। এমন ধরনের একটা প্রশাসন, যার হাতে সব ক্ষমতা। সিন্ডিকেট বলেন, সিনেট বলেন, শিক্ষক-সমিতি বলেন, ডিন বলেন, ছাত্র-সংগঠন বলেন, কালচারাল সংগঠন বলেন, সবকিছু গিয়ে কালমিনেট করবে, কেন্দ্রীভূত হবে, ঐ ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে; তাঁর নেতৃত্বে যে আমলাতন্ত্র আছে (কেরানিবাহিনী, অফিসারকুল আছেন), তাঁদের কাছে। আমি কিন্তু ‘ব্যক্তিগতভাবে ভাইস চ্যান্সেলর খারাপ’, ‘ব্যক্তিগতভাবে আমলারা খারাপ’, ‘ব্যক্তিগতভাবে কেরানিরা খারাপ’, এ রকম কথা বলার মতো মূর্খতা প্রদর্শন করার চেষ্টা করছি না। আমি বলছি কাঠামোটার কথা। এই কাঠামোটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতার প্রাণভোমরা। যে বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যে বিশ্ববিদ্যালয় অচলাবস্থায় আছে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থবিরতার প্রাণভোমরা হচ্ছে এইটা।
তো, ওনারা যা যা করতে পারেন, এই ধরনের কাঠামো হলে যা যা হওয়ার কথা, তাই হচ্ছে। স্বজনপ্রীতি। দুর্নীতি। শিক্ষকদের/শিক্ষার্থীদের ওপরে নানান ধরনের চাপ প্রয়োগ করা। এবং ঐ ভাইস-চ্যান্সেলরের নিজেরই নানানভাবে চাপগ্রস্ত হওয়া। সরকারের দিক থেকে চাপগ্রস্ত হওয়া। ছাত্র-সংগঠনের দিক থেকে চাপগ্রস্ত হওয়া। কর্মচারীদের দিক থেকে চাপগ্রস্ত হওয়া। যত রকম চাপ দেওয়ার বাহিনী আছে, সবাই ভিসিকে চাপ দেবে। আর, ভিসির যত ক্ষমতা আছে, সেই সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে উনি আবার চাপ দিবেন নিচের দিকে। প্রফেসর থেকে আরম্ভ করে পিয়ন সবাই ওনার চাপে অস্থির হয়ে থাকবে- উনি যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন।
হ্যাঁ, এটাকে ‘ক্ষমতায় থাকা’ বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষকরা এ ভাষাতেই কথা বলেন।৪ পিয়নরাও এই ভাষায় কথা বলেন। ‘অমুক ভিসির আমলে’ (আইয়ুব খানের আমলে), ‘তমুক ভিসির আমলে’ ইত্যাদি। যত দিন উনি ‘আমলে’ আছেন, তত দিন উনি গাড়িতে আছেন। তত দিন তার চারি পাশ দিয়ে বহুত লোক আছে। উনি যদি মর্নিং ওয়াকে বের হন (আমি নিজের চোখে দেখেছি, আপনারাও দেখবেন), একটা বিরাট বাহিনী সঙ্গে হাঁটবে। কিন্তু, যেদিন উনি ভিসি আর নাই, যেদিন ওনার আমল শেষ, পরের দিন উনি ‘প্যারিস রোড’ দিয়ে একা একা। সঙ্গে একজন পিয়নও থাকবে না। কেউ থাকবে না। তখন তিনি রিকশায় যাবেন। রিকশায় একা। সন্ধ্যারাতের আবছা অন্ধকারে কিংবা মর্নিং ওয়াকে হাঁটবেন, তষনও একা একা। বন্ধুবান্ধবও সঙ্গে নাই। [ভিসিদের মনে হয় ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধব থাকে না]। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এ রকম অনেক ‘মৃত উপাচার্য’কে দেখেছি এবং জীবিত উপাচার্যকেও দেখেছি। এর কারণ হচ্ছে ঐ যে: সমস্ত ক্ষমতার একটা কেন্দ্র, একটা আমলাতন্ত্র, যার মাথা ভাইস-চ্যান্সেলর। এই কাঠামোর জন্য এরকমটা হয়েছে। ওখানে যদি আপনি আমাকেও ভিসি বানিয়ে দেন, একই অবস্থা হবে। অন্য কিচ্ছু আমার পক্ষে করা সম্ভব হবে না। বড় জোর আমার পক্ষে চিৎকার করে বলা সম্ভব হবে: ‘বাঁচাও, আমি ভিসি হতে চাই না’। কিছু করা সম্ভব হবে না। যদি কাঠামো এইটা থাকে।
এই কারণে প্রশাসন এবং আমলাতন্ত্র-এইটা হচ্ছে সবার আগের কথা। আর, এখানে অন্য কী কী অসুবিধা হয়, এটা আপনারা আমার থেকে ভালো জানেন। সার্টিফিকেট তোলা নিয়ে সমস্যা। শিক্ষার্থীদের হলের সমস্যা। সিট পাওয়া নিয়ে সমস্যা। ভর্তি হওয়ার সমস্যা। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সমস্যা। সেশন জ্যামের সমস্যা। পরীক্ষা না হওয়ার সমস্যা। কত রকম! মাস্টাররা ক্লাস নিবেন না, কিচ্ছু বলা যাবে না। মাস্টাররা পরীক্ষার দিন উপস্থিত থাকবেন না, অন্য শহরে থাকবেন, অন্য দেশে থাকবেন, আন-নোটিশড। এভরিথিং। হোয়াটএভার ইউ ক্যান থিংক, অর আন-থিংক, ইজ পসিবল আন্ডার দ্যা ভাইস-চ্যান্সেলর, আন্ডার দিস অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার। দ্যাট ইজ দ্যা পয়েন্ট।
এটা একটা মহাক্ষমতাশালী আমলাতন্ত্র। মহাকেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র। মহা-হায়ারার্কিকাল। উচ্চ-নিচ ক্রমবিন্যাসওয়ালা। হায়ারার্কি মানে কে না জানে। বাংলায় বলি। বাংলায় কমই জানি আমরা। হায়ারার্কি মানে হচ্ছে: সবাই সবার বস। সবচেয়ে তলায় যিনি আছেন, তিনিও বস। কারণ তাঁর তলেও তো লোকজন আছেন। খুঁজলে পাবেন। আর সবচাইতে উপরে যিনি আছেন, উনি মহা-বস। এটা এক দিকে: বসের উপরে বস, তার উপরে বস, তার উপরে বস। আরেক দিকে: সবাই গোলাম। সবচাইতে উপরে যিনি আছেন, উনিও গোলাম। ওনার উপরেও বস আছে। এবং উনি থেকে আরম্ভ করে নিচের সবাই গোলাম। একদম তলা পর্যন্ত ঠেকবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাস পর্যন্ত ঠেকে যাবে, আমার ধারণা। এই হচ্ছে স্ট্রাকচার। সুপার্ব আমলাতান্ত্রিক স্ট্রাকচার। এই কাঠামোটা অ্যাকচুয়ালি রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর আবশ্যিক অঙ্গ। রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে এই কাঠামো ‘হেব্বি সে’, জুত করে, আটকানো আছে: স্ট্রং নাটবল্টু দিয়ে। কিংবা বলতে পারেন: অভ্যাসের স্কচটেপ দিয়ে কোনোরকমভাবে আটকানো আছে। কিন্তু, স্বার্থের ইন্ধনে এই বন্ধন একেবারে পবিত্র এবং অটুট। অটুট – কিন্তু বেকায়দা হলেই ছুটতে সময় লাগে না ঐটা। লাগবেও না। অতীতে আমারা অনেক বার দেখেছি।
রাষ্ট্রের দিক থেকে দেখলে, শিক্ষা-মন্ত্রণালয়, মঞ্জুরি কমিশন এগুলি হচ্ছে রাষ্ট্রের শুঁড়। এইসব শুঁড়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আমলাতন্ত্র আটকানো। মঞ্জুরি কমিশনের আমলাতন্ত্র, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলাতন্ত্র, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলাতন্ত্র পরস্পরের সাথে আটাচড। একেবারে জুত-মতো অ্যাটাচড। এই আলমাতন্ত্র ঐ আমলাতন্ত্রের এক্সটেনশন মাত্র।
রাষ্ট্রের একটা বড় শুঁড় হলো ভিসি-নিয়োগ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি-নিয়োগ করবেন আমাদের সরকার বাহাদুর। সুতরাং, ভিসি যেমন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে সমস্ত কিছুর গুরু, ওস্তাদ, বস; তেমনি তাঁর বস হলেন সরকার; তাঁর চেয়েও বিগ বস। কেননা, তুমি যেই হও, এবং তুমি শিক্ষকদের যত ভোট পেয়েই নির্বাচিত হও না কেন, যে তিনজন নির্বাচিত হবেন সেখান থেকে রাজনৈতিক দল এবং সরকার একজনকে ‘পছন্দমতো’ মনোনয়ন দেবেন। ঐ তিনজন নির্বাচিত হওয়ার আগে আবার তিরিশ জনের মধ্যে জটিল কনুই-চালাচালি চলবে।
আপনি আমাদের মহান মিছিলগুলো দেখবেন। ছোটবেলায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিলের ছবি দেখতাম পত্রিকায়। দেখতাম সাংঘাতিক গতিময়। সবাই দৌড়াচ্ছে। পত্রিকায় কখনও কখনও লেখা হতো ‘জঙ্গি মিছিল’। পরে যখন জঙ্গি মিছিলে ঢুকলাম, তখন গিয়ে দেখি ওটা আসলে কনুই-চালাচালির মিছিল। প্রথম লাইনে কারা থাকবেন, তা ঠিক করার জন্য কনুই-চালাচালি। তার জন্য নেতারা, সামনের লাইনের ‘নেতা’রা সবাই সবার কনুই ধরে আছেন, যেন কেউ কাউকে কনুই মারতে না পারেন। বছরের পর বছর ধরে আমি এই মিছিল করেছি এবং দেখেছি। এবং ‘নেতা’দের কনুইয়ের এই দেওয়াল ভেদ করে পেছনের কেউ যেন সামনে আসতে না পারে। কেন? আসলে পরে যে ফটো মিস হয়ে যাবে! সাংবাদিকদের ক্যামেরায় আমার ফটো মিস হয়ে যাবে। আর ফটোতে যদি আমি মিস হয়ে যায়, তাহলে আমার সবই শেষ: বিপ্লব শেষ, গণতন্ত্র শেষ, সমাজতন্ত্র শেষ, আমার নেতাগিরি শেষ, ফলে আমার চাঁদাবাজিও শেষ, ক্যারিয়ার শেষ, আমি ডুম।
তো, এই যে ভিসি হওয়ার জন্য তিন জনের সম্মুখ-সারি, এর পেছনে আছে এই তিনজনকে বাছাই করার জন্য পেছনের তিরিশ জনের ‘অদৃশ্য’ কনুই-চালাচালি। এই তিরিশ জনের প্যানেলে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের উপরও কিন্তু সরকারের আছর থাকবে। পলিটিকাল পার্টির আছর থাকবে: এই পার্টিরও, ঐ পার্টিরও, সেই পার্টিরও। এইসব ক্ষেত্রে ‘লেফট’- ‘রাইট’ সব সমান। রাষ্ট্রের প্রশ্নে, রাজনীতির প্রশ্নে, ক্ষমতার প্রশ্নে, হালুয়ারুটির প্রশ্নে গত ছত্রিশ বছর ধরে বাম-ডান-মধ্য-সব সমান। ভবিষ্যতে যদি আমাকে বলতে বলেন, আমি এ নিয়ে বুঝিয়ে কথা বলতে রাজি আছি। আর একটু যদি ভাবেন, আপনিও বুঝবেন। না বোঝার কোনো কারণ নাই। যাক।
তো, বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্যিকারের স্বাধীনতার পথে প্রথম সুনির্দিষ্ট সমস্যাটি তাহলে আমলাতন্ত্র। ক্যাম্পাসে এই আমলাতন্ত্রের প্রতীক বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসন। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার চিন্তাটি, ‘শাসন’ করার চিন্তার সাথে গিট্টু লেগে আছে। ভিসিগণ এখানে ‘ক্ষমতা’য় থাকেন, তাঁদের কারও ‘আমল’-এ ‘প্রশাসন’ ভালো চলে, কারও আমলে খারাপ চলে। প্রফেসরগণ এখানে ‘প্রশাসক’ হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। একেবারে আক্ষরিক অর্থেই বলছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সংক্রান্ত বিষয়-আশয় যিনি দেখেন তাঁকে বলে ‘পরিবহন প্রশাসক’, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বৃহত্তম সমাজের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের ব্যাপারগুলো যিনি দেখাশোনা করেন, তিন ‘জনসংযোগ প্রশাসন’ ইত্যাদি। পুলিশ, প্রক্টর, প্রভোস্ট, প্রশাসক, প্রফেসর এখানে প্রায়-সমার্থক শব্দগুচ্ছ। শাসন করার মনোবৃত্তিই গোটা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্রেফ একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরিণত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রশাসন রাষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকে রাজনৈতিক সূত্রে, প্রশাসনিক সূত্রে, আমলাতান্ত্রিক সূত্রে। তিনটা শুঁড় মঞ্জুরি কমিশন, একটা শুঁড় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এগুলো প্রাতিষ্ঠানিক শুঁড়। অপ্রাতিষ্ঠানিক শুঁড়ের অভাব নাই। চাপের অভাব নাই। আছরের অভাব নাই। সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের দিক থেকেই আছে। সরকার-প্রশাসন চান, ক্যাম্পাস-প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করতে। ক্যাম্পাস-প্রশাসন চান, আমাদের উপর আছর হোক, সারাক্ষণ আছর হোক; এর বাইরে যেন কিচ্ছু ঘটতে না পারে।
নেক্সট পয়েন্ট: শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া। আমার পয়েন্টগুলো খুব ধারাক্রমিক নাও হতে পারে। মানে যে পয়েন্টের পর যে পয়েন্ট আলোচনা করা উচিত, সেরকমটা নাও হতে পারে। আমি নিশ্চিত না। না হলে অসুবিধা নাই। অদল-বদল করে নিলেও পরিস্থিতি একই। তো, পরের পয়েন্টটা হচ্ছে: শিক্ষক-নিয়োগ প্রক্রিয়া।

শিল্পী: আঙ্গু ওয়াল্টার্স
দ্বৈত খাতা-পরীক্ষণ, দাপ্তরিক গোপনীয়তা ও
গোলাম-নিয়োগ: সর্বনাশের সরকারি পথ
এতক্ষণ বলেছি বিশ্ববিদ্যালয়-কাঠামোর একেবারে মাথার কথা: প্রশাসন। এবার বলছি গোড়ারও নিচের কথা, যা চট করে দেখা যায় না, চোখে পড়ে না। অদৃশ্য। আড়ালের জিনিস। তার নাম শিক্ষক-নিয়োগ প্রক্রিয়া। [প্রক্রিয়াগত বিন্যাস-বন্দোবস্তকে আড়াল করে স্রেফ শিক্ষক-নিয়োগ নিয়ে কথা বললে সেটা বহুল আলোচিত কিন্তু ওপরভাসা গোছের একটা জিনিসই থেকে যায়।] আর আড়ালেও ঘটনা আছে। এবং সেটাই আসল ঘটনা। আমি বলছি শিক্ষক-নিয়োগ প্রক্রিয়ার একেবারে গোড়ার ঘটনাটির কথা। আমি বলছি খাতা দেখা এবং পরীক্ষা-প্রণালির কথা। [আমি যে অর্থে বলছি, সেই অর্থে খাতা দেখা এবং পরীক্ষা-প্রণালির বিদ্যমান ব্যবস্থাটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা তো দূরের কথা,] এটা যে শিক্ষক-নিয়োগ প্রক্রিয়ার আবশ্যিক অঙ্গ, সেই উপলব্ধিটুকু আমি কাউকে কখনও প্রকাশ করতে দেখি নি। শিক্ষকতার ১৩ বছর হতে চললো আমার। এ পর্যন্ত এটা অনালোচিত।
শিক্ষক-নিয়োগ প্রক্রিয়াটা দেখেন। ব-ছ-রে-র পর ব-ছ-র ধরে চলছে। ভিসি যিনিই হন, দল যাই হোক, ‘ক্ষমতা’য় যিনিই থাকুক, লোক ভালো হোন, লোক খারাপ হোন, দলের আহ্বায়ক যিনিই হোন, শিক্ষকদের দলের কথা বলছি, তাতে কিছু যায় আসে না। শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াটায় ধীরে ধীরে একটা পচন ধরতে ধরতে ধরতে এখন এসে ছাগল, গরু, গবাদি পশু টিচার হবেন। [এমন দাঁড়িয়েছে যে: মনুষ্যত্বের অবাধ বিকাশের পথে বিদ্যমান হাজারও বাধাকে উড়িয়ে দিয়ে দ্বিপদী প্রজাতির যেকোনো সদস্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘শিক্ষক’ হতে পারেন, এটা আজ সম্ভবত সর্বজনস্বীকৃত, যদি তিনি ‘আমাদের লোক’ হয়ে থাকেন।]
আমি নিজে ‘মেধাবী’, ‘আউটস্ট্যান্ডিং’ এইসব ফালতু জায়গা থেকে কথাটা বলছি না। ‘মেধা’ কী, ‘আউটস্ট্যান্ডিং’ কী জিনিস, ‘বাইরে গিয়ে দাঁড়ানো’টাই বা কী জিনিস আমি বুঝিও না। পৃথিবীকে নাড়িয়ে দেবার জন্য পৃথিবীর ‘বাইরে গিয়ে দাঁড়ানো’র মতো একটা জায়গা আইনস্টাইনও নাকি খুঁজেছিলেন, পান নি। তিনিই যদি আউটস্ট্যান্ডিং হতে না পারেন, তাহলে আমি আর কোন কুতুব। (হাসি)। মেধা-টেধা অন্য প্রসঙ্গ। পৃথক মিথ। আইনস্টাইনের ব্রেন কী জিনিস, ঐ ব্রেন ফরমালিন দিয়ে ভিজায়ে রাখতে হয় কেন এবং ওর মধ্যে বিশেষ ‘কিছু একটা’ পাওয়া যাবে কিনা, উনি ‘মঙ্গলগ্রহের মানুষ’ ছিলেন কিনা, এবং সে কারণে ওনার ‘বুদ্ধি’ বেশি ছিল কিনা- এসব আমি বুঝি না। এই ‘মেধা’ আমি বুঝি না। এই ‘মেধা’ সায়েন্সও বোঝে না আসলে। সব মানুষের ঘিলু কমবেশি একই রকমের থাকে। সেটা অন্য প্রসঙ্গ।
কিন্তু বাস্তবিকই যাঁরা দ্বিপদী প্রাণী মাত্র, বিবর্তনসূত্রে আনুগত্য ছাড়া এবং দাসত্ব ছাড়া যাঁরা আর তেমন কিছু শেখেন নি, তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হচ্ছেন। দলে দলে। দীর্ঘ কাল ধরে চলছে এই নিয়ম। তো, এই শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াটা কী? প্রক্রিয়াটা এরকম: আমার পছন্দের লোককে আমি নিয়োগ-বোর্ড থেকে নিয়োগ দেব। নিয়োগ-বোর্ডে থাকব ‘আমরা আর মামুরা’। আর নিয়োগ-বোর্ডে যাঁরা আসবেন পরীক্ষা দিতে, তাঁরাও ঐ ‘আমরা আর মামুরা’ই। কিন্তু, আপনারা এবং আপনাদের মাতুলবংশই যে এসব জায়গায় থাকবেন, সেটা আপনি প্রত্যেকবার কনফার্ম করেন কিভাবে? চিন্তা করে দেখেন; এইটাই হচ্ছে গোড়ার জায়গা।
আপনি কনফার্ম করেন কিভাবে যে নিয়োগ-বোর্ডে যাঁরা হাজির হচ্ছেন, মানে যাঁরা শিক্ষক পদের জন্য নিয়োগ-অভিলাষী, তাঁরা সবাই প্রায় আমাদের আর মামুদের লোক হবেন, তা কেমন করে হয়? প্রায় সবসময়? ব্যতিক্রম তো ব্যতিক্রমই। বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া, এ্যাকসিডেন্ট ছাড়া এটা আমরা কনফার্ম করি কেমন করে যে সাক্ষাৎকার-সভায় শুধু ‘আমাদের আর মামুদের’ লোকেরাই থাকবেন, আর আমরা শুধু বেছে নেব: কোন ছাগলটা সেরা ছাগল? এটা কেমন করে পারি?
পারি, তার কারণ হচ্ছে, যাঁরা যাঁরা ফার্স্ট-ক্লাস পেয়েছেন, তাঁরা সবাই ‘আমাদের লোক’। কোনো না কোনোভাবে। এই দলের, না ঐ দলের, না হয় সেই দলের। সবাই প্রায় ছাগল-বংশীয় লোক। দাস-বংশীয় লোক। অন্য বংশের কেউ এখানে থাকবেন না। এঁরা ছাড়া আর কেউ ফার্স্টক্লাস পাবেন না। মোটামুটি গ্যারান্টিড। আমোঘ।
আমি যা বলব একটু গড়ে ধরে নেবেন। একেবারে হানড্রেডে হাসড্রেড ধরে নেবেন না। সামান্য আসমানী ব্যতিক্রম দু-একটা কল্পনা করে নেবেন যা ঘটতে পারে। ঘটেও। এবং ঐটুকু ব্যতিক্রম যে আছে, সেটা খুবই মহান। সেই ব্যতিক্রমটুকুই মহান। এবং সেটা যে আছে তার কারণ হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়টা এখনও সবকিছুর পরেও স্বায়ত্তশাসিত। তার জন্য একশতে একশ হওয়া যায় নি। নিরানব্বই, সাড়ে নিরানব্বই, উন নিরানব্বই- এগুলোতে আছে।
আচ্ছা। তো, তার মানে আপনাকে ফার্স্ট-ক্লাস কনফার্ম করতে হবে।
সামনের বেঞ্চগুলিতে লোকজন বইসেন কিন্তু। এগুলা রিজার্ভড না। এগুলা ভাইস চ্যান্সেলরদের জন্য রিজার্ভড না (দর্শক-শ্রোতাদের হাসি) বা অন্য কোনো কর্তাব্যক্তিদের জন্যও রিজার্ভড না। পেছনের দিকে ভরে গেলে সামনের দিকে চলে এসেন।
তো, সবাইকে যে ফার্স্ট-ক্লাস দিব আমরা, ফার্স্ট-ক্লাস দেওয়ার প্রক্রিয়াটা তাহলে এমন হতে হবে যে ‘হিসেবের বাইরে’ কেউ যেন ফার্স্ট-ক্লাস না পায়। এই ‘হিসেবে’ আপনি মেইনটেনন করেন কিভাবে? এটা কিন্তু মহা-হিসাব। একদিনের হিসাব না। এই ‘হিসাব বছরের পর বছর স্মুথলি রান করে। পর পর। উইদআউট এনি এক্সেপশন। কেমন করে এটা এত স্মুথলি রান করতে পারে? এর অপারেশনাল দিকগুলো কী? কার পরে কোনটা হয়? আমাকে এটা নিয়ে দীর্ঘকাল ভাবতে হয়েছে: ঘটনাটা কী? মানে বাস্তবে এটা চলে কেমন করে? প্রক্রিয়া-প্রণালিগুলো কী? কিসের পরে কী হয়? কার পরে কোনটা হয়? আমাকে এটা নিয়ে দীর্ঘকাল ভাবতে হয়েছে: ঘটনাটা কী? এটার জন্য দীর্ঘকাল ভাবা লাগে না আসলে। সামান্য তাকালেই দেখা যায়। আমি যে বহুকাল দেখতে পাই নি, তার কারণ আমি মুখস্থ ধারণা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলাম। আপনাদেরই অনেকের মতন। দীর্ঘকাল ধরে।
আমাদের সমাজে তো কোনটা কী, সবকিছুই আমরা রেডিমেড জানি। মুখস্থ। [অন্যান্য দেশে/সমাজেও পরিস্থিতি মূলত একই। পরিমাণে কমবেশি। বা মাত্রাগত কমবেশি। মায়ের পেট থেকে পড়ার আগেই জানতে আরম্ভ করি। নিজেরা নিজেদেরকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার আগেই], আমরা শিখতে আরম্ভ করি: কোনটা কী। আসমানের নিচে, সূর্যের নিচে যা কিছু আছে, তার সবকিছু। ঘাস কী? মাটি কী? বটগাছ কী? বন্দুক কী? বিচারবিভাগ কী? গণতন্ত্র কী? পদার্থবিজ্ঞান কী? সাহিত্য কী? প্রেম-ভালোবাসা কী? ডিভোর্স কী? এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং। জানতে-শিখতে আরম্ভ করি। এই কারনেই নিজের মাথা খাটায়ে যেটা সহজে জানা যেত, সহজেই, তাকালে পরেই জানা যেত, সাদা চোখে দেখা যেত, সেটা আর দেখা হয়ে ওঠে না।
ঘটনা হচ্ছে: আমরা ফার্স্ট-ইয়ারেই টার্গেট করি। সম্ভাব্য এক্স, ওয়াই, জেড- কে ‘আমার লোক’ হতে পারেন। সম্ভাব্য কে কে। এটা অনেক রকম প্রক্রিয়াতেই হবে। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা। আমি খুঁজব ‘আমার লোক’। লক্ষণ দেখব। বেয়াদবির লক্ষণ আছে কিনা। আদবকায়দার লক্ষণ আছে কিনা। (এইগুলার মানে বুঝে নিয়েন কিন্তু। বেয়াদবির লক্ষণ মানে কী? আদব-কায়দার লক্ষণ মানে কী? আপনাদের চেয়ে, শিক্ষার্থীদের চেয়ে, সেটা বেশি আর কে বোঝেন?) আরও অনেক কিছু দেখব। তার সঙ্গে আমার স্বভাবচরিত্র মিলতে হবে। ক্লিক করতে হবে। জ্যাক এবং পিন খাপে-খাপ লাগতে হবে। লাগল কিনা দেখব।
মোটামুটি এরকমভাবে একটা ‘সেট’ ঠিক করে ফেলব আমরা। আমি হয়তো একজনকে ঠিক করব। আপনি হয়তো আরেকজনকে ঠিক করবেন। আরেকজন অন্য কাউকে ঠিক করবেন। এভাবে একটা ‘সেট’ হয়ে যাবে। এ সেট অফ অল্টারনেটিভস। কিন্তু ‘সেট’ হতে হবে একটা। তিন-চারজনের সেট। বা কখনও কখনও পাঁচ-ছয়জনের সেট। এর বেশি নরম্যালি হয় না।
এইবার এই শিক্ষার্থীরা, ফার্স্ট-ইয়ার থেকেই, কম বেশি ফার্স্ট-ক্লাস নম্বর পেতে থাকবেন। অথবা পরিস্থিতি যদি আরও খারাপ হয়, তাহলে ফার্স্ট-ইয়ারেই তিরিশ সারপ্লাস বা বিশ সারপ্লাস। মিস যেন না হয় ফার্স্ট-ক্লাস কোনোভাবেই। কিংবা ফার্স্ট-ইয়ারে এক-দুই নম্বর শর্ট? ঠিক আছে। পরে দেখতেছি। সেকেন্ড-ইয়ারে, থার্ড-ইয়ারে, ফোর্থ-ইয়ারে, মাস্টার্সে পোষায়ে দেব। ব্যবস্থা করে নেব। এইবার ‘টিম’, এই যে ‘সেট’, এরাই ‘আমাদের লোক’। ‘আমাদের’ মানে ‘আমরা’, যাঁরা আছি, বিভিন্ন দলের মাস্টাররা, সেই ‘আমাদের’ লোক। এই ‘সেট’ই ভবিষ্যতের শিক্ষক। সেকেন্ড-ইয়ারে। থার্ড-ইয়ারে। ফোর্থ-ইয়ারে। মাস্টার্সে। এঁরাই। হয় এ ফার্স্ট, নয় ও ফার্স্ট। এঁদের মধ্যেই যত ‘কম্পিটিশন’ হবে। ‘প্রতিযোগিতা’ হবে। প্রতিযোগিতা কিন্তু পড়াশোনার না। ভুল করবেন না। প্রতিযোগিতা হবে পরীক্ষা বেশি নম্বর পাওয়ার।
পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়া, আর ভালো করে পড়াশোনা করা আকাশ-পাতাল আলাদা জিনিস। ভালো রেজল্ট করা, আর ভালোভাবে অধ্যায়ণ করা দুইটা দুই বিপরীত মেরুর জিনিস। এটা একটা বৈজ্ঞানিক সূত্র। অন্তত এখনকার দিনে। এমনিতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা জিনিসটা এক ধরনের; আর আমলাতান্ত্রিক শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষাকাঠামো আরেক পদের জিনিস। অক্সফোর্ড হোক, হার্ভার্ড হোক, যাই হোক, ঐ আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে সত্যিকারের অধ্যায়নের, বোঝাপড়ার, পড়াশোনার, উপলব্ধির ও কর্তব্য-পালনের মিল কমই ঘটে। নোবেল পুরস্কার পাওয়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনার উৎকর্ষ কনফার্ম করা যায় না। রচানার সাহিত্যগুণ কখনও পুরস্কার-মানদণ্ড দিয়ে বোঝা যায় না। পৃথিবীর কোনো পুরস্কার দিয়েই জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, মানবিক মূল্যবোধ, উচ্চতর অনুভূতির চর্চা- এগুলো হয় না। পুরস্কারের সাথে এমনিতেই এগুলোর বিরোধ আছে। তবুও আমরা যেহেতু ইম্প্র্যাক্টিকাল চিন্তা করতে পারি না, আমাদেরকে সমাজের এই মুহূর্তের বাস্তব চাহিদা তো মেটাতে হয়, যার ফলে সমাজে এরকম স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রয়োজন থেকেই যায়। মূল প্রশ্নটা এর কালোপযোগী সংস্কার নিয়ে।
তো, ঐ যে আমরা একটা সেট ঠিক করেছিলাম ফার্স্ট-ইয়ারে থাকতে, ঐ টিমের মধ্যে চলছে এখন কপাল-কাকতাল, চেষ্টা-চরিত্র, সাধনা-অধ্যবসায়। সেই সাথে শিক্ষকদের রেষারেষি, ঘষাঘষি, সহযোগিতা-শত্রুতা। আর শিক্ষার্থীদের হুজুর হুজুর, ধামাধরা ভাব। সারাক্ষণ একটা ‘হায় হোসেন, হায় হোসেন’ ভাব, দৌড়াদৌড়ি। সারাক্ষণ জিহ্বা বের হয়ে ঝুলছে। হাঁপাচ্ছে এবং টেনশনে ভুগছে: এই স্যার কী মনে করলেন, ঐ স্যার কী মনে করলেন, এই স্যারের গুড-বুকে আমি আছি কিনা, নম্বরটা পাব কিনা, এই কোর্সের টিচারের কী হবে, ঐ কোর্সের শিক্ষক তো এখনও ম্যানেজ হলো না, তার কী হবে- এইসব দুশ্চিন্তা-সাধনা-অধ্যয়ন করতে করতে এদের মধ্যে থেকে এ, না হয় ও, ফার্স্ট- সেকেণ্ড-থার্ড এগুলো হলেন। কোনো ব্যাচে হয়তো ফার্স্ট-ক্লাসই হলো না কারও। তার মানে সবকিছু মিলিয়ে কম্বিনেশন মেলে নাই। কোনো ব্যাচে হয়তো হলো। এসব করে যাঁরা ফার্স্ট-ক্লাস নিয়ে বের হয়ে আসতে পারলেন, তাঁরাই তো আমাদের শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ-বোর্ডে যাবেন।
আচ্ছা। এবার আমি আরও একটু গোড়ার দিকে এগোই। ঐ যে আপনি ফার্স্ট-ইয়ার থেকে শুরু করতে পারলেন, একটা সেট যে বাছাই করতে পারলেন, এবং ঐ সেটই যে অনার্স-মাস্টার্স পার হয়ে আসল, এটা আপনি কিভাবে পারলেন? এর ম্যাজিকটা কী? এর প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিটা কী? পদ্ধতিটা হচ্ছে খাতা দেখার বিদ্যমান পদ্ধতি। মানে পরীক্ষা-পদ্ধতি।
খাতা দেখার পদ্ধতিটা এরকম: খাতা দেখবেন দুইজনে। এই দুজনের মধ্যে যদি মতান্তর হয়, নম্বর যদি আলাদা আলাদা হয়, তাহলে তাঁদের দেওয়া নম্বরের গড়ে বের করতে হবে। আর, দুজনের দেওয়া নম্বরের মধ্যে যদি শতকরা ২০ নম্বর বা তার বেশি তফাত হয়, তাহলে পরে তিন নম্বর আরেকজন খাতা দেখবেন। এভাবে, আমরা যে নিরপেক্ষ, আমরা যে মুখ চিনে নম্বর কমবেশি করি না, সেটা একদম কনফার্ম করা আছে। কাঠামোগতভাবে। পদ্ধতিগতভাবে। ভাবটা এ রকম। ভণিতাটা এ রকম।
[বাস্তব অবস্থা ঠিক উল্টা ‘ঠাকুর ঘরে কে রে, আমি কলা খাই নি’ অবস্থা।] এই যে ভণিতাটা, এই ভণিতাটার মধেই তা স্ট্রেইটকাট বলা আছে। এই ভণিতাটা ইটসেল্ফ, পরীক্ষার এই আইন নিজে, স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে-সগর্বে ঘোষণা করছে যে একজন শিক্ষক একাই যদি খাতাটা দেখেন, তাহলে উনি ঠিকমতো খাতাটা দেখবেন না। দ্যাট ইজ দ্যা অ্যাজাম্পশান, দ্য বেসিক অ্যাজাম্পশান। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর, অথচ সেই আমিই আমার ছাত্রের খাতার মূল্যায়ন যদি একা করি, তাহলে স্বাজনপ্রীতি করে ফেলব। নম্বর কম দিব, নম্বর বেশি দিব! এটা হচ্ছে নিজের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-প্রফেসরদের চরিত্র সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-আইনের মৌলিক অনুমান। তাহলে আমি কিসের প্রফেসর? তাহলে আমি কিসের শিক্ষক? আমার নীতি, মূল্যবোধ, শিক্ষাদীক্ষা এগুলো কোথায়? তাহলে শিক্ষকের নীতিবোধ বলে কিছু নাই?
অবস্থাটা খেয়াল করুন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করলাম। করে দেখলাম যে বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে চোর মনে করে। বিশ্ববিদ্যালয় ধরেই নে, আমি যদি খাতাটা এক একা দেখি, তাহলেই আমি নয়ছয় করে ফেলব। এরই জন্যে, খাতা দেখবেন দুই জন। বিশেষ এদিক সেদিক হলে তিনজন। [যেহেতু অনুমিতভাবে আমি চোর, তাই আমাকে একা খাতা দেখতে না দিয়ে আরও একজন চোরকে পরীক্ষক নিয়োগ করা হবে। দুই চোরের কর্মফলে (খাতা দেখা উপলক্ষে প্রদত্ত নম্বরে) শতকরা ২০ ভাগের বেশি পার্থক্য ঘটলে নিয়োগ দেয়া হবে তৃতীয় চোরটিকে। এক চোরে শান্তি নাই, তিন চোরের জোট! কে না জানেন: “চোরে চোরে মাসতুতো ভাই”।]
তাতেও শান্তি নাই। গোটা প্রক্রিয়াটা [আইনত] ‘গোপন’। মহা গোপন। [কাকপক্ষীও যেন জানতে না পারে।] এবং মহা প্রকাশ্যও বটে। জায়গামতো। [যেখানে যেরকম দরকার: টু হুম ইট মে কনসার্ন আর কি। যাহার জন্য যাহা প্রযোজ্য। ফলে, বিভাগের ও পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রক দপ্তরের পিয়ন-কেরানিগণ প্রকাশ্য কর্মস্থালে বসে স্বহস্তে সংগুপ্ত পত্রাবলি টাইপ করেন। তারপর সমস্ত খামের ওপর ‘গোপন’ সিলমোহর এঁকে কাকপক্ষী ব্যতিরেকে এই মর্মে গ্রামময় রাষ্ট্র করে দেন: ‘এটা কিন্তু গোপন, কেউ দেখে ফেলবেন না, প্লিজ।
গোপনীয়তার যুক্তি কী? কারণ, গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গেলেই মাস্টাররা নয়ছয় করে ফেলবে। কে কে খাতা দেখছেন, ফার্স্ট এগজামিনার কে, সেকেন্ড এগজামিনার কে, এগজাম কমিটির কারা কারা মেম্বার, এগজাম কমিটির চেয়ারপারসন কে, এসব যদি শিক্ষার্থীরা জানেন, তাহলেই কী কী জানি হয়ে যাবে, আর মাস্টাররা সব উল্টাপাল্টা নম্বর দেওয়া শুরু করবেন। [ঐ গোপন ব্যাপার শিক্ষকবৃন্দ তো জানবেনই, কারণ সকল শিক্ষকের প্রত্যাশিত উপস্থিতিতে সিন্ধান্তগুলো নেওয়া হয়, পিয়ন-কেরানি জানলেও কোনো ক্ষতি নেই, যেহেতু তাঁরা কাকপক্ষী নন।] এটা হচ্ছে গোপনীয়তা বজায় রাখার পক্ষে যৌক্তিক আইনসিদ্ধ অনুমান। আবারও, অনুমানটা মাস্টারদের চরিত্র সম্পর্কেও বটে।
অনুমান একই রকম শিক্ষার্থীদের চরিত্র সম্পর্কেও। [তাঁরা যদি জানতে পারেন পরীক্ষা-প্রণালির গোপন কুশীলব কারা, ওমনি তাঁরা তখন শিক্ষকদের বাসায় ‘নিজেদের বাগানের’ কলাটা মুলাটা কিংবা নিজেদের পার্টির রামদাটা, পিস্তলটা নিয়ে শিক্ষকদের পেছনে পেছনে ঘুরতে শুরু করবেন। শিক্ষকদের সচ্চরিত্র বিনষ্ট না করে তাঁদের শান্তি নেই।] এমনকি শিক্ষার্থীরা খাতার উপর নিজের নামটাও লিখবেন না। সাংকেতিক রোল নম্বর লিখবেন। নামধাম সব ‘গোপন’। অথচ সবাই জানেন। পিয়ন জানেন, কেরানি জানেন। শিক্ষক জানেন। সুতরাং, শিক্ষার্থীও জানেন। প্রশাসন ভবনে গিয়ে ২০ টাকা দিলে আপনিও জানবেন। যে কেউ জানতে পারবেন। অথচ, আইনত ‘গোপন’। মহা গোপন।
কোনো ছাত্র যদি নাম লেখেন, মানে খাতা যদি বলে, “স্যার, নিউটন স্যার, এই খাতাটা আমার, আমি অমুক ছাত্র”, তাহলেই আমি একদম গলে যাব: “ওরে আমার ছাত্র রে, আয় তোকে নাম্বার বেশি দিই”, কিংবা “পাইছি বেয়াদবটারে, এত বড় বেয়াদব, দেই বেটারে ফেল করায়ে।” এগুলোই হচ্ছে আমাদের অনুমান। ছাত্রদেরকে নিয়ে এবং শিক্ষকদেরকে নিয়ে। অথচ, এই ‘শিক্ষার্থীরাই আগামীতে দেশ চালাবে’, ‘এরা দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব’, ‘শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড’, এইসব বুলিতে কথা-কাগজে ভরপুর।
এবার দেখেন, খাতা দেখার এই যে ‘দ্বৈত পরীক্ষণ পদ্ধতি’, আর এই যে গোপনীয়তা, এর মজাটা কী। এর মজাটা হচ্ছে, আমি আর আমার বন্ধু দুজনে মিলে ঠিক করব, “দোস্ত, আমাদের ক্যান্ডিডেট কিন্তু অমুক, ‘এক্স’। তুমি সেকেন্ড এগজামিনার আছ, আমি ফাস্ট এগজামিনার আছি, নাম্বার কিন্তু ঠিকমতো দিও।” এইটা আলাপ করে নেব আমরা। দরকার মতো।
দরকার যদি না পড়ে [অপর পরীক্ষক যদি ‘শত্রু’ দলের কেউ হন], তাহলেও একটা অদৃশ্য ‘আলাপ’ থাকবে: “দেখি তুমি কেমনে ওরে ৬০% নম্বর দিয়া পার করাইতে পার!” অপর পক্ষের মনেও একই কথা: “দেখি, তুমি কেমনে আটকাও!” মানে, তখনও একটা ‘অলিখিত আন্ডারস্ট্যান্ডিং’ আছে। [তলে তলে একই পাটাতনে দাঁড়িয়ে থাকেন পরস্পরের ‘শত্রু’।] মানে শত্রুতার আন্ডারস্টান্ডিং। [শত্রুতার সন্ধিপত্র আর কি।] রেষারেষির আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এই মর্মে যে: “তুমি যে ফার্স্ট এগজামিনার আছ, তা তো আমি জানিই। আমিও সেকেন্ড এগজামিনার হয়ে আছি। আমিও ধরায়ে দিব।” যেখানে প্রয়োজন সেখানে একসাথে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে আলাদা-আলাদাভাবে। মানে উইথ এ ফুল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, অ্যান্ড এ কমপ্লিট নোয়িং অফ দ্যা সিচুয়েশন, আমাদের যা করণীয় সেটা আমরা করব। এইটা হচ্ছে প্রক্রিয়া।
এইটা হচ্ছে প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থী এসে তো বলতে পারবেন না যে আমি স্যার নম্বরটা বেশি পেলাম কেন, বা কম পেলাম কেন? কোনো শিক্ষার্থী এসে যদি জিজ্ঞেস করেন জনাব কোর্স-শিক্ষককে, কোর্স-শিক্ষক বলবেন, “আমি তো জানি না, বাবা। খাতা যে কে দেখেছেন, সেকেন্ড-এগজামিনার যে কী করেছেন, সেটা তো আমি জানি না। আমার কাছে তো তুমি ভালোই পেয়েছে।” এখন শিক্ষার্থী ‘হাইকোর্ট’ পেয়ে গেলেন [দ্বিতীয়-তৃতীয় পরীক্ষকের নামে এবং গোপনীয়তার যুক্তিতে]। ছাত্রের এখন হাইকোর্টে দৌড়াদৌড়ি করা লাগবে: কে সেকেন্ড-এগজামিনার। আর, তিনি যদি ২০ টাকা দিয়ে হোক, বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে হোক, জানেনও সেকেন্ড-এগজামিনার ব্যক্তিটি কে, তবু তো তাঁকে তিনি ধরতে পারছেন না অফিশিয়ালি। [পরীক্ষার ফলাফল চ্যালেঞ্জ করার কোনো বিধান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃতপক্ষে নাই।] ফলে, এইটা এমন একটা বিচার-প্রক্রিয়া, যে বিচার-প্রক্রিয়াতে গোপনীয়তার আড়ালে খুব চমৎকার উচ্চ পর্যায়ের ‘নিউট্রালিটি’ কনফার্ম করার ভান করার মাধ্যমে আপনি নিজের ‘ইচ্ছামতো’ নম্বর খাতায় দিতে পারবেন। কোনো সমস্যা হবে না।
[কে কতটুকু নম্বর দিলে নম্বরের ব্যবধান শতকরা কুড়ির ঘরে পৌছাবে না, সেটা ঠিক করতে প্রথম এবং দ্বিতীয় পরীক্ষককে সুদীর্ঘ বৈঠক করতে হয় না। আর প্রথম পরীক্ষক এবং দ্বিতীয় পরীক্ষক যেন একই লাইনের লোক হন, সেটা কনফার্ম করেন পরীক্ষা-কমিটি। পরীক্ষা-কমিটিতে কারা কারা থাকবে, সেটা ঠিক করবেন অ্যাকাডেমিক কমিটি। স্রেফ ব্রুট মেজরিটির জোরে। অন্য কোনো বিবেচনায় নয়, স্রেফ অন্ধ গরিষ্ঠতার জোরে। আর, বছরের পর বছর কারা পরীক্ষা-কমিটি হন, কারা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পরীক্ষক হন, কার কার দেরির জন্য পরীক্ষার ফলপ্রকাশে বিলম্ব ঘটে, বাইরের লোক হলে এসব তো আপনি কখনই জানতে পারবেন না। পুরো ব্যাপারটাই যে আইনত ‘গোপন’ ঘটনা।
এসব কাজে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, শিক্ষকদের পরস্পর এমনকি আলাপও করা লাগে না। আমরা বুঝি। চোখে চোখে তাকালেই বুঝি, আমাদের কী দরকার। পরস্পরকে আমরা বুঝি। কেন বুঝব না? আমরা এখানে এক জায়গাতে এক সাথে ১২ বছর, ১৩ বছর, ৩২ বছর, ৪২ বছর ধরে থাকবো, আছি, আর আমরা পরস্পরকে চিনব না? আমরা কি বুঝব না, আমরা কে কী চাই? কার কোথায় আনন্দ? কার কোথায় দুঃখ? আমরা তো বুঝি। আমরা পরস্পরকে অতিরিক্ত ভালো করে বুঝি। স্বামী-স্ত্রী ৫০ বছর ঘর করলেও সবসময় এত ভালো বোঝেন না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টাররা পরস্পরকে এত ভালো বুঝি।
সভ্য দুনিয়াতে বিচার-প্রক্রিয়া মানেই কিন্তু বিচারটা ওপেন হতে হবে। এটা স্বচ্ছ হতে হবে। এখানে আপিল করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। উচ্চ আদালত থাকতে হবে। নিম্ন আদালতে আমি যদি বিচার না পাই, আমি উচ্চ আদালতে যেন যেতে পারি। শুনানি থাকতে হবে। বুঝায়ে দিতে হবে। আপনি যে বিচারক রায় দিলেন, কী বুঝলেন? বুঝায়ে বলতে হবে যে কী বুঝে ‘রায়’ দিছেন। দশ পাতা লিখতে হবে। পঞ্চাশ পাতা রায়ের দলিল লিখতে হবে। আমরা মাস্টাররা ‘রায়’ দিব, ঐ ছাত্রের সারা জীবনের জন্য কপালে দাগ টেনে দিব। এক (I) দাগ, দুই (II) দাগ, তিন (III) দাগ। ফার্স্ট-ক্লাস, সেকেন্ড-ক্লাস, থার্ড-ক্লাস। এবং বাকি সারা জীবন ঐ ছাত্রটা, ঐ ছাত্রীটা ঐ দাগ নিয়ে ঘুরবে। কিন্তু আমাদেরকে কোনো রায়ের দলিল দাখিল করতে হবে না। কোনো শুনানি করতে হবে না। আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না, কেন ও নম্বরটা বেশি পেয়েছে। কেন ও নম্বরটা কম পেয়েছে। [আমাদেরকে কেউ প্রশ্ন পর্যন্ত করতে পারবেন না। কেউ জানবেনই না যে নম্বরটা আমিই দিয়েছি। শিক্ষার্থী বেচারা সারা জীবনে জানতেও পারবেন না, কোন ‘বিচারক’ তাঁর রায়টা দিলেন। আমাদেরটা ‘গুপ্ত বিচার-পদ্ধতি’। আমরা সব মুখচোরা, অপ্রকাশ্য, আড়ালের বিচারক। অন্ধকারে অবস্থিত গোপন বিচারক। দিনের আলোয় আমরা সাধারণ শিক্ষকের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াই। রাতের অন্ধকারে খাতা দেখি।
আমি যে ‘রায়’ দিয়ে দিব, সেই রায়ের বিরুদ্ধে কোথাও কোনো আপিলও করা যাবে না। শিক্ষর্থী বলতে পারে, আমার খাতাটা ঠিকমতো দেখা হয় নি। তখন বিশ্ববিদ্যালয় কী করবে? বিশ্ববিদ্যালয় গুনে দেখবে যে সবগুলো প্রশ্নেই নম্বর দেওয়া হয়েছে কিনা, এবং সেইসব নম্বরের যোগফল ঠিক আছে কিনা। ব্যস! নম্বর তার মানে যা আছে তা-ই থাকবে। বদলাবে না। যদি আবার আমার বৌ, বা আমার কন্যা, বা আমার এরকম একেবারে আপনার জন, ‘আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন’, এরকম কোনো জন যদি আবার ক্যান্ডিডেট হয়, তখন আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদের উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠিত হয়ে যাবে। তখন প্রয়োজনে এক খাতা পাঁচবার দেখা হবে। এবং পাঁচবার দেখার ফলে রেজাল্ট বদলেও যেতে পারে। উদাহরণ আছে। কিন্তু সেটা ঐ ক্ষেত্রে, ‘আপনার চেয়ে আপন যে জন’, তাঁদের বেলায়। অন্য কোনো বেলায় না।
তার মানে, আপনি এ-ও দেখলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়-আদালত এমন একটা আদালত, যেখানে আইন কোনো সমস্যা না। চাইলে পরে বিশ্ববিদ্যালয় রেজাল্ট সত্যি সত্যি ‘রিভিউ’ করতে পারে। কিন্তু অন্য কারও বেলায় সেটা করা হবে না। [সুযোগ সীমিত]। ঠিক আছে?
এই হচ্ছে আমাদের বিচার প্রক্রিয়া। এই বিচার-প্রক্রিয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়েই বছরের পর বছর ধরে আমরা মাস্টাররা আমাদের পছন্দ মতো লোকদেরকে ফার্স্ট-ক্লাস দিয়ে যাচ্ছি। [আর, বাইরে-বাইরে ধোপদুরস্ত সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে জুম্মার নামাজে যাচ্ছি, সরস্বতী পূজায় যাচ্ছি।] হিসাবের বাইরে কাউকে কোনো ফার্স্ট-ক্লাস দেওয়া হবে না। আমরা চাইলে পরে একই ব্যাচে ৫২ জনকেও দিতে পারি ফার্স্ট-ক্লাস। আমরা চাইলে অনার্স পরীক্ষায় পর পর ১৩ বছর উইদআউট এ ফার্স্ট-ক্লাস একটা ডিপার্টমেন্ট চলবে। উদাহরণ আছে। দুই রকমরেই। দুইটাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ দিলাম। একটা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের। যেখানে ১২ বছর কী ১৩ বছর ফার্স্টক্লাস ছাড়া ডিপার্টমেন্ট চলেছে। পার্টিকুলারলি অনার্স। আর ৫২ জনের যেটা, ঐটাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ের। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। এটা আপনার জানেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ফলে, আমরা দুই রকমেরই পারি। আমরা সব পারি। আচ্ছা। এর ফলাফলটা কী?

বিশ্ববিদ্যালয় কী বস্তু: এমনিও সেকেন্ড-ক্লাস, ওমনিও সেকেন্ড-ক্লাস
যে ছাত্র বা ছাত্রী ফার্স্ট-ইয়ারে ভর্তি হলো অনেক স্বপ্ন নিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পড়বে, কত স্বপ্ন এবং আশা নিয়ে, সে শিক্ষিত হবে, পড়াশোনা শিখবে, পরে ভালো চাকরি পাবে, বিশ্ববিদ্যালয় তার গৌরব, তার মর্যাদার জায়গা এটা, সেই ছেলেটা বা মেয়েটা ফার্স্ট-ইয়ারটা কোনোরকমে পাশ করতে না করতেই তার হাড়ে হাড়ে আক্কেল হয়ে যায় যে ‘বিশ্ববিদ্যালয়টা কী বস্তু’।
এবং সবার আগে সে যেটা শেখে, সেটা হচ্ছে এই যে ‘পড়াশোনা করার কোনো দরকার নাই’। কারণ, পরীক্ষা আসলে কার? পরীক্ষা তো ঐ ‘সেটের’! ঐ যে আমি ‘সেটের’ কথা বলছিলাম, ঐ ‘সেট’। ওদের মধ্যে কে ফার্স্ট হবে, কে সেকেন্ড হবে, কে কোন ‘দাগ’ পাবে, ঐটা হচ্ছে পরীক্ষা। বাকিরা দুধভাত। বাকিরা ফাউ।
বাকিদের জন্য পরীক্ষার মানে কী? প্রমোশন! ‘ফার্স্ট-ইয়ার থেকে সেকেণ্ড-ইয়ারে উঠেছে’ [উত্তীর্ণ], যেটা ওরা এমনিতেই উঠবে। ফেল করার নিয়ম নাই। বাস্তবে। থার্ড-ক্লাস পাওয়ার নিয়ম নাই। বি-র-ল ব্যতিক্রম। দুই-একটা বিভাগে আবার ঐটা আরেকটা মর্যাদা। যে ‘আমাদের বিভাগে থার্ডক্লাসও দেই আমরা। আমাদের বিভাগ যেমন-তেমন না।’ নির্দিষ্ট কোনো বিভাগের নাম বলার দরকার নাই এখানে। কোনো বিভাগকে উঁচুতে-নিচুতে নামানোর প্রয়োজন নাই। আপনারা জানেন। আচ্ছা। তো, এই ছাত্রছাত্রীরা ফার্স্ট-ইয়ারেই হাড়ে হাড়ে শেখে যে পড়াশোনাটা করে লাভ নাই। এমনিও সেকেন্ড-ক্লাস, ওমনিও সেকেন্ড-ক্লাস।
তারপর থার্ড-ইয়ারে উঠতে উঠতে একটু মনে হয়: ‘না, সেকেন্ড-ক্লাসটা একটু ভালো হলেই ভালো। ৫০ এর জায়গায় ৫৫-৫৬ হলে একটু ভালো হয়। চাকরি পাইতে মনে হয় একটু সুবিধা। বিসিএস-টিসিএস দিকে একটু সুবিধা।’ টার্গেটটা হলো কোনো রকমে চাকরিটুকু পাওয়া ভবিষ্যতে। কোনোরকমে বিসিএসটা দেওয়া।
এই অনুভূতিগুলো তীব্র। এই অনুভূতিগুলো কিন্তু আমারও। আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার আজকে, এটা একটা এ্যাকসিডেন্ট, ইন মাই লাইফ। সেটা অন্য কাহিনী। এখানে আজকে বলার দরকার নাই। আমিও ফার্স্ট-ইয়ারে প্রথম টিউটোরিয়াল পরীক্ষা দিয়ে শিখেছিলাম যে পড়াশোনা করার প্রয়োজন নাই। এবং পড়াশোনাটা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। মাস্টার্সে উঠে অন্য কাহিনীর কারণে আবার সেটা করেছি। সেটা অন্য হিসাব। সেই হিসাব আমি না বলি। টেম্পটিং। বলার জন্য খুব প্রলুব্ধকর কাহিনী। হ্যাঁ? কিন্তু না বলি। বলা যাবে। জায়গামতো। পরে।
তো, এইভাবে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনাটা বাদ দিয়ে দেন। কী দরকার? নোট আছে। প্রশ্ন কমন আছে। প্রশ্ন কমনের বাইরে যাবে না। বিরল ব্যতিক্রম না হলে। নোট ফটোকপির দোকানে গেলেও পাওয়া যাবে। এখন আর মানে ক্লাসমেটের কাছেও যাওয়া লাগে না। সুতরাং কোনো অসুবিধা নাই। সেকেন্ড-ক্লাস তো পাব এমনিতেও, ওমনিতেও। এইভাবে ছাত্রদের মনোভাবটা এইরকম পাকাপোক্ত হতে হতে এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে যে টিচার পড়াবে সিনসিয়ারলি, (সিনসিয়ারলি; কতটুকু ইফিসিয়েন্টলি আমি জানি না, কিন্তু উইথ মিনিমাম সিনসিয়ারিটি সে টিচার পড়াবে) ঐ টিচার ছাত্রদের জন্য অসুবিধাজনক। যদি এরকম টিচার দু-একজন থাকে। ঐ টিচার বেশি পড়ায়ে ফেলে। ঐ টিচারের পরীক্ষা দেওয়া কঠিন। প্রশ্ন বুজতে একটু মুশকিল হয়ে যায়। টপিক আটটা হলেই হয়। সে পড়াইছে বিশটা বা পনেরটা। অসুবিধা। [তাঁর কোর্সে পরীক্ষা দেওয়াও ঝামেলা। প্রশ্ন জানা থাকলেও মুখস্থ উল্টর দেওয়া যায় না।] এগুলা অসুবিধা।
আরও বড় কথা হচ্ছে শিক্ষার্থীরা এখন পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন করে না আর। তাঁরা পরীক্ষা আগানোর আন্দোলন করে। আক্ষরিক অর্থে। কারণ পড়াশোনা তো লবডঙ্কা! এমনিও ঐ জিনিস, ওমনিও ঐ জিনিস। মাঝখান থেকে দেরি করে কাজটা কী! দেরি করা মানে বিসিএস কম দিতে পারব। দেরি করা মানে বিসিএস ফস্কেও যেতে পারে। মাস্টারদের ও তো বিশ্বাস নাই! ওঁদের যদি কিছু না বলা হয়, তাহলে পরে তো সেশন জট লম্বা হতেই থাকবে। ফলে, ছাত্ররা ঐ সেকেন্ড-ইয়ার থেকেই বলা শুরু করে, ‘তাড়াতাড়ি স্যার’, ‘তাড়াতাড়ি স্যার’, ‘তাড়াতাড়ি স্যার’। এক বছরের কোর্স ছয় মাসে হয়ে গিয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে। আইনগতভাবে। অনেকদিন আগে। ঠিক আছে?
এইবার আইনের বাইরে আমরা তিন মাসেও কোর্স শেষ করে দিচ্ছি। তিন মাস পড়িয়ে। চতুর্থ মাসে পরীক্ষা। আমরা করেছি। ইয়াজউদ্দিন-ভ্যাকেশনে আমরা এটা করেছি। আমাদের ডিপার্টমেন্টে করেছি। বাধ্য হয়েছি করতে। শিক্ষার্থীদের চাপে। আমাদের মনেও মনে হয় চাপ ছিল। কারণ আমাদেরও তো ঘটনা ঐ একই। আমাদের তো সেট-ই আছে। আর, কোনো কারণে বিশেষ একটা ইয়ারে যদি আমাদের নিজেদের কোনো সেট না থাকে, তাহলে তো আরও মওকা। আমার যদি মিশন-ই না থাকে, তাহলে তো আমি আরও ফ্রি। তখন আর পড়ালেই কী, আর না পড়ালেই কী। তিন মাস হলেই কী আর ছয় মাস হলেই কী। ফলে, আমরা বাধ্য হয়েছি। এবং এটা এখন রেওয়াজ।
ব্যাপারটা এরকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে বাড়ির থেকে পড়ে-টড়ে এসে, কোর্স-টোর্স শেষ করে এসে ভর্তি হবে। ভর্তি হয়ে পরের দিনই বলবে যে “ভাই, আমাকে একটা সার্টিফিকেট দেন। পরীক্ষা নিয়ে নেন। আমি সেকেন্ড-ক্লাস পেতে পারি। আমি জানি সেকেন্ড-ক্লাস পাওয়ার জন্য কী লাগে। আমাকে ছেড়ে দেন। আমি [গিয়ে] বিসিএসটা দিই গা।” ছাত্রের সাথে শিক্ষকের আর কী লেনদেন? এটা হচ্ছে অবস্থা। একদম বাস্তব অবস্থা। আক্ষরিকভাবে এটা হচ্ছে অবস্থা। আপনারা দেখবেন নিজেদের অভিজ্ঞাতার সাথে মিলিয়ে।

প্রাথমিক সমাধান-সূত্র: সিঙ্গেল এগজামিনারশিপ
তার মানে বোঝা যাচ্ছে: খাতা দেখার জায়গাটা হচ্ছে আমাদের গোড়ার জায়গা। আমাদের লাগবে সিঙ্গেল এগজামিনারশিপ। যা আছে, তার মধ্যে এটাই মূল সমাধান-সূত্র। এর চাইতেও মহান সমাধান নিশ্চয়ই আছে। সেটা বিপ্লবের পরে হবে। নানান ধরনের বিপ্লব করার পরে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যেটা পথ দেখি, এই মুহূর্তে যা আছে তার মধ্যে যেটা পথ দেখি, সেটা হলো: সিঙ্গেল এগজামিনারশিপ লাগবে। একক খাতা-পরীক্ষণ পদ্ধতি। কোর্স পড়িয়েছি আমি, আমি একাই প্রশ্ন করব, খাতা আমিই দেখব, আমি একাই নম্বর দেব। ঐটাই চূড়ান্ত।
এর ফলে কী ঘটবে বুঝে দেখেন। এর ফলে আমার জন্য মুশকিল হবে। আমার জন্য। শিক্ষকসমাজের জন্য। মুশকিল কী হবে? তখন আমি আর বলতে পারব না: “বাবা, সেকেন্ড-এগজামিনার কী নম্বর দিয়েছেন, আমি জানি না।” তখন নম্বর আমি যেটা দিব, শিক্ষার্থীরা জেনে যাবেন। জেনে যাবেন যে নম্বর নিউটন স্যারই দিয়েছেন, আর কেউ কিছু করে নি এখানে। তখন আমার আকাম করে লুকানোর জায়গা থাকবে না। তখন যে যদি সরাসরি আমাকে কিছু না-ও বলে, তবু গোটা ক্লাস জানবে, আমার খাতা দেখা কী চরিত্রের। অফিসিয়ালিই জানবে। ওপেনলি জানবে। সবাই সবকিছু জেনে যাবেন। সবাই তখন বিশাল মিছিল বের না করলেও ‘গুজুর-গুজুর ফুশুর-ফুশুর’ তো করবেন অন্তত। এখন যে যুগ এসেছে, আমি নিশ্চিত, তার পর শিক্ষার্থীরা নির্ঘাৎ বলবেন: ‘আমি নম্বরটা কম পেলাম কেন বলেন’। আমি নিশ্চিত, বলবে। তাহলেই চলবে।
খাতা দেখার এই ‘একক পরীক্ষণ পদ্ধতি’তে শিক্ষকদর/বিচারকের জবাবদিহিতা এবং রেসপন্সিবিলিটি অনেক বেড়ে যাবে। আমাকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে। একক দায়িত্বে নম্বর দিতে হবে। এবং সেটা সবাই জানবেন। সঙ্গে শুধু এইটুকু আইন নতুন করে যোগ করে দিতে হবে যে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় যে গ্রেড পেলেন, তার ব্যাখ্যা তাঁরা কোর্স শিক্ষকের কাছে দাবি করতে পারবেন, এবং ভরা-ক্লাসে শিক্ষক তাঁর ব্যাখ্যা হাজির করতে বাধ্য থাকবেন। এগুলো কিন্তু কোনো ‘আবিষ্কার’ না। আমাদের বন্ধুরা যাঁরা বাইরে পড়াশোনা করতে যান এবং ফিরে আসেন, তাঁরা জানেন। ওখানে এসব ধারণা ডালভাত। এগুলো সাধারণ নিয়ম। ঠিক কিনা? আমি কাকে কত নম্বর দিলাম আমাকে সেটা বুঝিয়ে বলতে হবে না? দরকার হলে নম্বর বাড়াতে হবে, যদি সে আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারে যে তার নম্বর বেশি পাওয়ার কথা। দরকার হলে নম্বর কমাতেও হবে। তাহলে আর কোনো ফাঁকিবাজি থাকতে পারবে না। আড়াল থাকবে না। কোনো গোপনীয়তা থাকতে পারবে না। পরীক্ষার সম্পূর্ণ পদ্ধতিটা হতে হবে প্রকাশ্য এবং জবাবদিহিতামূলক। প্রকাশ্য বিচার এবং বিচারের রায়ের প্রকাশ্য মডিফিকেশন।
আর, অবশ্যই একটা বোর্ড জাতীয় [কিছু একটা] থাকতে হবে। ফ্যাকাল্টি ধরে অথবা যেটা সুইটেবল হয়। সেখানে আপিল করা যাবে। শিক্ষার্থীরা আপিল করতে পারবেন যে আমি নম্বর কম পেয়েছি, আমি ভিক্টিম হয়েছি। টিচারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, নেগোসিয়েশন, যুক্তিতর্ক-দেনদরবার করেও যদি তাঁর মনে শান্তি না হয়, যদি তিনি সন্তুষ্ট না হতে পারেন, তাহলে তিনি আপিল করতে পারবেন। এবং আপিলের রায় যদি টিচারের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে তাঁর ব্যাপারে কিছু না কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রাখতে হেব। ঐ টিচার কিছুদিন খাতাপত্র না দেখেই থাকবেন। বা অন্য রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। নীতিগতভাবে এক্ষেত্রে কঠোরই হওয়া উচিত।
ফলে সমাধান খুব সিম্পল। আপনি যদি সমাধানটা করেন, তাহলে, [প্রস্তাবিত ‘একক পরীক্ষণ পদ্ধতি’তে] আমি দিনের পর দিন নম্বর নিয়ে নয়ছয় করে যেতে পারব না। একের পর এক ব্যাচ বের হবে, আর গোটা বাংলাদেশে আমার ‘সুনাম’ রটতে থাকবে, নিউটন স্যার খাতায় নম্বর কম দেয়, বেশি দেয়। একের পর এক ব্যাচ বের হবে, আর গোটা বাংলাদেশে আমার ‘সুনাম’ রটতে থাকবে, পছন্দের ছেলেকে, অপছন্দের মেয়েকে নিউটন নম্বর বেশি দেয়, কম দেয়। একের পর এক ব্যাচ বের হবে, আর চল্লিশ-পঞ্চাশটা করে ‘মাইক’ আমার ‘সুনাম’ গাইতে থাকবে সারা বাংলাদেশে। আমি বেশিদিন কন্টিনিউ করতে পারব না। ছাত্ররা এখন আর অত ম্যান্দামারা না। সেগুলো বাদই দিলাম।
এর আরও সুফল আছে। কী সুফল? [‘একক পরীক্ষণ পদ্ধতি’তে খাতা দেখার এবং পরীক্ষার ফলপ্রকাশের ক্ষেত্রে সময়ও লাগবে কম।] আর, এই পদ্ধতিতে আমি চাইলেই পছন্দের ছেলেমেয়েকে ফার্স্ট-ক্লাস দিতে পারব না। তার মানে আমি [দ্বৈত পরীক্ষণ পদ্ধতি’র সৃষ্ট] ঐ চেইন, ঐ দুষ্টচক্রের শিকল আমি এখানে কেটে দিলাম। ছেদ করে দিতে পারলাম।
চেইনটার কথা মনে আছে তো? [এক] ‘হিসেবের বাইরে’ কেউ ফার্স্টক্লাস পাবে না। [দুই] সুতরাং, ভাইভা বোর্ডে সব ‘হিসাবের লোকেরা’ই ভাইভা দিবে। [তিন] সুতরাং, মাস্টারও ঐখান থেকেই হবে, ‘হিসাবের লোকেরা’ই হবে। [চার] ‘হিসাবের লোকেরা’ই আবার হিসেবটাকে নতুন করে করবে। এই দুষ্টচক্র থাকলে, ফার্স্ট-ইয়ার থেকে আমি যে ছাগলটাকে পাতা খাওয়াচ্ছি, ঘাস খাওয়াচ্ছি, সেই ছাগলটা যখন মাস্টার্স পাশ করে মাস্টার হবে, তখন সে তো আমাকে ছাড়া আর কিছুই বুঝবে না। আমি বলব এটা সকাল। ও বলবে হ্যাঁ, সকাল। আমি বলব এটা বিকাল। সে বলবে বিকাল। আমি যদি অন্যায়ও করি, ও সেটা মানবে। কারণ, ও তো ধামা ধরতে ধরতেই ফার্স্ট-ইয়ার থেকে এ পর্যন্ত এসেছে। ধামাধরা ছাড়া অন্য কোনো বিদ্যা সে ভালো করে আয়ত্ত করে নাই। এইসব ধামাধরা লোকেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেজরিটি টিচার। এখন। এই মুহূর্তে। এবং সে কারণে ওনারা এই মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধামা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পেলেই ধরে ফেলবেন। এবং নিরাপদে থাকবেন। ফলে, এই ধামাধরার প্রক্রিয়া সম্পর্কে এবং ধামাধরাদের সম্পর্কে যদি যাঁরা সংস্কার চান তাঁরা এ্যালার্ট না থাকেন, তাহলে গোটা সংস্কার-উদ্যোগ একেবারে ভেস্তে যাবে। মাঠে মারা যাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার। এটা খুব ক্লিয়ার।
তো, একবার আপনি যদি দুষ্টচক্রের ঐ শিকলটা ছিন্ন করে দেন, তাহলে কী হবে? ছাগল রিক্রুটেমেন্ট প্রক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে যাবে। যাঁরা অলরেডি আছে, তাঁদেরকে বেছে বেছে আপনি যদি বাদ দিতে নাও পারেন, ধরেন যদি নাও পারেন, প্রক্রিয়াটার নবায়ন তো আর হবে না। প্রক্রিয়াটা তো বন্ধ হয়ে গেল। [এই দুষ্টচক্রই গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত সর্বনাশের গোড়ায়। একবার যদি এতে ছেদ ঘটানো যায়, তাহলে ভোটার রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া বন্ধ। সরকার-রাজনৈতিকদল-সুশীলসমাজ-সেনাবাহিনী ক্ষমতাচক্রের বিষাক্ত আঁচ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা-সংহতিকে রক্ষারও এটাই পথ।]
একবার যখন অনুগত লোকেরা সাবই বুঝবেন, মাস্টারদের হাতে অত ক্ষমতা এখন আর নাই, তখন কিন্তু সবচাইতে বড় দাসেরও স্বাধীনতার সীমা বেড়ে যায়। মানুষের বাচ্চার নিয়মই এরকম। মানুষের বাচ্চার নিয়ম এরকম যে মানবসন্তান যদি কেউ হন, তাঁর ভেতরে স্বাধীনতার ‘বিষ’ থাকে। স্বাধীনতার জার্ম থাকে। স্বাধীনতার বীজানু থাকে। বীজানু। আবহওয়া সামান্য অনুকূল হলেই ঐ বীজানু মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সে স্বাধীনতা চায়। স্বাধীন হতে চায়। ফলে, আপনি যদি একটু পরিবেশটা এনে দিতে পারেন, এই মাস্টারদের অনুগত বাহিনী ডিগবাজি মারবে। কনফার্ম থাকেন। কারণ, কার এত ভালো লাগে বাজার করে দিতে, ব্যাঙ্কের বিল দিয়ে দিতে, মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করায়ে দিতে। প্রফেসরদের জন্য যত রকমের কাজ করতে হয় ফেলোদেরকে, শিক্ষক পদের প্রত্যাশী পূর্বকথিত ঐ ‘সেট’-এর ছাত্রদেরকে, সেগুলো করতে কোনো মানুষের বাচ্চার ভালো লাগে না। আমি জানি। আপনারাও বোঝেন এইটা। ফলে পরিস্থিতি বদলাবেই।
ওকে, নেক্সট পয়েন্ট। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে শিক্ষকদের নির্বাচন আর রঙবাজি। মানে দলবাজি। লাল-নীল দল। কে লাল, কে নীল, কে গোলাপি, কে পিংক, কে হলুদ, কে সাদা। এইসব।

তিয়াত্তরের বিশ্ববিদ্যালয় আইন, নির্বাচন এবং শিক্ষক-রাজনীতির রঙবাজি
এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে নতুন করে জানতে হবে, আদি ধারণাটা কী ছিল? এই যে কথাবার্তা শুনে যাচ্ছি, ‘শিক্ষক-রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে’। এটা কী নিষিদ্ধ করবে! শিক্ষক-রাজনীতি জিনিসটা আদৌ চলছে কোন আইনে? এটা কোনো আইনে আছে নাকি? বাংলাদেশে কোনো আইনে কি আদৌ বলা আছে যে শিক্ষকেরা লাল-নীল দল বানাতে পারবেন? ইসলামি মূল্যবোধের দল বানাতে পারবেন? গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দল বানাতে পারবেন? অথবা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ‘বিশ্বাসীদের’, অর্থাৎ ‘ঈমানদার’ মুক্তিযোদ্ধাদের দল বানাতে পারবেন?
এমন কোনো আইন বাংলাদেশে নাই। আমার জানামতে নাই। যতি কারও জানা থাকে, তাহলে দয়া করে আমাকে জানাবেন। আমি শিখব। আমি অনেক ভুল কথা বলতে পারি। আমার কোনো দুঃখ নাই। কিন্তু ভুলটা ধরিয়ে দেন। আমি তো প্রকাশ্যেই বলছি। রেকর্ডেড বলছি। ভুলটা ধরায়ে দেন। আমি এক্ষুণি কান ধরে শিখে নেব যে এটা ভুল হয়েছে। কোনো অনুবিধা নাই। ভুল করতে আমার লজ্জা নাই। আমি তো ‘বুদ্ধিজীবী’ না। আমার নাম তো নিয়মিত প্রথম আলোতে দেখেন না। কিন্তু, এখন [বিপদের সময়] এখানে এসে সেই আমাকেই দাঁড়াতে হচ্ছে। যাঁদের নাম পেপারে-টিভিতে দেখেন, তাঁরা এখন কোথায়? শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছি না। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছি। কোথায় তাঁরা? তাঁরা এখন ‘ভুল’ করতে রাজি না। কিন্তু, আমি ভুল করতে আগ্রহী। কেননা, ভুল না করলে শেখা যায় না। জ্ঞানী-গুণী লোকেরা বহুকাল আগেই বলেছেন, যে ভুল করে না সে কিছুই করে না।
ঘটনাটা কী তাহলে? ‘শিক্ষক-রাজনীতি নিষিদ্ধ করিতে হইবে’ কথাটার মানে কী? এটা তো সিদ্ধ নাই। এটা তো নিষিদ্ধ আছেই। মানে সিদ্ধ অবস্থায় নাই। এটা অসিদ্ধ আছে। এটা চাল আছে, ভাত হয় নি, অসিদ্ধ। এটা তো আইনত সিদ্ধই নাই! কী করে আইন করে নিষিদ্ধ করবেন তাহলে! তাহলে ঘটনাটা কী? ঘটনাটা হচ্ছে, ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ/আইন আমাদের টিচারদেরকে সুযোগ দিয়েছিল যে আমরা ভোট করতে পারব। এটার উদ্দেশ্য খুবই মহান ছিল। পাকিস্তান আমলে বিশ্ববিদ্যালগুলোর অবস্থা আরও খারাপ ছিল। আরও খারাপ। ঠিক আছে? এ কারণে, ঐ অভিজ্ঞতা থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে অত্যন্ত মহৎ এই আইন পাশ হয়। এখনও পর্যন্ত এই আইন তার সব সীমাবদ্ধতা নিয়েও অতিশয় মহৎ। আমি চিন্তা করতে পারি না এর চেয়ে মহৎ আইন আর কী হতে পারে আমাদের মতো দেশে। যা আছে তার মধ্যে। এত মহৎ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটা প্রতিষ্ঠান সব অন্ধকারের মধ্যেও, এখনও, বাংলাদেশে ভরসার এবং আশার জায়গা হতে পারে। সেটা এই আইনের জোরে।
ঐ আইন কার জোরে হয়েছে? কোনো ভদ্রলোকের বা কোনো মহান ব্যক্তির সদিচ্ছার জন্যে না। মুক্তিযুদ্ধের জন্যে। বাংলাদেশের ৭ কোটি/৮ কোটি মানুষের রক্তক্ষয়ী লড়াই এর পেছনে আছে। সেই লড়াইয়ের কারণে ঐ সরকার বাধ্য হয়েছে এই ধরনের একটা আইন করতে। ঐ সরকারের আরও অনেক এরকম মহান কাজ আছে। বাধ্য হয়ে যেটা করেছেন তাঁরা। তাঁরা কিন্তু কী জিনিস, আপনি এখন বুঝতে পারবেন। আওয়ামী লীগের কথা বলছি। আজকের আওয়ামী লীগ কী আপনি জানেন। বাহাত্তরের আওয়ামী লীগ এই জিনিস ছিল। সব রাজনৈতিক দল এই জিনিসই বটে। আজকে নতুন না।
জরুরি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পরে আমাকে এগুলো শিখতে হয় না। আমাদের যাঁদের চোখ আছে, আমরা যাঁরা এসব রাজনীতি দীর্ঘকাল ধরে করেছি, আমার বহু আগে টের পেয়েছি, বহু আগে ছেড়েও এসেছি। আজকে সাত-আট বছর হলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ওপেনলি বলছি যে আমি লাল-নীল কোনো দল করি না। ডিজওন করি। আমি মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় দুর্দশার জন্য এই লাল-নীল-হলুদ দলই দায়ী। আমি গত কয়েক বছর ধরে, পার্সোনালি, এই কথা বলে যাচ্ছি। সর্বত্র। সম্ভাব্য সর্বত্র। আমার কথা আপনারা সব জায়গায় শুনতে পান না। আমি ‘তালিকাভুক্ত বুদ্ধিজীবী’ নই বলে। আমাকে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছ থেকে অথবা মতিউর রহমানদের কাছ থেকে এটা শিখতে হয় নাই যে শিক্ষক-রাজনীতির জন্যেই আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবস্থা।
কিন্তু, আমি ওনাদের মতো করে বুঝি না। আমি বাস্তব জায়গা থেকে দেখতে চাই। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও অনেকেই এগুলো জানেন, এগুলো বোঝেন। কথা বলা শুরু হলে তাঁরাও বলবেন। আমার তাই বিশ্বাস। এবং যদি আমরা শুভ কাজকে উৎসাহিত করতে পারি, আমাদের সমাজ যদি পারে, আমাদের রাষ্ট্র যদি পারে, রাষ্ট্রে এবং সমাজে শুভশক্তির অবশিষ্ট যদি এখনও থেকে থাকে তাহলে পরে আরও অনেকেই মুখ খুলবেন আমি জানি। এখন অথবা সামনের দিনগুলোতে। অথচ, এই মুখ খোলার কারণে গত অনেক বছর ধরে আমাকে এই ক্যাম্পাসে, শিক্ষক-সমাজে নচ্ছার হিসেবে এবং অচ্ছুৎ হিসেবে, একটা কলঙ্ক হিসেবে অনেকেই মনে করেন।৫ আমি সেটা আমার জন্যে গৌরবের মনে করি। আর কিছু না পারি, এইটুকু তো পারি যে লেফট-রাইট করি না। মস্তিষ্ক বন্ধক দেই না কারও কাছে। আজ থেকে কয়েক বছর আগে আমাদের ডিপার্টেমেন্টের একটা সঙ্কলনে লিখেছিলাম, ‘মস্তিষ্ক কারো কাছে বর্গা দিব না’। এইটা হচ্ছে পজিশন। ফলে আমরা এগুলো আগে থেকেই জানি।
তো, ঘটনাটা কী? ঘটনাটা হচ্ছে, ১৯৭৩-এর আইন শিক্ষকদেরকে সুযোগ দিয়েছিল: আমরা ভোট করতে পারব। বলা ছিল: শিক্ষকরা নিজেরাই নিজেদের মতো করে বিশ্ববিদ্যালয় চালাবেন। স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে চলবেন। স্বাধীন থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে সরকারের কোনো আইন, সরকারের কোনো এজেন্সি বা অন্য কোনো ফোর্স লিগালি, ইলিগালি কোনো চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না। এটা ছিল ঐ অধ্যাদেশের স্পিরিট। ফলে কোন শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন, সেটা শিক্ষকরা নিজেরাই ঠিক করবেন। কিভাবে ঠিক করবেন? ভোট দিয়ে ঠিক করবেন। ডেমোক্রেটিকালি। উদ্দেশ্য খুব সৎ। খুব মহৎ। আচ্ছা। কারা ভোট দেবেন? সব মাস্টাররা ভোট দেবেন। কাদেরকে ভোট দেবেন? যাঁরা নির্বাচনে দাঁড়াবেন। কারা নির্বাচনে দাঁড়াবেন? যাঁরা নিজেরাই দাড়াবেন, তাঁরা। এবং যাঁদেরকে আপনি-আমি ‘সমমনা’ শুভানুধ্যায়ী কয়েকজনে মিলে দাঁড় করিয়ে দেব, তাঁরা। এইটা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনের আদি প্রক্রিয়া। নিয়ম হচ্ছে: সমমনের শিক্ষকেরা মিলে কারও নাম প্রস্তাব করতে পারবেন। যাঁর নাম প্রস্তাব করা হচ্ছে, তাঁর সম্মতিক্রমে অবশ্যই।
সমমনা শিক্ষকরা মিলে কাউকে দাঁড় করানোর সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তী সময়ে নিয়ম দাঁড়িয়ে গেল, সমমনা শিক্ষকরা একটা ‘প্যানেল’ দিতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে কিন্তু ‘প্যানেল’ বলে কিছু নাই। দল তো দূরের কথা। ওখানে আমি ইন্ডিভিজুয়াল, আপনি ইন্ডিভিজুয়াল, তিনি ইন্ডিভিজুয়াল। সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমরা নানা ব্যক্তি একটা নির্দিষ্ট পদে কমপিট করছি- ডেমোক্রেটিকালি, ফ্রেন্ডলি। আমরা-আমরা; নিজেরা-নিজেরা। নো পলিটিকাল পার্টি, নো স্টেট, নো প্রেশার, নো প্রপাগান্ডা। ঠিক আছে?
এই ‘সমমনা’ লোকদের জিনিসটা অচিরেই সমমনাদের ‘প্যানেল’ হয়ে গেল। তাহলে এবার আপনার প্যানেল আর আমার প্যানেল আলাদা করব কেমন করে? দল তো করা যাচ্ছে না। দল তো করা বেআইনি। দলের কথা তো নাই-ই। ফলে, দলের নাম তো লেখা যাচ্ছে না আইনত। তাহলে, আমরা যে একটা আলাদা ‘বংশ’ আর আপনি যে একটা আলাদা ‘বংশ’- এটা তাহলে বুঝাব কিভাবে? তার জন্যই, আমার প্যানেল-শিট ছাপানোর কাগজটা লাল রঙ করে দিলাম, আপনার প্যানেলের কাগজটা আপনি নীল রঙ করে দিলেন। এরকম গোলাপি রঙও হলো। এভাবে, প্যানেল-শিট দিয়ে বলা আমরা আরম্ভ করলাম, অমুক প্যানেলে ভোট দিন। ‘ইসলামিক মূল্যবোধ’ওয়ালাদের প্যানেল। ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা’ওয়ালাদের প্যানেল। অথচ, যেমনটা মাত্রই বললাম, এরকম প্যানেল-শিট ছাপানোটা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের মধ্যে কোথাও আদৌ উল্লেখ করা নাই। বিদ্যমান আইনের ব্যাখ্যায় বরঞ্চ এই কথাই বলে দেওয়া যেতে পারে যে এরকম প্যানেল-শিট ছাপানো যাবে না। নির্বাচনী সভাও করা যাবে না। দল করার, তথা দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার, তো প্রশ্নই ওঠে না। শিক্ষক-রাজনীতিটা আদৌ তাহলে চলছে কোন আইনে? এই যে লাল-নীল প্যানেল হয়ে গেল, প্যানেলের রঙ দিয়ে এইবার আমি হলাম লাল দল, আপনি হলেন নীল দল। সাদা দল, হলুদ দল- এগুলো হলো।
তারপারও শান্তি হলো না। তা-ও চেনা যাচ্ছে না, কে কোন দল। আরও ভালো করে চেনা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হাজার টিচার। এক হাজার জনকেই ‘ছাগল’ হতে হবে। এক হাজার জনকেই দলের কমান্ডের অধীনে আসতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কিছু কিছু বেয়াদব আছে। তারা পুরা ছাগল হচ্ছে না। তাঁরা এখানে-ওখানে উল্টাপাল্টা ভোট দিয়ে দিচ্ছে মাঝেমধ্যে। মাঝেমধ্যে কেউ কেউ আবার ভোটই দিতে আসছে না।
এঁদেরকে তো আরও সাইজ করতে হবে। তখন কী করতে হবে? প্রত্যেকেই কে কোন দল করছেন না করছেন, আমাকে একদম লিখিতভাবে নিশ্চিত হতে হবে। কারণ কী? কারণ, আজকে আপনি লাল দল, পরের দিন গনেশ উল্টায়ে গেল, ঘুমের থেকে উঠে আপনিও চুলটা আঁচড়ায়ে, অন্য একটা জামা গায়ে দিয়ে নীল দলের মিটিঙে চলে গেলেন। [গিয়ে] বললেন, আমি নীল দল। [দর্শকশ্রোতার হাসি] বিশ্বাস করুন। আল্লাহর কসম বলছি। এই জিনিস নিজের চোখে দেখলাম। অনেক বার। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এটা আছে। সুতরাং, দলের নেতারা প্রমাদ গুনতে লাগলেন। এদেরকে সামলানোর জন্য আরও উপায় চাই। ‘ব্যাটা, তুমি যে আমার দল কর, তার প্রমাণ চাই।’ সুতরাং, সদস্যপত্র চাই। হ্যাঁ, তাঁরা সদস্যপত্রও চালু করেছেন। নমুনা আছে। ঘটনা সত্য।
শিক্ষক-রাজনীতি আমিও করেছি। সরল বিশ্বাসে। মতিউর রহমান নিজামীর মতো; সরল বিশ্বাসে। ১৯৯৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ঢুকি, দেখলাম: শিবির ছাড়া কিছু নাই। হাঁটতে গেলেও শিবিরের অনুমতি লাগে। উঠতে-বসতে অনুমতি লাগে। আমি তো ‘মুক্তিযুদ্ধ’ করে আসছি ছোটবেলা থেকেই, তাই না? আমার কাছে মনে হলো, এত বড় কথা। আমি স্বাধীনতার সৈনিক বেঁচে আছি। একজন থাকলেও আছি। সুতরাং আমি কী করব? শিবিরের বিরুদ্ধে যে দল আছে, ঐ দল আমি মনেপ্রাণে করা শুরু করে দিলাম। সভায় ডাকলেন। সভায় গেলাম। গিয়ে দেখি ১৫ জন। ১৬/১৭ জন। ২০ জনও হয় না। ৩০ জন হলে দলের নেতারা খুব খুশি হন। আজকে বড় মিটিং। তখন থেকে আমি ঐ দল করা শুরু করলাম। অচিরেই দেখলাম, বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ধারণা, এবং এর পরিচালনাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থানের প্রশ্নে শিবির যা, অতীতে মৈত্রীও তাহাই ছিল, জাসদও তাহাই ছিল।
বাস্তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নে, লাল দল যা, নীল দলও তাই। মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধে ‘বিশ্বাসী’দের দলও যা, স্বাধীনতাবিরোধীদের দলও তাই। একই জিনিস। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরা পরিচালনা করেন এবং করতে চান হুবহু একই রকম পদ্ধতিতে। তাঁরা কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তন চান না। তাঁরা কেউ লেখাপড়াটা চান না। তাঁরা কেউ গবেষণা চান না। তাঁরা কেউ নিজেরা পড়াশোনা করেন না। তাঁরা কেউ চান না, শিক্ষকরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করুক, পড়াশোনা করুক। তাঁরা এটা চান যে: শিক্ষকরা শুধুমাত্র নিজেদের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকুন; আর-কারও কাছে দায়বদ্ধ না থাকুন। এটা তাঁরা কেউ চান না। ফলে আমি বুঝে ফেললাম: সব দলই এক। সো আই ডিসওন। এই জন্যেই আমি শিক্ষক-রাজনীতির পরম্পরা বহন করতে অস্বীকার করেছি। আমি নাই এর মধ্যে। আমি নাই এর মধ্যে। এইটুকু বুঝতে আমার যে কয়দিন লেগেছে, সে কয়দিনই করেছি শিক্ষক-রাজনীতি।
তাহলে এই হচ্ছে আমাদেল লাল-নীল দলের ইতিহাস। এবং আইনগত প্রক্রিয়ার জায়গা থেকে ব্যাখ্যা। তার মানে, আরেক বার বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের রাজনীতি তো বেআইন-ই আছে। একে আবার নতুন করে কী বেআইনি করতে হবে? তিয়াত্তরের আইনকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। ঠিক আছে? [কেননা, এখানে তার আকাঙ্খা হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কর্ম-পরিচালনা কাঠামোয় যেন কেউ বিশেষ মাতব্বর হয়ে উঠতে না পারেন, এবং বেশির ভাগ শিক্ষকের অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে যেন সব কাজকর্ম পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার জন্য এই ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক শুঁড়বিন্যাস
বলেন তো, তিয়াত্তরের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের যে স্পিরিট, সেই স্পিরিট, এবং তার পেছনে মুক্তিযুদ্ধের মতো একটা মহান ঘটনা, তার পেছনে গোটা ষাটের দশক ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা বড় অংশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা বাঙালি জাতির জন্য, মুক্তিযুদ্ধের জন্য- এই সব কিছু উড়ে গেল কেমন করে? সব কিছু পাপ হয়ে গেল কেমন করে? ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ করে কোনো মহাপ্রলয় তো এখানে ঘটে নি। তাহলে বলেন: কী দিয়ে সব হাওয়া হয়ে গেল?
এইটা যদি আপনাকে বুঝতে হয়, তাহলে আপনাকে দেখতে হবে ১৯৭২ থেকে এ পর্যন্ত বিদ্যমান আমাদের রাষ্ট্রের কাঠামোটাকে। আমাদের রাষ্ট্র-রাজনীতির কাঠামোটাই মূলত এর জন্য দায়ী। একটু আগে আমি বলেছি: রাষ্ট্র তার শুঁড় ঢুকিয়ে রেখেছে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। শুঁড় মানে পাইপলাইন। ঐ পাইপলাইন দিয়ে প্রেশার আসে। ঐ পাইপলাইন দিয়ে হালুয়ারুটি আসে। দু-একজন খাওয়া শুরু করলেন প্রথম প্রথম। সংখ্যা বাড়তে লাগল। খাওয়া-দাওয়া এবং প্রেশারের কাছে মাথা নত করা মানুষের সংখ্যা।
রাষ্ট্র এবং তার শুঁড়বিন্যাসই এর জন্য দায়ী। সরকার এবং রাজনৈতিক দল- তাঁরা যত মহানই হোন এবং যে তন্ত্রীই হোন; যায় আসে না। তাঁরাই এই অবস্থার জন্য দায়ী। যে রাজনৈতিক দল সরকারে নাই, ছিলেন না, তাঁদের দায় মোটেও কম নয়। কারণ তাঁরাও রাষ্ট্র। তাঁরা রাষ্ট্রের পাইপলাইনের মেম্বার। তাঁদের বাড়িতে বাড়িতে রাষ্ট্রের পাইপলাইন যায়। কখনও সমন নিয়ে যায়। কখনও ওয়ারেন্ট নিয়ে, বন্দুক নিয়ে। কখনও আবার হালুয়ারুটি নিয়ে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যেকোনো ব্যাখ্যায় পলিটিকাল পার্টি মাত্রই রাষ্ট্রের প্রধান একটা অঙ্গ। বাস্তবেও তাই। নানাভাবে তাঁরা রাষ্ট্র-পরিচালনার অংশীদার বটেন। যাঁরা ছোট দল, তাঁরা বড় দলের লেজ, বি টিম, সি টিম। ফলে, তাঁরাও হালুয়ারুটির কানাকড়ি, ভগ্নাংশ, অল্পসল্প পান।
এবং রাজনৈতিক দলের কেউই, তিনি যে তন্ত্রীই হোন, এই প্রক্রিয়া চ্যালেঞ্জ করেন নি। এক্সপ্লেইনও করেন নি এতটা ডিটেইলে। তাঁদের প্রয়োজন পড়ে নি। কারণ কী? কারণ, রাজনীতি মানেই হালুয়ারুটি। রাজনীতি মানেই ক্ষমতা। রাজনীতি কথাটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অ্যাকাডেমিক জায়গা থেকেই আপনি দেখেন, অথবা আপনার আক্কেল থেকে দেখেন, আপনি দেখবেন, রাজনীতি মানেই হচ্ছে, মোট ক্ষমতা কে কতটা প্রয়োগ করবে, কার ওপরে প্রয়োগ করবে, ক্ষমতার ভাগাভাগিটা কী হবে, আর যাঁরা ক্ষমতার শিকার হবে, যাঁদের ওপরে ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে, তাঁদের ভাগাভাগিটাই বা কী হবে? এই সংক্রান্ত আইনকানুন-অ্যারেঞ্জমেন্ট সমুদয়ের নামই রাজনীতি। আর কিছুই না। শাদা চোখে তাকিয়ে দেখেন।
তো, যাঁরা রাজনৈতিক দল করেছেন, তাঁরা তো এই কাজই করেছেন। পাকিস্তান আমলেও করেছেন। ব্রিটিশ আমলেও করেছেন। বাংলাদেশে আমলেও করেছেন। আমরা এখন জ্ঞানী। বাংলাদেশের মানুষ এখন অনেক জ্ঞানী। ‘এখন কোথাও আর কোনো কিছু গোপনীয় নাই’। বাংলাদেশের মানুষ গত ৩৫ বছর ধরে নিপীড়িত হয়ে, নির্যাতিত হয়ে, একটা লাভ হয়েছে। হাড়ে হাড়ে সবাই এখন সব জানেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিয়নও জানেন, ঘটনা কী ভিসির? এখন বঙ্গভবনের পিয়নও জানেন, ইয়াজউদ্দিনের ঘটনা কী। এইটা হচ্ছে লাভ। বাংলাদেশের মানুষ এই কারণে রাজনৈতিক দিক থেকে অসম্ভব জ্ঞানী। এবং এইটা হচ্ছে সব সময়, সব যুগে ক্ষমতাবান মানুষদের জন্য একটা অসুবিধা।
আমি সেই আলোচনায় আরেক দিন যাব। আমাদের ইচ্ছা আছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে আমরা এক দিন আলোচনা করব। আরেকটা এজেন্ডা। এই সরকারের, সুশীল সমাজের, মিডিয়ার। এবং সময়মতো-বুদ্ধিজীবীদের, যাঁরা সময়ে চুপ, অসময়ে নীরব বা সরব। [দর্শকশ্রোতার হাসি] দুই রকমই। এরা মহা কাব্যিক জিনিস। মহা হেঁয়ালিপূর্ণ জিনিস। রহমস্যময় জিনিস। ঐ নিয়ে অন্য দিন না হয় আলোচনা করব?
ঐ যে ভিসি নিয়োগ দিয়ে, মঞ্জুরি কমিশন দিয়ে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় দিয়ে, পলিটিকাল পার্টি দিয়ে, এবং তার পরে রাজনৈতিক ছাত্রদের দল দিয়ে, আপনি যে বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও করে ফেলেছেন, শুঁড় ঢুকিয়ে দিয়েছেন, পাইপলাইনে খাবার আসছে, পাওয়ার আসছে, প্রেশার আসছে, ভয় আসছে, এবং আপনার লাঠিয়াল-বাহিনী ক্যাম্পাসের মধ্যে আছে, ছাত্রসংগঠনের ক্যাডার–বাহিনী, ক্যাডারপুল, যাঁরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ক্যাম্পাসের মধ্যে মাস্তানি করবে, সবার আগে তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয়কে সাইজ করা শুরু করেছিল রাষ্ট্রের তরফ থেকে যে টিচাররা সবাই ‘লাইনে’ আছেন কিনা, ‘দল, সোজা হবে, আরামে দাঁড়াবে’, এটা আছে কিনা, এইটা দেখার দায়িত্ব ছিল প্রাইমারিলি পলিটিকাল পার্টির ক্যাডার-বাহিনীর। তারা এগুলো দেখতেন এবং টিচাররা যদি কেউ বিশেষ অন্য রকম কিছু করতেন, তখন ওনারাই গিয়ে ‘সাইজ’ করতেন। ভয় দেখিয়ে। হুমকি দেখিয়ে। তারপরে ‘অনুরোধ’ করে, “খুব একটা ভালো হচ্ছে না, স্যার!” এ রকম হুমায়ুন আজাদের লেখায় দেখেছি। প্রাচীন কালে, শিক্ষকের বাসায় গুপ্ত বাহিনীর (গুপ্ত পলিটিকাল পার্টির) লোকেরা কাটা রাইফেল-টাইফেল নিয়ে গিয়ে বলেছে, “লাইনে আসেন, বে-লাইনে লেখালেখি করবেন না”, ইত্যাদি প্রভৃতি।
পরে এদের সঙ্গে আমাদের মাস্টারদের নিজেদের দল, এমপি, লোকাল এ্যাডমিন্সট্রেশন, পুলিশ-প্রশাসন, মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মঞ্জুরি কমিশন, এবং ভিসি-নিয়োগের শুঁড়-সব মিলে আমরা এই জায়গাটাতে দীর্ঘকাল ধরে, তিল তিল করে, এসে পৌঁছেছি। কোনো মহাপ্রলয়ের কারণে না।

পিএইচডি-প্রমোশন-রাজনীতি: বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণপ্রথা
নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে শিক্ষকদের প্রমোশন। প্রমোশনের প্রক্রিয়া। পিএইচডি লাগবে। এইটা হলো তাবিজ। মাদুলি। এই মাদুলি আপনি যদি গলায় একবার পড়েন, আপনাকে জিন-ভুত-দৈত-দানব কেউ ধরতে পারবে না। একবার যদি এই মাদুলিটা আপনি গলায় লাগান, তাহলে আপনি লেকচারার থেকে সহকারী অধ্যাপক হবেন তাড়াতাড়ি। সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক হবেন চার-পাঁচ বছর আগেই। অন্যদের তুলনায়। যাঁদের মাদুলি নাই, তাঁদের তুলনায়। ঐ একই তাবিজ দিয়ে। কোনো কমনসেন্স এ রকম বলবে না। যে পড়া দিয়ে তুমি একবার পরীক্ষায় পাশ করেছ, ঐ একই পড়া দিয়ে বারবার পাশ! আশ্চর্য নিয়ম! সব বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। এবং কোনো প্রফেসর এই নিয়ে কথা তোলেন নি। কারও আত্মমর্যাদায় লাগে নি। আমি যে একই ডিগ্রি দিয়ে বারবার পাশ দিচ্ছি, এটা কারও ইজ্জতে লাগে নি। তাঁরা এরকম ইজ্জতওয়ালা প্রফেসর। আর, ঐ পিএইচডির মধ্যে কে কী সৃজন করেছেন, কে কী থিসিস লিখেছেন, সে তো এখন সবাই জানেন।
পিএইচডি এখন হাসাহাসির জিনিস। এক দিন চারুকলার এক টিচার আমাকে বলছেন গল্প করতে করতে, “এখন তো পিএইচডি অন্য রকম। চাল আর ডাল মিশিয়ে দিয়ে বেছে আলাদা করতে হয়!…পাকা চুল থেকে কাঁচা চুল আলাদা করতে হয়।” উনিই এই দুইটা উদাহরণ দিলেন। আমার বানানো না। এইটার নাম পিএইচডি। এর সাথে মেথডোলজি লাগতে হয়, আর তাত্ত্বিক কাঠামো লাগাতে হয়। তারপর থিসিসটা লিখলেই পাশ। কারণ, সবই তো ‘আমরা আর মামুরা’। দল-টল-নাট-বল্টু-কাঠামো তো রেডিই আছে। আর, কাঠামো যদি রেডি না থাকে, এবং আপনি যদি পিএইচডি-থিসিস জমা দেন, ঐ থিসিস পাশ হবে না। আপনি নিশ্চিত থাকেন। তবে এ রকম এগজাম্পল আদৌ থাকলেও খুব কমই থাকার কথা। অত বড় আহাম্মকি কেউ করে না। আমার জানা নাই, কেউ করেছেন কিনা কখনও। ভবিষ্যতে আমি যদি না করি। [দর্শকশ্রোতার হাসি] কিংবা আরও দুই-একজন যদি না করেন।
পিএইচডি ছাড়া প্রমোশনের জন্য আর কী লাগে? প্রকাশনা লাগে। জার্নালে গবেষণামূলক প্রবন্ধ। আমি যদি আপনার লোক হই, আর আমি যদি বিচিত্রা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে থাকি, ঐটা গবেষণা-প্রবন্ধ। আর, আমি যদি আপনার লোক না হয়ে থাকি, আর ঐটা যদি কোনো জার্নালেও ছাপা হয়ে থাকে, তাহলে আপনি বলবেন, ঐটা কী জার্নাল? এই জার্নালের ঠিকানা, কুলজি, এগুলো কী? রিভিউ হয়? হ্যান হয়? ত্যান হয়? আইএসএসএন নম্বর আছে? [মাঝখানে রটে গেল, আইএসএসএন নম্বর থাকলে পরে ঐটা হচ্ছে ‘স্বীকৃত জার্নাল’। কারণ, মাঝখানে অনেকখানি প্যাঁচ খেয়ে গেছে যে ‘স্বীকৃত জার্নাল’ কোনটা? বিচিত্রা? দৈনিক পত্রিকা? নাকি অমুক জার্নাল, তমুক জার্নাল? তখন এই আইএসএসএন-নিয়মটা সাম্প্রতিক সময়ে রটে গিয়েছিল। তার মানে, আইএসএসএন কী জিনিস, খায় না মাথায় দেয়, সেটা আমাদের প্রফেসররা জানেন না! ফলে, হয়তো ওনাদের ধারণা হয়েছে, যে জার্নালে আইএসএসএন নম্বর থাকে, সেইটাই মহা জার্নাল। আইএসএসএন হচ্ছে স্রেফ তালিকাভুক্তকরণের একটা প্রক্রিয়া। আর কিছু না। তালিকাটা সকলের জন্য সুলভ রাখা হয়। গবেষকদের খুব কাজে লাগে। প্যারিসে, ওখানে একটা বিবলিওগ্রাফি টাইপের একটা প্রতিষ্ঠান আছে, যাঁরা চায়, সারা পৃথিবীতে যা কিছু জার্নাল বের হয় সবই তাঁদের নলেজে থাক। পারলে একটা করে কপিসহ। হার্ড অথবা সফট। যেন তাঁদের জানা থাকে পৃথিবীতে কোথায় কী হচ্ছে। ভালো হোক, মন্দ হোক, যা-ই হোক। কিছুই যেন মিস না হয়। তাহলে তাঁদের গবেষণা করতে সুবিধা হয়। এইটা হচ্ছে ওনাদের ভিশন। আর, আমরা এখানে ভাবছি নম্বর পাওয়াটা একটা বিরাট ব্যাপার। অথচ এটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাডার্ড সিরিয়াল নাম্বার। একটা সিরিয়াল নম্বর। আর কিছু না।]
আমার এক বন্ধু, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার, এখন কানাডাতে ডিগ্রি করছেন, উনি একদিন বলেছিলেন, যখন উনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে এসেছিলেন প্রথম, তখন ওনার মনে হয়েছিল, ‘ওরেব্বাপ, এত বড় বড় গাছ! বিশ্ববিদ্যালয় তাহলে কত বড় জিনিস।’ তার পর যখন এক বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন, এক সময় তার মনে হলো, গাছ যেরকম বড় হয়, লেকচারররা সেরকম প্রফেসর হয়। ন্যাচারালি। কোনো কিছু অর্জন করা লাগে না নতুন করে। ঐ রিক্রুটমেন্ট হওয়া পর্যন্তই। ঐ ধামাধরা পর্যন্তই। তার পর একবার ঢুকে গেলে, আপনি আজকে লেকচারার আছে, কালকে ‘প্রাকৃতিকভাবে’ প্রফেসর হবেন। অলমোস্ট ন্যাচারালি। খুব মহান উক্তি। আমি একটা কোনো দিন ভুলে যাই না।
প্রমোশনের মধ্যে আরেকটা রাজনীতি আছে। এখানে একটা বর্ণপ্রথা আছে। চতুর্বর্ণ প্রথা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র। মেইন চারটা ক্যাটেগরি। প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং লেকচারার। চুতর্বর্ণ-প্রথা। যাঁরা লেকচারার, তাঁদের লজ্জার শেষ নাই: ‘আমরা লেকচারার’। [দর্শকশ্রোতাঁদের হাসি] যাঁরা প্রফেসর, তাঁদের ডাঁটের শেষ নাই: ‘আমরা প্রফেসর’। সঙ্গে আবার ড.। ইশকুলে থাকতে আমরা শিখেছিলাম গ্রামারের বইয়ে, কারেকশন শেখার সময়: প্রফেসর এবং ডক্টর এক সঙ্গে লিখতে হয় না। ভুল হয়। ব্যাকরণের ভুল হয়। ‘কিসের ব্যাকরণের ভুল। আমি প-ও আছি, ড-ও আছি, আবার লিখব না! লোকে জানবে না!’
ফলে, প্রফেসর ডক্টর ইয়াজউদ্দিন আহমেদ। খোদ হিমসেল্ফ। প্রফেসরও লেখেন ‘ডক্টর’ও লেখেন। উনি আমাদের রাষ্ট্রপতি। বহাল আছেন। এখনও আছেন। মাঝখানে বহু কিছু করেছেন। কিন্তু এখনও বহাল তবিয়তে আছেন। ঐটার নাম হচ্ছে: ‘ইয়াজউদ্দিন সিনড্রোম’। এই বিদ্যার নাম। এত কিছু করার পরেও উনি বহাল তবিয়তে রাষ্ট্রপতি আছে।
আমাদের প্রথম আলো একটা রিপোর্ট করেছিল। ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ছেলে নাকি সরকারের জায়গায় না কার জায়গায় পেট্রল পাম্প না সিএনসি-র পাম্প বানিয়েছেন, না কী, সব নয়ছয় করেছেন। পাম্পের ছবিও দিল প্রথম আলো। প্রথম পাতায়। তারপর চেপে গেল: না, ইয়াজউদ্দিন নিয়ে এখন বেশি কিছু বলার দরকার নাই। এখন অসময়। ঐটা নিয়ে বলার সময় না।
দুর্নীতি হয় হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদও হবে। এবং ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ছেলের পাম্পও থাকবে। রিপোর্ট একবার অত বড় করে হয়েও সবাই ভুলে যাবে। ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা খুব জরুরি দরকার। এটা সংবাদপত্র পাঠক হওয়ার জন্য একটা আবশ্যিক শর্ত। আপনি যদি আগের দিনের পত্রিকা ভুলে না যান, তাহলে পরের দিন অত বড় পত্রিকা, ২৪ পাতা, আবার কেমন করে পড়বেন? আগের দিনটা ভুলে যেতে হয়। এটা ‘নিয়ম’ আছে। তবু, আলোচ্য প্রাণীটা যেহেতু মানুষ, তাই কিছু কিছু বেয়াড়া লোকের স্মৃতি বেয়াড়াভাবে তাজা থাকবে, এবং বেয়াড়া জায়গায় বেয়াড়া কথা মনে পড়েও যাবে। এবং তারা সেটা বলবেও। চাইলে আপনি-আমি যে কেউই এ রকম অতীব প্রয়োজনীয় বেয়াড়ামি করতে পারি। করাটা দরকার। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদ্য-পদত্যাগী উপদেষ্টা (তার মানে অথেনটিক পার্সন, অ্যান অথরিটি টু বি কোটেড) সুলতানা কামাল সেদিন বলেছেন, যে মেয়েরা, যে নারীরা সমাজে ‘বেয়াদবি’ করেছেন, তাঁরাই কিছু একটা হতে পেরেছেন। তার মানে, ‘বেয়াদব জিন্দাবাদ’। ‘বেয়াদবি’ই রীতি হওয়া উচিত। তো, এভাবে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বেয়াদবি এখন ‘অনুমোদিত’ হলো। তাই না? ঘটনা সত্য। তাঁরা সব কথা ঠিক বলেন না, কিছু কিছু কথা ঠিক বলেন। যেগুলো ঠিক বলেন, সেগুলো বাঁধিয়ে রাখা উচিত। [দর্শকশ্রোতার হাসি]
তারপর, ধরেন, অ্যাজাম্পশন বা অনুমানটা হচ্ছে, বুড়ো হওয়া মানে জ্ঞানী হওয়া। আপনি যা-ই-হন, এবং যা-ই করেন। সারা বছর কী লিখেছেন না লিখেছেন তা দেখার দরকার নাই। কী ধরনের জীবন যাপন করছেন, তাও জানার দরকার নাই। প্রবীণ মানে প্রাজ্ঞ। তারপর ধরেন যে প্রমোশনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বলার কিছুই নাই। আমি কেমন পড়াই, সবচাইতে বেশি কে বোঝে? আমার ক্লাসরুম। হাড়ে হাড়ে বোঝে। এবং মানুষের বাচ্চা তো, এগেইন, অদ্ভুত প্রাণী এইটা। ক্রিয়েটিভ। জন্মসূত্রে ক্রিয়েটিভ। এর পক্ষে নন-ক্রিয়েটিভ হওয়া সম্ভব না। নন-ক্রিয়েটিভ হওয়া সম্ভব, ইফ ওনলি দেয়ার হ্যাজ বিন এ ভেরি লং হার্ড ট্রেনিং।
লম্বা ট্রেনিং আমরা পাই। ক্লাস ওয়ান থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত এ ট্রেনিং। মাথা কেমন করে না খাটাতে হয়। চিন্তা কেমন করে না করতে হয়। তিন পাতা পড়ে কেমন করে না বুঝতে হয়। বাবা-মা অথবা টিউশনির টিচার দাগিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত কেমন করে অবুঝ থাকতে হয়। তাই না? এ রকম আরও অনেক কিছু। কেমন করে অনুগত হতে হয়। কেমন করে শুধু অনুকরণ করতে হয় (কবি সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ এটাকে বলেন ‘হনুকরণ’; হনুমান আর অনুকরণ মিলিয়ে)। এগুলোর লম্বা ট্রেনিং আমাদের আছে। এ প্রসঙ্গে আমি একটু আসব আবার পরে।
তো, আমার এই মানুষের বাচ্চারা, ক্লাসরুমের মেম্বাররা, পণ্ডিত হোক বা না হোক, টের পায়। কোন মাস্টার পড়ে এসেছে। কোন মাস্টার পড়ে আসে নি। কোন মাস্টার পড়া বুঝে পড়াচ্ছে। কোন মাস্টার পড়া না বুঝে পড়াচ্ছে। টের পায়। কিন্তু, তাঁদের বলার কিছু নাই। ক্লাসরুম পারফর্মেন্স তো প্রধান জিনিস- মাস্টারির। ফলে, শিক্ষকদের প্রমোশনে এর একটা বড় রোল থাকা উচিত।
বাস্তব কিছু অসুবিধাও আছে। টিচার হওয়ার পরে প্রথম দিকে আমাকে এক সঙ্গে নয়টা কোর্স পড়াতে হতো। প্রতি ব্যাচে নয়খান কোর্স আমি একা পড়াতাম। সর্বোচ্চ-আমার ডিপার্টমেন্টে। সর্বনিম্নরাও পাঁচটার নিচে কেউ নন। তার পরে ধরেন, সারা বছর শুধু ক্লাস ক্লাস ক্লাস ক্লাস। পরীক্ষা পরীক্ষা। পরীক্ষার হলে চোর-পুলিশ খেলা। তার পর খাতা দেখা খাতা দেখা। ট্যাবুলেশন ট্যাবুলেশন। সাধারণ লেখালেখি করার, বিশেষত প্রবন্ধ লেখার, গবেষণা করার, একটা বই লেখার সুযোগ নাই। একমাত্র সুযোগ আছে আপনি কয়েক বছর ছুটি পাবেন-স্টাডি লিভ। পিএইচডি করবেন- ঐ জন্য ছুটি। একবার পিএইচডি করে ফেলতে পারলে, ব্যস, বাকি জীবন আর পড়াশোনা করার দরকার নাই। সুযোগও নাই বাস্তবে। এইগুলো আমাদের ভাবা উচিত-সংস্কারওয়ালাদের। টিচারদেরকে পড়াশোনা করার জন্য টাইম দিতে হবে। টিচিঙের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করতে হবে। রিসার্চের নিয়োগ এবং টিচিঙের নিয়োগ আলাদা করতে হবে। আমি তিন বছর ক্লাসে পড়াব। তার পর চাইলে আমি যেন তিন বছর গবেষণা করতে পারি, তেমন ব্যবস্থা দরকার। ওটাই আমার টিচার হিসেবে কাজ। শুধু পিএইচডি না।
তো এইভাবে আমাদের শিক্ষক-নিয়োগ, আমাদের প্রমোশন, আমাদের লাল-নীল দল, শিক্ষক-নির্বাচন, এ সমস্ত কিছু মিলে আমরা একবার যখন এই ধরনের লোকেরা প্রমোশন পেতে পেতে, নিযুক্ত হতে হতে, প্রফেসর হয়ে যাই, আমাদের মতো লোকদেরকে দিয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয় ভরে যায়, তখন গরুত্বই মানদণ্ড হয়, গুরুত্ব শেষ-শিক্ষার।

বাজার, নৈরাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়
তার পর ধরেন, টিচারদের টাকাপয়সা কামানোর ধান্দা। খ্যাপ মারার ধান্দা। কাউন্সেলিং-কনসালটেশান এগুলো করা। নানান জায়গা থেকে টাকা পাওয়ার অবিরাম চেষ্টা করা। এগুলো আছে। সবাই জানে। সবাই বলছে। টিআইবি রিপোর্ট বের করেছে। প্রফেসর ইয়াহিয়া। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। ওনার নাম দেখেছি পত্রিকায় আমি। উনি একটা গবেষণা করেছেন। টিআইবির পক্ষ থেকে গবেষণা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচাররা কিভাবে কিভাবে ক্লাস নেয় না। অন্য অন্য কাজ করে। আরও অনেক এ রকম গবেষণা নিশ্চয়ই আছে। গবেষণা লাগেও না। ঘটনা সত্য।
টিচারদের তো বেতনভাতা আসলেই কম। টিচাররা অনেক কম বেতন পান। তাঁরা তো বাড়তি টাকার জন্য দৌড়াদৌড়ি করবেনই। শিক্ষকদের বেতন আপনাকে সর্বোচ্চ করতে হবে সমাজে। সর্বোচ্চ মর্যাদা আপনাকে দিতে হবে টিচারদেরকে। প্রাইমারি স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছি না এক্ষেত্রে। প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত টিচারদের হায়েস্ট পেইড হতে হবে। তা যদি না হয়, আপনি শিক্ষার মর্যাদা কী দিয়ে দেবেন? মুখে মুখে মর্যাদা দেবেন?
আপনি সমাজের আদর্শ বানাবেন টাকা কামাই করাকে, সম্মান-মর্যাদা মানে তো তখন টাকা। ক্ষমতা মানেই মর্যাদা। টাকা মানেই ক্ষমতা। গোটা সমাজের আদর্শ হচ্ছে; যেমন তেমন করে যেভাবে পার ড্রইংরুমে দোকান খোলো বেডরুমে ঘুমাও, তা-ও দুইটা পয়সা কামাও। ঘরে ঘরে দোকান বানাও। দোকানদারি ছাড়া কিছু নাই। বাজার ছাড়া কিছু নাই। বেচাকেনা ছাড়া কিছু নাই। টাকা পয়সা কামাই করা ছাড়া কিছু নাই। গোটা সমাজে এটা অ্যাকসেপ্টেড। এটা সেলিব্রেটেড। এটা উদযাপিত, স্বীকৃত। যখন অবস্থা এ রকম, তখন টিচাররা আপনার টাকাপয়সার জন্য কোনো চিন্তা করবে না, এ রকম মনে করা তো ঠিক না। ফলে, তাঁরা করবেন। [না করার যেকোনো উপায়ই নাই, তা তো অবশ্যই নয়। গা ভাসানো ছাড়া পথ আছে বৈকি! কিন্তু কী আর করা।]
এখন টাকা যদি হয়, ছাত্র সালাম দেয়, পিয়ন সালাম দেয়, কর্মচারী সালাম দেয়, রিকশাওয়ালা সালাম দেয়। টাকা যদি না হয়, কারও কাছে আপনি গুরুত্ব পান না। দোকানদাররাও সালাম দেয় না। আপনি দোকনে [গিয়ে] দাঁড়িয়ে থাকবেন, অনেকক্ষণ পর আপনাকে বলবে, ‘কী চাই?’ বাস্তব। সাহেব বাজারে যান। কাজলায় যান। এই হচ্ছে অবস্থা।
তো, এর নাম হচ্ছে অবক্ষয়। এর নাম হচ্ছে মাৎসন্যায়। এর নাম কিন্তু নৈরাজ্য না। তকদির সাহেবরা, আর ও অনেকেই, প্রায় সাবই, ‘নৈরাজ্য’ ‘নৈরাজ্য’ করে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছেন। শিক্ষায় নৈরাজ্য। সমাজে নৈরাজ্য। প্রশাসনে নৈরাজ্য। রাজনীতিতে নৈরাজ্য। নৈরাজ্য আসলে অন্য জিনিস। নৈরাজ্য মানে স্বাধীনতা। যেখানে রাজ্য নাই। যেখানে আপনার ওপরে বস নাই। রাজা নাই। রাজাবিহীন সমাজ- তার নাম হচ্ছে নৈরাজ্য। নৈরাজ্য করতে অনেক উন্নত সমাজ লাগে। সেখানে সবলোকে রাজা হয়। কোনো একজন লোককে রাজ হতে হয় না।
তার নাম নৈরাজ্য। থানা-পুলিশ লাগে না যেখানে। যেখানে উঠতে-বসতে আপনার আইনকানুন লাগে না। যেখানে লোকেরা নিজেরা নিজেদেরকে পরিচালনা করে। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়। এখনও পর্যন্ত এ রকম সমাজ আমরা পৃথিবীতে দেখি নি কোথাও। আদি গ্রিক ভাষায় ‘অ্যানার্ক’ মানে ‘উইদাউট অ্যান আর্ক’। ‘আর্ক’ বলতে শাসক, রাজা। শাসক ছাড়া, রাজা ছাড়া সমাজ অ্যানার্কি। ফলে, আমাদের সমাজের যে অবস্থার কথা বলছিলাম, তার নাম নৈরাজ্য না। এর নাম আপনি বড়জোর বলতে পারেন বিশৃঙ্খলা। এর নাম মাৎসন্যায়। এর নাম অবক্ষয়। এর নাম ধস।
এই জিনিসের মধ্যে গোটা সমাজ পড়েছে। টিচাররাও পড়েছেন। টিচারদেরকে আপনি যদি এর থেকে বের করে আনতে চান, টাকা কামানোর ধান্দা থেকে সরিয়ে আনতে চান, তাহলে আপনাকে ঠিক করতে হবে, গোটা সমাজ কিভাবে চলবে। গোটা সমাজের আদর্শ কী হবে। বাজার? নাকি শিক্ষা। শিক্ষাদীক্ষা মূল্যবোধ এ সব আপনার আদর্শ হবে- জীবনের? নাকি, যেন তেন উপায়ে টাকা কামাই করা, বাজারি জীবনযাপন করাটা আদর্শ হবে? এটা আপনাকে ঠিক করতে হবে তো। সমাজটা কি দোকান হবে? গোটা সমাজ কি বাজার হয়ে যাবে? নাকি সমাজটা মানুষের হবে? সমস্ত মানুষ কি স্রেফ ক্রেতা হবে? বিক্রেতা হবে? নাকি সমস্ত মানুষ মানুষ থাকবে? যাঁরা সমাজে ব্যবস্থাপক, যাঁরা রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক, তাঁদেরকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই আলাপটা কেউ তুলছেন না। ঐ আলাপ যাঁরা তুলছেন না, তাঁরা দয়া করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কার নিয়েও আলাপ করবেন না। কোনো কাজে আসবে না।
নেক্সট পয়েন্ট শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক
সামনে ‘সালাম’। পেছনে ‘শালা’। এই তো এক কথায়। আমার সময়েও দেখেছি, যখন আমি ছাত্র ছিলাম। টিচারদেরকে সামনে দেখা হলে পরেই ‘স্লামালেকুম স্যার’, পিছনে সিগারেটের ধোঁয়া উঠছে। আর, সামনে চলে গেলে পরেই ‘শালা, বদমাইশ, ক্লাস নেয় না’। আমি বলেছি প্রচুর। আমি। মাইসেল্ফ। প্রচুর বলেছি। কেন বলব না? ছাত্ররা এখনও বলে। কেন বলবে না? অবশ্যই বলবে। সামনে বলতে পারে না বলে পেছনেও বলবে না! এ হলো সম্পর্ক।
আর, আমি টিচার। আমি কী? গম্ভীর। আমি কী? বস। আমি হচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজা। ছাত্ররা কী? প্রজা। কর্মচারী। সুতরাং, আমি গম্ভীর স্বর ছাড়া কথা বলব না। [দর্শকশ্রোতার হাসি] ঐ স্বর যদি না দেই, তাহলে আমার রাজত্ব থাকে না। আমি যদি ঘন ঘন হাসি, আর ছাত্রদের সাথে যদি অবাধে, বন্ধুর মতো, বাস্তবিকই সাবালক দুজন মানুষের মতো, মিশি [সেটাই উচিত], তাহলে পরে তো আমার রাজত্ব শেষ। ছাত্ররা বুঝে ফেলবে যে আমার পেট খালি। পেটে বিদ্যা নাই [হাসি]। কলসি ঠনঠন। বুঝে ফেলবে। এ এক আতঙ্ক! যার যেটা যত আতঙ্ক, তারই সেটাতে তত বেশি গর্জন। ক্লাসরুমে। এবং বাইরেও। সে নিজে আতঙ্কিত। সেই কারণে তার কাজ হচ্ছে ছাত্রদেরকেও আতঙ্কিত রাখা যে [গম্ভীর স্বরে] “খবরদার! আমি কিন্তু বাদশাহ নওয়াবজাদা অমুক, এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, সুতরাং….”। এই হচ্ছে আমাদের সম্পর্ক।
এই যদি সম্পর্ক হয়, পড়াশোনাটা কেমন করে হবে? আর যাই হোক, পড়াশোনাটা কেমন করে হবে? আমাদের দেশে সাধনার ধারা আছে। প্রাচীন কাল থেকে, হ্যাঁ। বুদ্ধ ধারা। গোপন ধারা। যার অনেকাংশ গোপন। আজকে যার একটা বড় অংশ লালনদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। বাউলদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। সুফি সাধনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। আগে তান্ত্রিকরাও ছিলেন। এখনও আছেন বৈকি। তার আগে বৌদ্ধ সহজিয়ারা, সাধকরা ছিলেন। ভিক্ষুরা ছিলেন। তাঁরা হাজার বছর আমাদের সমাজে ‘রাজত্ব’ করেছেন। দাপটের সঙ্গে ছিলেন। সেখান পর্যন্ত, গুপ্ত আচারে পর্যন্ত, বৌদ্ধ গুরু তাঁর যে শিষ্য হতো (যে শিষ্য তখনও এবং এখনও গুরুকে মনে করে লর্ড, গুরুমে মনে করে আল্লাহ) সেই শিষ্যকে নিজের সমান মর্যাদা দিতেন।
ফরহাদ মাজহারের (তার সঙ্গে আমার বহু মতপার্থক্য আছে; তারপর, তার কারণে আমার বহু সমালোচনা ছিল, হয়তো আছেও; সেগুলো অন্য প্রসঙ্গ; কিন্তু তার বহু ভালো দিকও আমি সবিনয়ে অ্যাক্সেপ্ট করি; শিখেছি অনেক জিনিস, না বলে উপায় নাই। আরও অন্য অনেকের বেলায়ও ঘটনা তাই। আমার গুরুর ঠিক নাই, অজস্র গুরু আমার, যদিও আমি কারও অধস্তন শিষ্য নই), তো ফরহাদ মজহারের একটা কবিতার চরণ আছে: “গুরুকে প্রণাম করি, এই বঙ্গে গুরুই ঈশ্বর”। এইটা হচ্ছে আমাদের সাধনার ধারা, গত এক হাজার বছরে যে গুরু হচ্ছে আল্লাহ হিমসেল্ফ। এইটা আমাদের সুফি-সাধকরা মনে করেন। ভেতরে ঢুকে খবর নিয়ে দেখবেন। তবে, বৌদ্ধ গুরুদের যে কথাটা বলছি, সেখানে পর্যন্ত (ভিক্ষুক-সঙ্ঘে) গুরু এবং শিষ্যের সমান ভোট দেওয়ার অধিকার থাকত। এবং গুরু শিষ্যকে যেমন চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন, শিষ্যও গুরুকে তেমনি চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন। যুক্তিতে। তর্কে। [গুরুর মতের এমনকি যুক্তিপূর্ণ বিরুদ্ধাচরণকে পর্যন্ত অনুমোদন করা হতো। শিষ্যের কাছে হার মানতে শিখতে এইসব মহাগুরুদের কোনো অসুবিধা হতো না।] আর এখানে? আমি গুরু আপনি শিষ্য- ঐ যে বললাম, রাজা আর প্রজা।
তাহলে লেখাপড়া কিভাবে হবে? আমি যুক্তি নির্ণয় কেমন করে করব? আমি বই লিখলাম। বাই ভালো হলো না খারাপ হলো কে বলবে? আপনি যদি না বলেন? আপনি জ্ঞানী লোকদের বই দেখেন। আপনি প্লেটোর অ্যাকাডেমিক খবর নিয়েন। অ্যারিস্টটলের লাইসিয়ামের খবর নিয়েন। ওদের দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের খবর নিয়েন। এখনও ঐ বাইরের দেশের টিচারদের বই দেখেন। বইয়ের প্রথম ড্রাফট পড়েছে তার ছাত্ররা। তাঁরা মতামত দিয়েছে। সবার আগে।
পয়লা মে [২০০৭] দেখলাম, ইমামউদ্দিন আহমদ চৌধুরী। প্রাক্তন আমলা। উনি স্মৃতিকথা লিখেছেন। “আমার অভিজ্ঞতায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক”। পয়লা মে। প্রথম আলো। পৃষ্ঠা ১১। আমি জাস্ট একটা এগজাম্পল হিসেবে বলছি আর কি। তো, উনি ওখানে লিখেছেন, ওনাদের ছোটবেলায়, ওনাদের স্মৃতিতে, ছাত্র এবং শিক্ষকদের সম্পর্ক কেমন ছিল।

তালিকাভুক্ত বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গ
[সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের একজনের প্রশ্ন: “নামটা কি ইমাম না ইনাম?”] ইনাম না। ইনি হচ্ছেন ইমাম। ইনাম একজন নিয়মিত লেখেন। [কপট গম্ভীর গলায়] উনি লেখেন বড় কলাম। প্রথম আলোতে তিন ক্যাটেগরির কলামিস্ট আছেন। এক ক্যাটেগরির কলামিস্ট হলেন, ‘তালিকাভুক্ত বুদ্ধিজীবী’। বড় বুদ্ধিজীবী। ওনাদের কলাম যত বড় ইচ্ছা, ওনারা তত বড় লিখতে পারেন। কোনো অসুবিধা নাই। উপর থেকে তলা পর্যন্ত কলাম দৌড়াবে। সমস্যা নাই। এটা প্রথম ক্যাটেগরি। দ্বিতীয় ক্যাটেগরি: প্রথম আলোর যাঁরা নিজেদের সাংবাদিক, কিন্তু প্রথম আলোর পরিচয়ে লেখেন না। লেখেন ‘সাংবাদিক’। ওনারা মোটামোটি বারোশ, তেরোশ শব্দ লিখবেন। আমি কলামের মাপ দেখে এটা আন্দাজ করে বলছি। এটা কমবেশি হতে পারে। আচ্ছা। নেক্সট হলো: ‘ছয়শ শব্দের বুদ্ধিজীবী’। সিক্স হ্যান্ড্রেড ওয়ার্ডস ইন্টেলেকচুয়াল। এদের মধ্যে পড়েন ইমাম সাহেব। [হাত দিয়ে কলামের দৈর্ঘ্যে মাপ দেখিয়ে] এতটুক। তিন-সাড়ে তিন ইঞ্চি, তিন কলাম। তার বেশি না। ওনারা বলে দেন: “আপনার লেখা ছয়শ শব্দের মধ্যে লিখে দিতে হবে”। কখনও কখনও আমাকেও বলেছেন। “অমুক বিষয়ে একটা লেখা দিতে পারবেন?” আমি বলেছি, “হ্যাঁ, পারব।” তখন বলে দিল: “ছয়শ শব্দের মধ্যে লিখে দিতে হবে”। আমি বললাম, “আমি নাই। আমি অত কম লিখতে পারি না। আমার জ্ঞান আরেকটু বেশি।” [দর্শকশ্রোতার হাসি] এই তিনটি ক্যাটেগরির ইন্টেলেকচুয়ালরা প্রথম আলোতে লেখেন। ইনি [ইমাম] থার্ড ক্যাটেগরির। ইনাম সাহেব ফার্স্ট ক্যাটেগরির। ওনার ছবি থাকে। ওনার কলামের ব্যানার আছে। লক্ষণ আছে: ওনার জাত আলাদা। উচ্চ জাত। ‘তালিকাভুক্ত বুদ্ধিজীবী’- আমি নাম দিয়েছি। প্রথম আলোর এবং ‘সুশীল সমাজ’-এর তালিকাভুক্ত বুদ্ধিজীবী। এটার নাম হচ্ছে ‘লিস্টেড ইন্টেলেকচুয়াল সিন্ড্রোম’। সুযোগ-সুবিধা পেলে একদিন শুধু এই নামেই, এই নিয়ে আলাপ করা যাবে। বিস্তারিত। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির একটা প্রধান সিন্ড্রোম। আমাদের মাথার অসুখের রোগলক্ষণ। আচ্ছ।
তো, ইমাম সাহেব বলছিলেন যে ওনার ছোটবেলায় স্কুলে উনি উচ্চতর গণিত ফোর্থ সাবজেক্ট হিসেবে নেবেন, নাকি পাবলিক এ্যাডমিন্সট্রেশন নেবেন এই নিয়ে দুই টিচারের মধ্যে রেষারেষি। ইতিবাচক রেষারেষি। ইনি বলেন যে তুমি পাবলিক এ্যাডমিন্সট্রেশন নাও। আমি এটা পড়াই। আমি ভালো পড়াই। তোমাকে আরও ভালো করে পড়াব। তুমি এটা পড়লে ভালো করতে পারবা। তোমার তো রেজাল্ট এমিনতে ভালো। আরেক জন ওদিকে উচ্চতর গণিত নিয়ে। উনি অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। উনি বলছেন, তুমি অঙ্কে নিরানব্বই পেয়েছ। তুমি কেন পাবলিক এ্যাডমিন্সট্রেশন পড়বে? তুমি উচ্চতর গণিত নিও। এই নিয়ে টানাটানি করতে করতে দেখা গেলা যুদ্ধ লেগে গেল। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। তারপর দেখা গেল স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। উনি গণিত নিয়েছিলেন। পরে দেখলেন যে বিপদ। তখন ঐ টিচার এসে বললেন, দেখ, এখনও সময় আছে। পাবলিক অ্যাড নাও। পড়ার টাইম কিন্তু নাই। তোমার মূল গণিতই কিন্তু এখনও পড়া হয় নি। উচ্চতর গণিত কখন করবা? এই শুনে অঙ্কের টিচার দৌড়ায় আসলেন। এত বড় কথা! আমি তোমাকে বাসায় প্রতি দিন পড়াব। কিন্তু তোমাকে উচ্চতর গণিতই নিতে হবে। তারপর ঐ টিচার বাসায় কয়েক মাস নিয়মিত আসলেন। প্রতিদিন। এবং ঐ ছেলেকে পড়ালেন। বিনা পয়সায়।
খুব মহৎ। খুব সুন্দর। খুব ভালো একটা স্মৃতি। তাই ছিল অবস্থা। ঠিক না? এ রকম কথা আপনি অনেক পাবেন। অনেক স্মৃতি পাবেন। বাস্তব। এর রকম হওয়া উচিত। স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যাল পর্যন্ত। সে রকম এখন নাই। উনি দুঃখ করে বলেছেন। কেন নাই? সেইটা বলা দরকার। সেইটা লোকেট করা দরকার। সাথে এটাও খেয়াল রাখা দরকার যে এ রকম টিচার, ঐ রকম ছাত্র এখনও হয়তো কোথাও কোথাও আছে। বিশ্ববিদ্যালয়েও আছে। কিন্তু আমরা ধরে নিয়েছি। কোথাও কিছু নাই।
নেক্সট পয়েন্ট। শিক্ষার্থীদের অবস্থা। আমি এতক্ষন যে আলোচনাগুলো করেছি। এতক্ষণ যে আলোচনা হলো, সবই কিন্তু শিক্ষকদের জায়গা থেকে। শিক্ষার্থীদের অবস্থাটা কী।

শিক্ষার্থীদের অবস্থা: হাই-কমান্ডের জন্য জীবন যাপন
শিক্ষার্থীরা হচ্ছেন প্রতিক্রিয়াশীল। বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁরা নিজেরা নিজেদের উদ্যোগে তেমন কিছু করেন না। প্রতিক্রিয়া করেন। ক্রিয়া যা করার মাস্টাররা করেন, কেরানিরা করেন। শিক্ষার্থীরা শুধু পরিস্থিতির শিকার হন। কবীর সুমনের গান কি আপনারা শোনেন? “এইখানে শিকার বোধ হয়, বসে থাকে শিকারীর খোঁজে”। ভিকটিম হতে থাকেন তাঁরা। কোথাও তাঁদের কথা বলার উপায় নাই। কথা বললেই শেষে সেকেন্ড-ক্লাসটাও যদি না থাকে। কথা বললে পরে সেকেন্ড-ক্লাসটা যদি মরা সেকেন্ড-ক্লাস হয়ে যায়! ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট। তার মানে তো প্রায় থার্ডক্লাস! জাত নাই ঐ সেকেন্ড-ক্লাসের। ফলে, শিক্ষার্থীদের, প্রায় কোথাও কিছু করার নাই।
আর ঐ যে একটু আগে বললাম: ট্রেনিং। লম্বা ট্রেনিং। কঠোর ট্রেনিং। ক্লাস ওয়ান থেকে মাস্টার্স। মাথা না খাটানোর। চিন্তা না করার। অনুগত হওয়ার। পড়ে না বোঝার। নিজে নিজে লিখতে না পারার। ঐ লম্বা এইসব ট্রেনিং শেষ করে আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হন। তার পরে, প্রথম বছরটা পার করতে না করতেই টের পেয়ে যান, পড়াশোনা করার আদৌ কোনো দরকার নাই। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এখানে পড়াশোনা করার বিশেষ কোনো ব্যাধি দেখা দেয় না। কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল পর্যায়ের কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনমতো চ্যালেঞ্জ করার কিংবা বেয়াদবি করার (যে বেয়াদবি এ্যাপ্রুভড বাই সুলতানা কামাল, আমি আবার বলছি) কোনো লক্ষণ দেখি না।
যে শিক্ষার্থীরা বলেন বিপ্লব করবেন, সমাজতন্ত্র করবেন, ইসলামি সমাজ কায়েম করবেন, জীবন দিয়ে দেবেন; ঐ শিক্ষার্থীদেরকেও তো দেখি শেষমেশ ঐ লেফট-রাইট-ই করতে! লেফট-রাইট, লেফট-রাইট, লেফট। পার্টির হাই-কমান্ড যা বলেন, এঁরা সেটুকুই বোঝেন। তার বাইরে কিছু বোঝেন না। একবার একটা মত শিখে ফেলেন। মতাদর্শ। অমুক বাদ। তমুক তন্ত্র। ব্যস। হয়ে গেল। ঐ তন্ত্রটা আদৌ কী জিনিস, মতবাদটাই বা আসল কোথা থেকে, কী ব্যাপার, এসব নিয়ে তদন্ত করে দেখার কোনো আগ্রহ দেখি না। তলিয়ে দেখার মতো হয়তো কিছুই নাই।
আল্লাহ-রসুলের নামে স্লোগান দিচ্ছি। মার্ক্সের নামে স্লোগান দিচ্ছি। “সর্বহারার মতবাদ, মার্ক্সবাদ- লেনিনবাদ।” “নো ইস্ট নো ওয়েস্ট, ইসলাম ইস দ্য বেস্ট।” এ রকম ইসলামপন্থী, মার্ক্সপন্থী, নানান পন্থী লোকেরা আছেন। যাঁরা কার্ল মার্ক্সের আশপাশ দিয়ে জীবনে কোনোদিন হাঁটেন নাই। মার্ক্স দু’পাতা উল্টিয়ে দেখেন নাই। যিনি দেখেছেন, দেখে বুঝে ফেলেছেন যে ওটা দেখা যাবে না। ওটা বোঝা যাবে না। কিংবা কোরআন শরিফ নাড়াচাড়া করেন নাই। হাদিসের বইও নিয়ে পড়াশোনা করে দেখেন নাই। বড়জোড় হয়তো মওদুদীর বা আর কারও এ রকম বই থেকে কিছু কোটেশান পড়া আছে। সেই কোটেশানও নিজে মওদুদীর বই নিজে হাতে উল্টায়ে খুঁজে বের করেছেন যে তা-ও না। নেতারা যে কোটেশান দিয়েছেন, ঐ কোটেশান। আর, বামওয়ালাদের পকেটে তো কোটেশানের বই-ই ছিল। রেডবুক। মাও সে তুঙের। চেয়ারম্যান মাওয়ের পকেট-মাপের উদ্ধৃতি-গ্রন্থ। এ বুক অফ কোটেশানস। মাও সে তুঙের হাদিস। চীন সরকারের সরকারি প্রকাশনা। আপনাকে আর মাও সে তুঙের গোটা গোটা বই পড়তে হবে না। মাও সে তুঙের হাসিদ পড়। এতটুক এতটুক কোটেশান। ঐ পড়লেই হবে।
এ হচ্ছে আনুগত্য। এই হচ্ছে লেফট-রাইট করা। এ হচ্ছে হাই-কমান্ডের জন্য জীবনযাপন করা। এই দিয়ে নাকি সমাজতন্ত্র হবে! সমাজতন্ত্র: ‘মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজ’। ওনারাই বলেন। কার্ল মার্ক্স লিখেছেন। তো মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজ হবে কি লেফট-রাইট করে? মার্চ-পাস্ট করে? স্রেফ অনুগত হয়ে? কোনো প্রশ্ন না করে? প্রশ্নাতীতভাবে? মানুষ না হয়ে? সৃজনশীলতার যিনি চর্চা করেন না, প্রশ্ন যিনি করেন না, তিনি কিসের মুক্ত মানুষ? নিজে যিনি একেবারে ঝাড়া-হাত-পা ‘চিন্তাভাবনা-মুক্ত মানুষ’, পার্টির থিওরি আর বক্তৃতা যাঁকে মুখস্থ করতে হয়, নকল করতে হয়, তিনি গড়বেন উন্নত সমাজ? বিদ্রোহী নন যিনি, জীবনে কখনও বিদ্রোহ করেন নি যিনি, তিনি হবেন বিপ্লবী? নিতান্তই হাসির কথা।
তো, শিক্ষার্থীদের মাঝে আমরা দেখি এই রকম। পঙ্গুত্ব। পরনির্ভরশীলতা। আনুগত্য। অনুকরণ। তদবিরের ট্রেনিং। ঝোপ বুঝে দুই রকম কোপ মারা। সময় বুঝে হম্বিতম্বি। আর, ‘সময় বুঝে প্রাজ্ঞ-ভাবুক অনেকে নিশ্চুপ’।
এগুলো হচ্ছে শিক্ষার্থী-সমাজের বৈশিষ্ট্য। বলতে আমার খারাপ লাগছে। শিক্ষকদের বেলায় এই খারাপটা লাগে নাই। শিক্ষার্থীদের বেলায় লাগছে। এটা দুঃখের বেশি। শিক্ষকরা তো পেকেই গিয়েছে। একেবারে পরিপক্ক হয়ে গেছেন। আর কী? গাছ থেকে ঝরে পড়ার অপেক্ষা। পচে যাওয়ার অপেক্ষা। কিন্তু, শিক্ষার্থীদের অনেক কিছু করার আছে। এখনও তাঁরা পচেন নি। পরিবর্তন তাঁদের হাত ধরেই আসতে পারে। এই জন্য দুঃখ। তাঁরাই যদি এমন অন্ধ হন, আর আনুগত্যপরায়ণ হন, তাহলে আর থাকেটা কী একটা জনগোষ্ঠর জীবেন? এবং তার মধ্যে আবার সবচাইতে যাঁরা বিপ্লবী (কি ডান বিপ্লবী কি বাম বিপ্লবী) তাঁদের যদি এই হাল হয়, তাইলে আর কী থাকে, বলেন? হাতে হারিকেন, লাল বাত্তি, ঘুটঘুটে অন্ধকার ছাড়া?
সাধারণত শিক্ষার্থীরা সক্রিয় নন, নিষ্ক্রিয়। মাস্টার বলেন, ওঁরা করেন। কেরানি-অফিসারগণ বলে, ওঁরা করেন। ঘুষ চায়, ওরা ঘুষ দেয়। শিক্ষকরা অপকর্ম করেন, ওঁরা শুধু দেখে যান, সহ্য করে যান। [বদরে মুনীরের কবিতার মতন: “আমার কেবল দ্রষ্টার অধিকার, দেখে দেখে ছবি এঁকেছি চাহিদা মতো”।] কিন্তু, এছাড়াও আছে। সক্রিয়তা আছে। হা হুতাশ করা। দুঃখ করা। আর গালাগালি দেওয়া। এগুলাও ইতিবাচক। ওগুলোতে প্রমাণিত হয় যে না, …. কিছু আছে। এত যে অন্ধকার, তার মধ্যে সক্রিয়তাটুকুও আছে। যে সমাজে কিচ্ছু থাকে না, সেখানে যদি হা-হুতাশ থাকে, তাহলেও অনেক শুকরিয়া। অন্তত ফোঁস ফোঁস শোনা যাবে তো! দীর্ঘ নিশ্বাস। ঐটুকু শোনা গেলেও ভালো। আশা থাকে: এ দীর্ঘশ্বাস থেকে পরে কিছু হবে। ঝড় অথবা সুবাতাস। কিছু একটা হবে।

শিল্পী: বারখাৎকভ
সূত্র: সিঙ্গুলা আর্ট
স্বাধীনতাটুকুই বিশ্ববিদ্যালয়
ছাত্ররা আর কী করে? সারা জীবন ধরে স্মৃতিচারণা করে। ওমুক স্যার ভালো ছিল, তমুক স্যার খারাপ ছিল। সারা জীবন ধরে আমি দেখেছি। বুড়োদের দেখেছি, আমাদের দেখেছি, ছোটদেরকেও দেখছি। স্মৃতিচারণ আর স্মৃতিচারণ। মুগ্ধতার স্মৃতিচারণ। গালাগালির স্মৃতি চারণ। ঐ শালার জন্য আমি সেকেন্ড-ক্লাসটা পাইলাম না! আর অমুক স্যার, আহা, কত সুন্দরভাবে হাসে! এই থেকে শুরু করে অনেক কিছু। ঐ টুকুই ভালো। টিচাররা যদি একদিনও ভালোভাবে কথা বলে থাকে, ঐটা সারা জীবনের স্মৃতি। তার মানেটা কী?
এটাই তো স্বাভাবিক। ছাত্রদের এই কর্মে তো কোনো দোষ নাই। কারণ টিচাররা, তাঁদের মডেল। টিচাররা তাঁদের আইডিয়াল। রোল মডেল। এটা স্বাভাবিক। ফলে তাঁরা যে খারাপ করেছেন, ঐটাও তাঁদের সারা জীবনের স্মৃতি, ভালো করেছেন, ঐটাও সারা জীবনের স্মৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি বলতে এই স্মৃতিগুলোই। এই স্মৃতিগুলোই। আর কী স্মৃতি?
দুঃখের বাইরে, আনুগত্যের বাইরে, বঞ্চনার বাইরে আর কী স্মৃতি? ইতিবাচক, ভালো, মঙ্গলের কী স্মৃতি? নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বের স্মৃতি। নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার স্মৃতি। অনেক ছাত্রের সঙ্গে, অনেক ছেলেমেয়ে সঙ্গে, অনেক জেলার অনেক রকমের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার স্মৃতি। এখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আনন্দ। আনন্দের স্মৃতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দিকটাকে নিয়েই।
এই স্মৃতিগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য কী? স্বাধীনতা। এই সমস্ত জায়গা হলো ঐ জায়গা, যেখানে শিক্ষার্থীরা স্বাধীন ছিল। যেখানে যেখানে ছিল সেখানে সেখানেই তাঁরা পরস্পর সহযেগিতা করেছে। যেখানে স্বাধীনতা ছিল সেখানেই তাঁরা সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। একে অন্যকে আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কার করেছেন খোদ মানুষ্যত্বকে। কবিতা করেছে। কবিতা পড়েছে। অনুধাবন করেছেন মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ককে। আবৃত্তি করেছে। নাটক করেছে। গান গেয়েছে। গাছতলায়। অনুষ্ঠানে। কত রকম। প্রেম করেছে। এগুলো হলো স্বাধীনতার স্মৃতি।
প্রমাণিত হলো: সমাজে স্বাধীনতা যেখানে আছে, সেখানে মঙ্গল আছে, আনন্দ আছে, সহযোগিতা আছে, সংহতি আছে, সুখ আছে, সুখস্মৃতি আছে। বিশ্ববিদ্যালয় এরকম একটা জায়গা। এবং এইটুকু আছে বলেই, এখনও পর্যন্ত, যুগের পর যুগ করে, শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চান। কেন? স্বাধীন হওয়া যায়। স্বাধীন থাকা যায়। কার হাত থেকে? পরিবারের কর্মকর্তা-অফিসারদের হাত থেকে। শিশু শ্রেণি থেকে মাস্টার্স শ্রেণি পর্যন্ত যাঁরা আমাদের মহা অফিসার আছেন। পিতা এং মাতা। চিফ কন্ট্রোলার অ্যান্ড চিফ ইন্সট্রাক্টর অফ দ্য চিলড্রেন। এই অফিসারদের হাত থেকে মুক্ত থাকাটাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আসল আনন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়। তাহলে এই চার-পাঁচ বছর বাপ-মা এসে খবরদারি করতে পারবে না।
স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাটুকুই বিশ্ববিদ্যালয়ে যা কিছু মঙ্গল, সৃজনশীল ও শুভ, তার জন্ম দেয়। এবং এইটুকু হচ্ছে সুখস্মৃতি। আনন্দের স্মৃতি। তার মানে, আপনি যদি এই স্বাধীনতা, এই সহযোগিতা, এই আনন্দটুকু ক্লাসরুমে আনতে পারেন, যদি পড়াশোনার মধ্যে এটাকে প্রয়োগ করতে পারেন, তাহলে আপনি দেখবেন, সৃজনশীলতা কাকে বলে। আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই আবার দেখেবেন সত্যেন বুস, জগদীশ চন্দ্র বসু, কাজী মোতাহার হোসেনরা বের হবেন। আমাদের মতো বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তো সত্যেন বসু বের হয়েছেন।
পড়াশোনায় শিক্ষার্থীরা এত উদ্যমহীন কেন? পড়ালেখায় আনন্দ নাই বলে। আনন্দ নাই কেন? স্বাধীনতা নাই বলে। যেখানে যেখানে শিক্ষার্থীরা স্বাধীন না সেখানে সেখানে তাঁর নিস্তেজ, মরা, পঙ্গু, চিন্তাহীন, প্যাসিভ, অসক্রিয়, নিষ্ক্রিয়। এই জায়গাগুলো কোথায়? ক্লাসরুম। সেখানে শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয়। সক্রিয় কে? শিক্ষক। কারণ, তুলনামূলকভাবে তাঁর স্বাধীনতা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ‘ডিপার্টমেন্ট’ বলতে শিক্ষককে বোঝায়, তাঁদের সিদ্ধান্ত আর কর্মকাণ্ডকে বোঝায়, শিক্ষার্থীরা যেগুলোতে অংশগ্রহণ করেন মাত্র। রাজনীতি করব, এমনকি সেখানেও আমরা নিস্ক্রিয়। নেতা এবং ক্যাডার। তাঁরা ডিক্টেট করবেন। অন্ধত্ব ডিক্টেট করবে, মতাদর্শ ডিক্টেট করবে। আমরা ক্যারি আউট করব। আর কোথায় কোথায় স্বাধীনতা নাই? হলে আমার স্বাধীনতা নাই। ওখানে মাস্তান বাহিনী আছেন, প্রভোস্ট বাহিনী আছেন। আর কোথায়? ক্যাম্পাসে হাঁটাহাঁটি করার ক্ষেত্রে আমি নিষ্ক্রিয়। পুলিশ-প্রক্টর বাহিনী আছেন।

মুখস্থ+মাদক+মিথ্যা=মিডিয়া
এইসব পরাধীনতা আর নিষ্ক্রিয়তা থেকে আসে আমার হতাশা। আসে নিজের উপরে আস্থার অভাব। আসে নৈরাশ্য। নৈরাশ্য নিজেই একটা ব্যারাম। নৈরাশ্যের পিছে পিছে আসে মাদকাসক্তি। তো, আপনি প্রথম আলো, আপনি মাদকাসক্তি তাড়াবেন, অথচ সমস্যার গোড়ায় দেখবেন না। তা তো হয় না।
এক মুখে আপনি বলে বেড়াবেন, মাদককে না বলুন, আরেক মুখে বলবেন, পেপসিতে হ্যাঁ বলুন, পেপসির নেশা করুন, শীতে-বর্ষায় পেপসি খান, তা তো হয় না! গোল্ড লিফের জাহাজ কোন দিক দিয়ে কোথায় গেল তা নিয়ে দিনের পর দিন গুরুত্বসহকারে সচিত্র প্রতিবেদন ছাপবেন, তা তো হয় না! ‘আজকে আপনার বাসায় নানু যাবেন, আপনার ফ্রিজে পেপসি আছে তো!’ পাহাড়-সমান এত বড় বিজ্ঞাপন। এত বড় নানুর ছবিসহ। প্রথম আলোর পেপসি-প্রচারাভিযান। মনে আছে?
তখনই আমরা বলতাম, প্রথম আলো আসলে কর্পোরেট পুঁজির বিজনেস পার্টনার মাত্র। প্রধান মিডিয়া মাত্রেই কর্পোরেট পার্টনার। এখন ওনারা প্রকাশ্যেই বলেন, আমরা পেপসির মিডিয়া পার্টনার, আমরা ইউনিলিভারের মিডিয়া পার্টনার। ফলে অবস্থাটা দাঁড়ায়: মাদকে ‘না’ বলুন, পেপসিকে ‘হ্যাঁ’। মাদকে ‘না’ বলুন, সিগারাটকে ‘হ্যাঁ’। (মনে আছে প্রথম আলোয় ‘বেনসন খান, সোনা হয়ে যান’? মনে আছে বি গোল্ড বিজ্ঞাপনের কথা?) মাদককে ‘না’ বলুন, কর্পোরেট-ভোগবাদকে ‘হ্যাঁ’। মাদককে ‘না’ বলুন, গ্লামারকে ‘হ্যাঁ’।
মিডিয়া প্রসঙ্গে পরে আমি আরেকটু আসব। আপাতত বলি, প্রথম আলোর সাম্প্রতিক স্লোগান কী? মাদক-মিথ্যা-মুখস্থ এই তিনকে না বলতে হবে। এই তিন যোগ দিলে কী হয়? যোগ করে দেখেন তো: যোগ দিলে মিডিয়া হয়। [মাদক+মিথ্যা+মুখস্থ=মিডিয়া]
প্রথমে ‘মাদক’। মিডিয়া নিজেই হচ্ছে মহা-মাদক। রঙিন জগতে হাতছানির নেশা। গ্লামার, যৌনতা, অপরাধ, আর ভোগবাদের নেশা। সকাল বেলা পত্রিকা না পেলে টয়লেট হয় না। সন্ধ্যায় নাটক না দেখলে সারা রাত কেমন উসখুস উসখুস। প্রতিদিন টিভির খবর শো আর টক শো না দেখলে মনে শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। টিভি ছাড়া একটা বাসা কল্পনা করেন তো? পরিষ্কার মাদকাশক্তি।
তারপর দেখন: ‘মিথ্যা’ মিডিয়া মানেই তো অপ্রিয় সত্য গোপন করে যাওয়া। হাফ ট্রুথ দিতে পাতা ভরিয়ে রাখা। এর নাম হচ্ছে মিডিয়া। মিথ্যা হচ্ছে মিডিয়ার প্রধান কনটেন্ট।
আর কী? ‘মুখস্থ’। ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের দিকে তাকান। সবই তো মুখস্থ। সুশীল সমাজের বাণী চিরন্তনীও মুখস্থ। গল্প-উপন্যাস-সাহিত্য-রাজনীতি-সমরনীতি সবই তো মুখস্থ। লেখকের জন্যও মুখস্থ, পাঠকের জন্যও মুখস্থ। পাঠক জানেন তাঁর পত্রিকা কী লিখবে। রিপোর্টারও জানেন, হাউসে গিয়ে তিনি কী লিখতে পারবেন, আর কী লিখলে আমার চাকরি থাকবে না, প্রমোশন হবে না। সম্পাদক ডেকে বলবেন, তোমার রিপোর্ট ঠিক অবজেকটিভ হচ্ছে না, ব্যালান্সড হচ্ছে না। সেন্সরশিপ এর নাম। সেন্সরশিপও মুখস্থ, সাংবাদিকতাও মুখস্থ। এবার যোগ করেন: মাদক, মিথ্যা আর মুখস্থ। যোগ দিলে মিডিয়া হয়। শাসকশ্রেণি হয়। তো, প্রথম আলো বলেছেন মাদক-মিথ্যা-মুখস্থকে ‘না’ বলতে। কথাটার মানে হচ্ছে: মিডিয়াকে ‘না’ বলুন, মানুষকে ‘হ্যাঁ’। তিন ‘ম’ এর সাথে আরেক ‘ম’ যোগ করুন, ‘মানুষ’ও হবে।
আচ্ছা। মিডিয়া নিয়ে এরপরে আরেকটু বলব। দরকার আছে বলার।
তার মানে ছাত্রদের আপনি যদি ইনভল্ব না করেন, লিবার্টি না দেন, ছাত্রদেরকে যদি আপনি ডিপার্টমেন্ট চালানোর দায়িত্ব না দেন, তাহলে কিভাবে হবে?
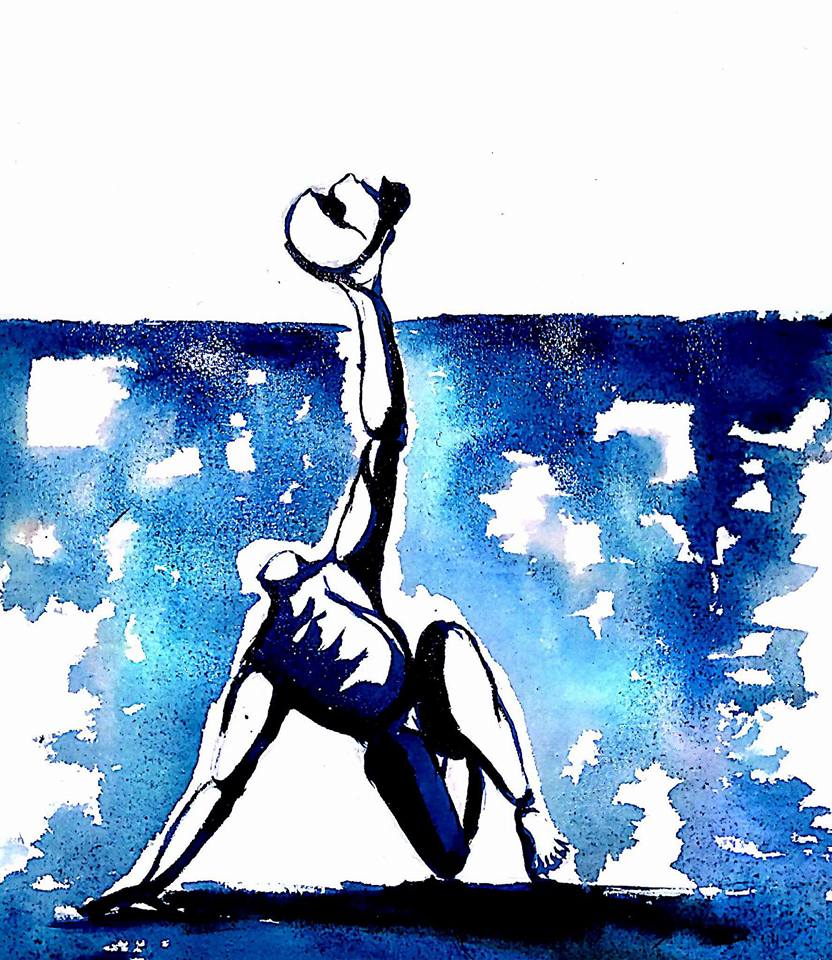
পার্টি মানে পলিটব্যুরো, বিভাগ মানে অ্যাকাডেমিক কমিটি
আচ্ছ, তখন আমি একটু খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। ঐ যে পার্টির কথা বললাম না। তখন আমরা শুনতাম, ‘কমরেড, পার্টি এই ডিসিশান নিয়েছে, এটা আপনার ক্যারি আউট করতে হবে’। আমি কেন? আমি পার্টি না। আমি ডিসিশান নেই নি। আমার কাজ কী? ডিসিশান ক্যারি আউট করা। আর লিডারের কাজ কী? উনি হচ্ছেন পার্টি। ওনার কাজ ডিসিশান নেওয়া। মন্ত্রীসভার কাজ কী? ডিসিশান নেওয়া। আর সারা দেশের লোকের কাজ কী? ডিসিশান ক্যারি আউট করা। মন্ত্রীসভায় যে ডিসিশন নেওয়া হয় সেই ডিসিশান কার? রার্ষ্ট্রের। আর সারা দেশের জনগণ যেটা মনে করে সেটা কী? সেটা রাষ্ট্রের মত না, কতিপয় ব্যক্তির মত বড় জোর, এমনকি রাষ্ট্রদ্রোহিতা, মাঝে মাঝে অন্তত।
তো, ঐ একই জিনিস শুনলাম এখানে এসে। ডিপার্টমেন্টে। যেই শিক্ষার্থীরা গিয়ে বলল স্যার, এই পরীক্ষাটা একটু আগে নিলে ভালো হয়, এটা একটু পরে নিলে ভালো হয়, এটা একটু পড়ালে ভালো হয়, এটা একটু না পড়ালে ভালো হয়, তখন শিক্ষকরা সাফ জানিয়ে দিলেন: এটা বিভাগের সিদ্ধান্ত।
সিদ্ধান্তটা আসলে কার কার? বিভাগের একাডেমিক কমিটির। আট-দশ জন শিক্ষকের, বা ১৮ জন শিক্ষকের। ঐ আঠারো জনই ডিপার্টমেন্ট। শিক্ষার্থীরা কী? ফক্কা। কিছু না। শিক্ষার্থীরা ডিপার্টমেন্ট না। শিক্ষকরা ডিপার্টমেন্ট।
বলার কী বাকি থাকে! এই সমস্ত আলাপ প্রতিদিন করছি আমরা। ভাষার মধ্যে আছে। বিভাগ সিন্ধান্ত নিয়েছে। তুমি বিভাগ না, তুমি সিলেবাস না, তুমি পড়াশোনা না, তুমি ভালো রেজাল্ট না, তুমি সেটের মধ্যে নাই, তুমি শিক্ষক হবা না। তুমি তাহলে কী? তুমি নোবডি।
তার মানে শিক্ষার্থীদেরকে ডিপার্টমেন্ট পরিচালনায় অংশ নিতে হবে। এদেরকে ইনভল্ব করতে হবে। রাকসুতে, ডিপার্টমেন্টে, শিক্ষার্থীদের ফোরামে। তিয়াত্তরের আইন আছে। অধ্যাদেশে আছে: প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে শিক্ষার্থীদের, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ফোরাম থাকবে। সেই ফোরাম নানান ধরনের কাজে অংশ নেবেন। আমি চাই তাঁরা ডিপার্টমেন্ট পরিচলানার কাজেও অংশ নেবেন। তাঁরা সিলেবাসও প্রণয়ন করবেন। তাঁরা শিক্ষকদের প্রমোশনেও মতামত দেবেন। আরও যেভাবে যেভাবে মতামত তাঁরা দিতে পারে সেভাবে সেভাবে তাঁদেরকে ইনভল্ব করতে হবে। যত বেশি পারা যায়। শিক্ষার্থীরা এখনই যদি নিজের দায়িত্ব নিজে না নেন, এখনই যদি নিজেরা নিজেদেরকে পরিচলানা না করেন, তাহলে ভবিষ্যতে তাঁরা কেন করে দেশ পরিচালনা করবেন। ওখানে গিয়ে তাঁরা আমলা হবেন, শুধু বসের হুকুম শুনবেন, আর কিছু করবেন না। তখনই স্বৈরাচার হবে। তখনই হাসিনা-খালেদা হবে। তখনই আবার ‘বিশেষ পরিস্থিতি’ হবে। জরুরি পরিস্থিতি।

ছাত্র-রাজনীতি ও ছাত্র-আন্দোলন এক কথা নয়
এবার আসেন, ছাত্র-রাজনীতির দিকে তাকানো যাক কিছুটা তো বলাই হলো। কিন্তু ‘ভালো ছাত্র-রাজনীতি’ আছে না! আমি নিজে সারা ছাত্রজীবন এই কাজই করেছি: ছাত্র-রাজনীতি। ফলে কটাক্ষ করার জায়গা থেকে বলছি না। ‘ছাত্র-রাজনীতি বাংলাদেশের গৌরব’ না।
শিক্ষার্থীরা/ছাত্র-রাজনীতি ৫২, ৬২, ৭১, ৬৯, ৯০- এসব সৃষ্টি করে নি? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথা কারা এনেছেন? ছাত্র-রাজনীতি। প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান সাহাবুদ্দীন। কারা বানিয়েছে? ছাত্র-রাজনীতি। এসবে গৌরব আছে না! ভালো কিছু আছে না! আছে।
কিন্তু, নব্বইয়ের পরে আসেন। ১৭ বছর। দু-এক দিন না। ছাত্র-রাজনীতি কী করছে? কোথায় আছে? কেমন আছে? বেঁচে আছে? দেখা যাচ্ছে? আমি তো দেখি না। নাই। নিষ্ক্রিয়। টের পাওয়ার উপায় নাই। কিন্তু আপনি আইন করছেন। শুনছি, ওই জিনিস নিষিদ্ধ করতে হবে। ঐ জিনিস তো এখন আর নাই-ই। ঐ জিনিস শিক্ষার্থীরা কেউ করেন না অলমোস্ট। শিক্ষার্থীরা যখন আন্দোলন করেন, শিক্ষার্থীরা যখন ঝুঁকি নেন, পুলিশের মারও খান, তখন তাঁরা ভয়ে থাকে: ছাত্র-সংগঠনগুলো যেন তাঁদের ভেতরে ঢুকে না যায়। ছাত্র-রাজনীতি, ছাত্র-সংগঠন শিক্ষার্থীদের কাছে আতঙ্ক।
সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটা বড় বড় ছাত্র-আন্দোলন আমরা দেখেছি। জাহাঙ্গীরনগরে দেখেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি। আমাদের [রাজশাহী] বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি। তিরিশে অক্টোবর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-অভ্যুত্থানের দিন। ছাত্র-বিদ্রোহের দিন। সেই দিন দেখেছি। সেইদিনকার বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষক-প্রশাসন-শিবির-পুলিশবিরোধী রক্তক্ষয়ী বিস্তৃত প্রতিরোধ ছিল প্রাতঃস্মরণীয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ধর্ষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বহু বহু দিন ধরে একটানা অভূতপূর্ব আন্দোলন করেছেন। বিশাল পরিসরে করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে সাধারণ মেয়েদের স্বর প্রতিরুদ্ধ করতে প্রফেসররা যখন রাতের বেলা পুলিশ ঢুকিয়ে মেয়েদেরকে জঘন্যভাবে মার খাইয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা তখন কয়েকদিন ধরে তীব্র, বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। মহা-পালোয়ান এক ভিসিকে চোখের পলকে ‘ক্ষমতা’ থেকে ফেলে দিয়েছেন। আরও অনেক উজ্জ্বল আন্দোলন আমরা বিগত নব্বই দশক জুড়ে দেখেছি। এই সমস্ত ছাত্র আন্দোলন কিন্তু ছাত্র-রাজনীতির যাবতীয় হিসাব-নিকাশের বাইরের ‘অরাজনৈতিক’ ঘটনা। ছাত্র-রাজনীতি কোনো কল্কে পায় নি। ছাত্র-সংগঠনগুলোকে শিক্ষার্থীরা দূরে রেখেছেন। কাছে ঘেঁষতে দেন নি। এবং ছাত্র-রাজনীতিওয়ালাদের, ঐ শক্তিও ছিল না যে জোর করে তাঁরা কাছে ঘেঁষবেন। ভয় দেখানোর জোরও ছিল না। আর, যাঁদের জোর ছিল, জোর থাকেই, তাঁরা তো সরকারি ছাত্র-সংগঠন। প্রতি যুগেই তঁরা এই সরকার ঐ সরকারের অঙ্গ-সংগঠন। এবং পরিস্থিতিমতো তাঁরাও টেকে নি, ছাত্রদের সামনে। অন্তত ফর এ টাইম বিইং টেকে নি। প্রকৃত শিক্ষার্থীদের, প্রকৃত ছাত্র-আন্দোলনের দৃঢ় সংহতি তাঁদের সমস্ত হুমকি-ধামকিকে রুখে দিয়েছে।
এই তো ছাত্র-রাজনীতি। গত ১৭ বছর। [বিগত এই ১৭ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ‘অরাজনৈতিক’ ছাত্র আন্দোলনগুলোকে, তথা সামাজিক প্রতিরোধ-আন্দোলনসমূহকে, উপলব্ধি করার কাজ এখনও বাকি আছে। ছাত্র-রাজনীতি করা ছাত্র-সংগঠনগুলোকে দিয়ে সেই কাজ হবে না। তাঁদের রচিত ইতিহাসে তাঁরা ছাড়া আর কেউ কোনো কর্ম করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। বাংলাদেশের ইতিহাস নাকি তাঁদেরই ইতিহাস।] তো এটাকে ব্যানড করার কী আছে? বাস্তবে এটা তো নাই-ই। ছাত্র-রাজনীতি নাই। শিক্ষক-রাজনীতি এমনিতেই বেআইনি।
এরপরেও শিক্ষক-রাজনীতি নিষিদ্ধ করো, ছাত্র-রাজনীতি নিষিদ্ধ করো- এই কথা যাঁরা বলছেন, তাঁরা আসলে কী নিষিদ্ধ করতে চান? এই প্রশ্ন আমাদের মনে আছে। এই প্রশ্ন একটু পরে তুলব। আপাতত ছাত্র-রাজনীতি নিয়ে আরও কিছু কথা বলি।
তাহলে আপনি দেখছেন, ছাত্র-রাজনীতি জিনিসটা অন্ধত্ব, লেপট-রাইট, হায়ারার্কি আপনি ছাত্র-রাজনীতির মধ্যেও দেখবেন। একই হায়ারার্কি। ক্যারিয়ার: নেতা হওয়ার ক্যারিয়ার, ভবিষ্যতে কিছু করে-কম্মে খাওয়ার ক্যারিয়ার। অসুখ-বিসুখ হলে পার্টির ডাক্তাররা দেখবেন ইত্যাদি প্রভৃতি নানান কিছু। তদবরিও হবে। আপনি যদি সিপিবির মতো একটা নাই-পার্টির নেতাও হন তবুও তো আপনার কিছু পুরানো বন্ধুবান্ধব সচিবালয়ে আছেন। কিছুটা তদবির তো করতেই পারবেন।

শিল্পী: স্যামুয়েলস গিলস
সূত্র: সাৎসি আর্ট
ছাত্র-রাজনীতির গৌরবের সমাচার
‘ভালো ছাত্র-রাজনীতি’ তাহলে কোথায় অবস্থিত? বাস্তবে জিনিসটা পাওয়া না গেলেও ‘গৌরবের ইতিহাসে’র পাতায় পাতায়। ছাত্র ইউনিয়নের ২৫-তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী যখন হয়, ১৯৭৭ সালে মনে হয়, তখন তাঁরা একটা বই বের করলেন। গৌরবের সমাচার। ছাত্র ইউনিয়ন করাটা কত গৌরবের। এই গৌরবের সমাচার বইটা দীর্ঘকাল ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে খুবই প্রশংসিত কেতাব ছিল। গৌরব কিন্তু মিউজিয়ামে থাকে।
বরেন্দ্র মিউজিয়ামে যান। ঘর ভর্তি, বারান্দা ভর্তি ‘গৌরব’ দেখতে পাবেন। শিব মূর্তি, মা তারার মূর্তি, বোম শঙ্করের মূর্তিতে ভরা। বোম শঙ্কর নাই এখন। মা তারাও এখন নাই। গৌরবের স্মৃতি আছে। উনিশশ বায়ান্নর সত্যিকারের গৌরব যাঁরা বানিয়েছিলেন, সেই শিক্ষার্থীরা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। বিদ্রোহ করেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন। দেশ ও সমাজের প্রতি নিজেদের কর্তব্য নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। তারপর তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দেশের জন্য কিছু করার। কাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তাঁরা? রাষ্ট্রকে। পুলিশকে। কর্তৃত্বকে। আর কাকে চ্যালেঞ্জ করেছিরেন তাঁরা? পার্টির হাই-কমান্ডকে। নিজের নিজের পার্টি হাই-কমান্ডকে। এইসব প্রশ্ন, ভাবনাচিন্তা, কর্তব্যবোধ, চ্যালেঞ্জ, এবং বিদ্রোহের জন্যই ‘একুশ’ হয়েছিল। ঐ জন্য গৌরব রচিত হয়েছিল।
পড়ে দেখেন। উনসত্তুরও তাই। বাষট্টির আন্দোলনও তাই। ছাত্র-সংগঠনগুলো নিজেরা নিজেদের পার্টিকে চ্যালেঞ্জ করেছে। পার্টি হাই-কমান্ড মানি না। মানলে ছাত্র-রাজনীতিটুকুই হয়, ছাত্র-আন্দোলন আর হয় না। তিরাশিতে আসেন। নব্বইয়ে আসেন। একই ঘটনা। এট ইতিহাস। যতক্ষণ সাধারণ শিক্ষার্থী আন্দোলন, যতক্ষণ ছাত্র-সংগঠন ওপরওয়ালা পার্টির পকেটে-ততক্ষণ ছাত্র-রাজনীতি নাই। যখন ছাত্র-সংগঠন প্রতিরোধ করছে নিজের মূল পার্টিকে, যখন চ্যালেঞ্জ করছে প্রথমত পার্টিকে, তারপরে আরও বড় কর্তৃত্বকে, তখন ছাত্র রাজনীতি গৌরবের।
এর নাম প্রকৃত গৌরব। গৌরব করার জন্য সৃজনশীল হতে হয়। স্বাধীন হতে হয়। চিন্তা করতে হয়। চ্যালেঞ্জ করতে হয়। তখন গৌরব হয়। বিগত ১৭ বছর ধরে আপনি গৌরবের কাজ করেন নি। কিন্তু আপনি গৌরব বেঁচে খাবেন। মিনিমিন মিনিমিন মিনিমিন মিনিমিন করে আমতলা জামতলায় বসে বসে বলবেন, আমার গৌরব, আমার গৌরব, আমার গৌরব আছে। আমাকে তাই নিষিদ্ধ করা যাবে না। নিজেই বলবেন, নিজেই শুনবেন। অন্য কাউকে শোনানোর মতো ক্ষমতাও আর নাই। এখন যদি গৌরব করতে চান, তাহলে আপনাকে এখন নতুন করে ৫২ বানাতে হবে। দেশে এখন বিশেষ সঙ্কট। দেশ এখন বায়ান্নর সেই গৌরব চায়। দেশ এখন নব্বইয়ের গৌরব চায়। বাষট্টি গৌরব চায়। কই সেই গৌরব? গৌরবআলারা কই? গৌরবআলারা গৌরবের দোহাই দিয়ে কোনোরকমে বলছেন যে আমাকে নিষিদ্ধ করো না। ঐ পর্যন্তই। এখন, এই মুহূর্তে, গৌরব তৈরির সংগ্রাম কই? নাই।
ফলে ঐ ছাত্র-রাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন-একটা হাওয়াই প্রশ্ন। ঐ জিনিস এমনি শুকাচ্ছে। মারা গেছে। মুমূর্ষ: ডাক্তার এসে ঘোষণা দিলেই হবে নাড়ি টিপে যে ওটা নাই। মারা গেছে। ওটা মৃত। আর যদি নতুন করে গৌরবের কিছু করার থাকে, তাহলে সেটা যাঁরা করার তাঁরাই করবে। যদি করে, তখন দেখা যাবে। আর যদি সত্যি তেমন দেখা যায়, তাহলে ছাত্র-রাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন কেউ তুলবে না। নব্বইয়ের আগে আগে অনেকদিন ঐ প্রশ্ন অনেকেই তুলতেন। আজকের মতো। নব্বইয়ের পরে বহুদিন তোলেন নি আর। ছাত্র-রাজনীতির ব্যর্থতার কথা ভুলে গিয়েছিলেন অনেকে। অনেক দিন পর্যন্ত। আবার মনে পড়ে গেছে। কারণ গৌরব আর নাই। আবার যদি গৌরব রচিত হয়, নিষিদ্ধ করণেওয়ালারা নিজেরাই নিষিদ্ধ হবেন। সুতরাং, আইন করে ছাত্র -রাজনীতি বাংলাদেশে শুরু হয় নাই, আইন করে নিষিদ্ধ করাটাও হাস্যকর।
সর্বোপরি, আমার জন্য ছাত্র-রাজনীতি নিষিদ্ধ করা না করা ইস্যু না। আমি চাই শিক্ষার্থীরা স্বাধীন হবে। যাঁরা ছাত্র-রাজনীতি করেন, তাঁরা স্বাধীন হন না। ফলে ঐ জিনিস সিদ্ধ হলেই কী, আর নিষিদ্ধ হলেই কী। আমার কিছু যায় আসে না। আমার এজেন্ডা ঐটা না। লোকে আলাপ করছে। প্রচুর কথাবার্তা হচ্ছে। কান্নাকাটি শোনা যাচ্ছে- প্রতিবাদের মতো করে। এজন্য বললাম কিছু কথা। ছাত্র-রাজনীতি করতাম এক সময়, তার জন্যে বললাম কিছু কথা।
কিন্তু আওমি চাই যে এই ছাত্র-রাজনীতি না থাক। না থাক। কিন্তু সেটা আইন করে ক্যামনে না থাকে- আমি এইটা বুঝি না। যাঁরা বোঝেন, তাঁরা আইন করেন। যাঁরা ঐ আইন ঠেকাতে চান, তাঁরা ঠেকান। আমি দুই গ্রুপের কোথাও নাই। কারণ, দেখতে পাচ্ছি, ঐ জিনিস এমনিতেই নাই। এবং আমি চাইও না যে ঐ জিনিস বাড়ুক। কেন চাই না? কারণ ওই জিনিস অন্ধত্বের জন্ম দেয়। আর যখন সেটা গৌরবের জন্ম দেয়, তখন সেটা আর ‘ছাত্র-রাজনীতি’ থাকে না, ‘ছাত্র-সমাজ’ হয়ে ওঠে। তখন বৃহত্তর ছাত্র-আন্দোলন হয়। ঐটা অন্য জিনিস। ঐটা ছাত্র-রাজনীতি না।
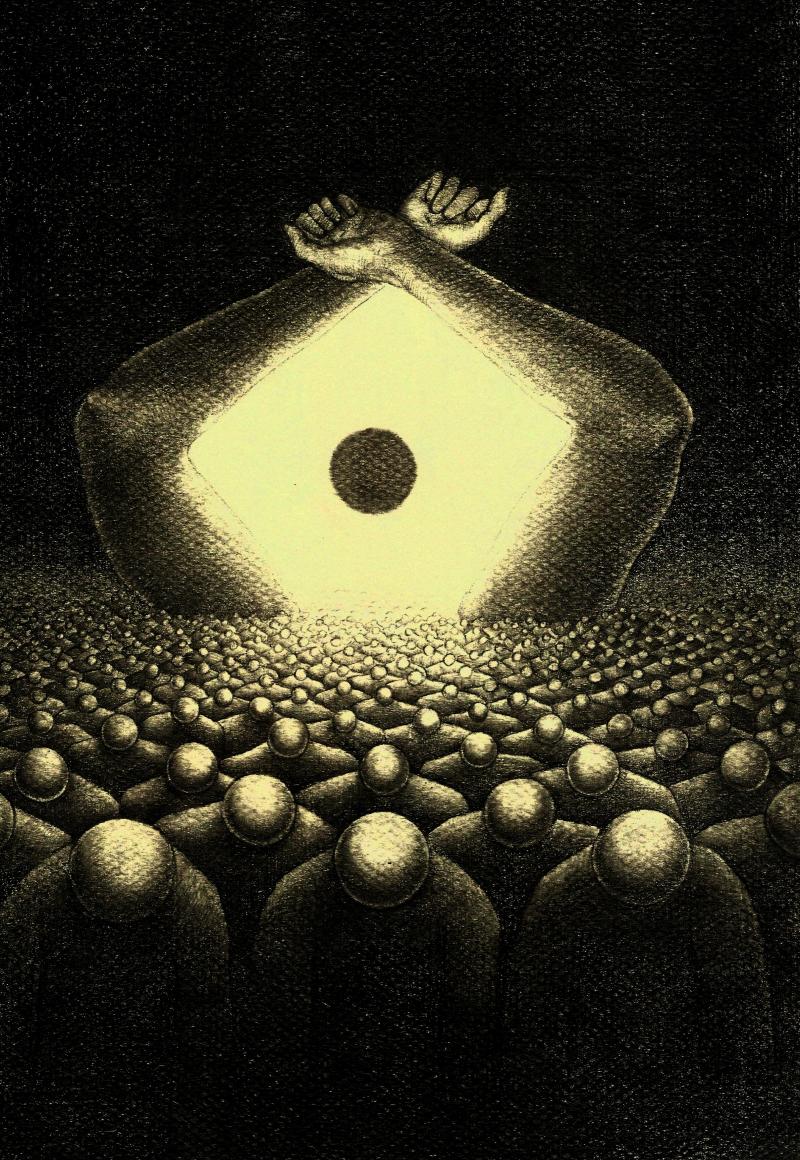
শিল্পী: কামিল জারজিক
সূত্র: কার্টুন মুভমেন্ট
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার: কী করিতে হইবে।
পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রক দপ্তর রাখার দরকার নাই
পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রক দপ্তর রাখার দরকার নাই। ডিপার্টমেন্ট পরীক্ষা সংক্রান্ত সব কাজই করতে পারে, আর সার্টিফিকেট দিতে পারে না। ওগুলো দেওয়ার জন্য, বলতে গেলে সার্টিফিকেটটুকু বানানোর জন্যই বিশাল এক ডিপার্টমেন্ট। আর পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। [ওখানে আসলে তাঁরা করেনটা কী? ডিপার্টমেন্টের ঠিক করা পরীক্ষার তারিখ সরকারিভাবে ঘোষণা করেন। ডিপার্টমেন্টের চূড়ান্ত করা পরীক্ষক-প্রশ্নকর্তাদের তালিকাটাকে তাঁরা উপাচার্যের টেবিলে পাঠান। সর্বশক্তিমান স্বাক্ষরের জন্য। এইসব হাবিজাবি কেরানি-কর্ম করাই এই পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রক দপ্তরের কাজ।] ধরেন, ঐ গোটা ডিপার্টমেন্ট যদি তুলে দেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ক্ষতি নাই।
হয়তো কেউ বলবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচাররাই পরীক্ষা নেবেন! কিন্তু, পরীক্ষা তো আমরাই নিই। রেজাল্ট তো আমরাই দিই। ওনারা স্রেফ ঘোষণা করেন। ওনাদের দেওয়ালে সাইক্লোস্টাইলে ছাপানো ফলাফল-তালিকা টাঙিয়ে দেন। পড়াও যায় না সেই তালিকা। এই যুগেও। এই যুগে ধ্যাড়ধ্যাড়া সাইক্লোস্টাইল তো আর পড়া যায় না। আর, টাঙান কখন সেই তালিকা? গভীর রাত্রে। সন্ধ্যাবেলায়। গিয়ে হারকিন দিয়ে দেখা লাগে। দেখা যায় না। আর যে নোটিশ বোর্ড! আহামরি আর কী। খোপ খোপ খোপ খোপ লোহার খাঁচা দিয়ে ঢাকা পুরো নোটিশ বোর্ড। (মমতাজউদ্দীন কলাভবনে যান। শহীদুল্লায় যান। সম্পূর্ণ বিল্ডিংই লোহার খাঁচা লাগানো।) গ্রিলের মধ্যে কী আছে পড়া যায় না। এই সবের জন্য গোটা একটা ডিপার্টমেন্ট। পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রক দপ্তর। আরও আলোচনা করা যাবে এটা নিয়ে। আজকে আর না করি।
উপাচার্য হবেন কে?
আমলাতন্ত্র ছোট করে ফেলতে হবে। ভিসি-কেন্দ্রিকতা দূর করে ফেলতে হবে। ভিসি কোনো অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হতে পারবেন না। আইন করে দিতে হবে। ভিসি নিযুক্ত হবেন ছয় মাসের জন্য। ছয় মাস পর পর ভিসি বদলাবে।
ভিসি কে হবেন? যিনি সিনিয়র মোস্ট, তিনিই ভিসি হবেন। অথর্ব হন, কথর্ব হন, পারেন, না পারেন, উনিই হবেন। উনি যদি না পারেন, উনি বলবেন ‘পারি না’। উনি যদি না পারেন, আমরা সব শিক্ষকরা মিলে বলব, আপনি পারেন না, আপনি রেস্ট নেন। নেক্সট লোক আসুক। নেক্সট সিনিয়র লোক। তার মানে, জীবনে একবার ভিসি হওয়ার চান্স আসবে কারও কারও। কারও কারও আসবে না। এ্যাকোর্ডিং টু সিনিয়রিটি।
ভিসি একটা আনুষ্ঠানিক পদ হবে। আর কিছু না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে ডিপার্টমেন্টে। ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের কাছে। তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয় চালান। ক্ষমতা থাকবে নিচে। শিক্ষার্থীদের কাছে। ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের কাছে এবং শিক্ষার্থীদের কাছে। তাঁরা যৌথভাবে ডিপার্টমেন্ট চালাবেন, মানে বিশ্ববিদ্যালয় চালাবেন। ডিপার্টমেন্টই বিশ্ববিদ্যালয়। হলই বিশ্ববিদ্যালয়।
কিন্তু, আপনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার খোলেন, নোটবই খোলেন, গাইড বই খোলেন, স্মারক খোলেন, বার্ষিকী খোলেন, যেকোনো বই খোলেন, দেখবেন যে এ্যাডমিন্সট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের ছবি দেওয়া আছে। ঐটা হয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক। প্রশাসনিক ভবন। মানে কেরানিকুলের ভবন। মানে আমলাদের ভবন। ঐটা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক। সিনেট ভবন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতীক না। অন্য কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক না।
তাহলে, ভিসি মানে কী? অফিসার। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিফ অফ স্টাফ। সেনাবাহিনীর মধ্যে যেমন চিফ অফ স্টাফ থাকে, এখানেও তেমন চিফ অফ স্টাফ। উনি সব চাইতে বড় অফিসার। উনি যে শিক্ষক, এই পরিচয় ওনার মনেই থাকে না। উনি কেরানিকুলের নেতা। কেরানিকুলের প্রধান। উনি বসেন প্রশাসনিক ভবনে। ঐজন্য ওইটা হচ্ছে প্রতীক। তো, এই ধারণা বদলাতে হবে। এই জিনিস তুলে দিতে হবে।
ভিসির নির্বাচন দরকার নাই। রাষ্ট্র ভিসিকে নিয়োগ দেবে না। সরকার ভিসিকে নিয়োগ দেবে না। ভিসি কে হবেন? আমরা বানাব। আমরা বানাব ভোট না দিয়ে। যিনি সিনিয়র, উনি ভিসি হবেন। উনি হচ্ছে গার্জেন। উনি আমাদের একটা প্রতীক। উনি সমাবর্তনের বক্তৃতা দেবেন। পড়াবেন। নিজের ডিপার্টমেন্টে প্রচুর ক্লাস নেবেন। আর ওনার গৌরবে আমরা গৌরাবান্বিত হব। উনি যত বেশি পড়াশোনা করবেন, ওনাকে বিদেশের লোকেরা ডিগ্রি দেবে, পদক দেবে, আমরা খুশি হব। এই পর্যন্তই।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অ-নে-ক উঁচু পদ হবে। সমাজের সম্ভবত সবাইতে উঁচু পদ। সম্মানের দিক থেকে। মর্যাদার দিক থেকে। ছিলও তাই। অতীশ দীপঙ্করের নাম করে আমরা এখন গলা ফাটাই না? নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নিয়ে গৌরব করি। ঐ আমলে কী ছিল? ঐ আমলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যখন সমাবর্তন হতো, রাজা আসতেন। রাজা যখন ঢুকতেন, কেউ উঠে দাঁড়াতেন না। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ঢুকতেন, তখন সবাই উঠে দাঁড়াতেন। রাজাও। এটা হচ্ছে মর্যাদা। এই মর্যাদা ক্ষমতাবানরা সহজে কাউকে দেয় না। স্বাধীনতা চর্চার মধ্য দিয়ে অন্যের শ্রদ্ধা আদায় করতে হয়। আর, কখনও কখনও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করতে হয়। কখনও কখনও কথা বলাটাও লড়াই। আরও অনেক কিছু। লড়াইয়ের রূপ- চেহারা-আদল-অবয়বের শেষ নাই।
বিশ্ববিদ্যালয় কারা চালাবেন? কিভাবে চালাবেন?
তাহলে, বিশ্ববিদ্যালয় চালাবে কে? শিক্ষকরা-শিক্ষার্থীরা। ডিপার্টমেন্টে এবং হলে। ব্যস। আর, কোথাও না। কোনো নির্বাচন না। কোনো রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ না। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার আরও যত রকম সুযোগ আছে, সেগুলো কেটে দিতে হবে। মঞ্জুরি কমিশনকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিতে হবে; যদি মঞ্জুরি কমিশন আদৌ লাগে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।
আপনি বলবেন যে এক জন শিক্ষক একাই প্রশ্ন করবেন, একাই খাতা দেখবেন, শিক্ষকদেরকে যে এত ক্ষমতা দিয়ে দেব ডিপার্টমেন্টে, পরে এদেরকে ঠিক করবে কে? এদের ঠিক করবে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেন। শিক্ষার্থীরা ঠিক করে রাখবে। শুধু ধিক্কার দিয়েই ঠিক করে রাখবে। ছি ছি বললেই ঠিক হয়ে যাবেন শিক্ষকরা। প্রতিদিন ছি ছি সহ্য করা খুব কঠিন। নির্লজ্জ হওয়া খুব কঠিন। এখন নির্লজ্জ রাষ্ট্রের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ আছে বলে, নির্লজ্জ রাষ্ট্রের নির্লজ্জ মিডিয়া আছে বলে, নির্লজ্জতার নানান কাঠামো আছে বলে নির্লজ্জতা সিদ্ধ। যখন রাষ্ট্রের ঐ হস্তক্ষেপ থাকবে না, যখন অস্ত্র থাকবে না, যখন রাষ্ট্রের প্রধান গোলাম হিসেবে ভাইস চ্যান্সেলার থাকবেন না (ঐ রকম ভাইস চ্যান্সেলার), তখন দেখবেন লজ্জা হবে। তখন দেখবেন, নির্লজ্জ হওয়া কত কঠিন। নিজেরা ট্রাই করে দেখেন, নির্লজ্জ হওয়া খুব কঠিন। ফলে, নিজের নিজের ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থীদের সামনে লোকলজ্জার ভয়েই শিক্ষকদেরকে সোজা হয়ে থাকতে হবে।
ক্ষমতা থাকতে হবে শিক্ষার্থীদের হাতেও। শিক্ষকদের প্রমোশনের জন্য শিক্ষার্থীরা মতামত দেবেন। মতামত দেবেন তাঁরা নিজেদের পাঠ্যসূচি প্রণয়নে, শিক্ষকদের ক্লাস পরিচালনা-পদ্ধতির ব্যাপারে, পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়নে, আরও অনেক কিছুতে। পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নতি সাধনে। কী কী করলে আরও পরীক্ষা আরও ভালো হয়, কী কী করলে পড়াশোনা আরও ভালে হয়, কী কী করলে গবেষণা আরও ভালো হয়, ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা তখন এখানে অংশগ্রহণ করবেন আইনগতভাবে। তখন ডিপার্টমেন্ট বলতে শুধু শিক্ষকদেরকে বোঝাবে না। তখন দেখবেন পরিস্থিতি বদলাবে। খুব কঠিন না। এই কাঠামোর মধ্যেই শুরু করা সম্ভব।

সূত্র: কার্টুন মুভমেন্ট
রাষ্ট্রের সমস্ত শুঁড় কেটে দিতে হবে
আরেকটা দিক আছে। আমি কিন্তু ভেতরের দিক, বাইরের দিক দুই রকমই বলছি। ভেতরের দিক যেটা সেটা আমরা আমরা ঠিক করব। আর, বাইরের দিক যেটা, সে ক্ষেত্রে সমস্ত শুঁড় কেটে দিতে হবে। রাষ্ট্রকে বলে দিতে হবে যে আপনারা ভেতরে আসবেন না। কিন্তু আপনারা আমাদের উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় মর্যাদা নিশ্চিত করবেন। সর্বোচ্চ বেতন দেবেন। এর পর থেকে কেউ আর ভিসি হবেন না। শুধু সি [ভাইস-চ্যান্সেলর নন, শুধু চ্যান্সেলর] হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকই হবেন। কিসের প্রসিডেন্ট? কিসের প্রাইম মিনিস্টার? প্রাইম মিনিস্টার, প্রেসিডেন্ট কি প্রফেসরের চাইতে বড়? আচার্য, জ্ঞানী, সক্রেটিস, তার ওপরে কে? কেউ না। ঠিক না? বিবেক ছাড়া আর কারও কাছে তিনি দায়বদ্ধ না। এসব আমরা চাইব বাইরের দিক থেকে। কিন্তু এটা চাওয়ার জন্য তো ভেতরে ভেতরে আমাকে রেডি হতে হবে। তার জন্য আরও কাজ আছে। ভেতরের দিকে।
ভোটাভুটি বন্ধ করে দিতে হবে
শিক্ষক-সমিতি নির্বাচন, ডিন নির্বাচন, এসব বন্ধ করে দিতে হবে। আপনি বড় জোর একটা সিনেট এবং একটা সিন্ডিকেট বানাতে পারেন। তাও ছয় মাস মেয়াদের জন্য। ছয় মাসের বেশি কোনো দায়িত্বকাল নাই। চেয়ারম্যান-ছয় মাস। ছয় মাস পর পর চেয়ারম্যান বদলান। ছয় মাস পর পর ভিসি বদলান। বাই রোটেশন।
সব শিক্ষক মিলে আপনি একটা মাত্র জায়গায় ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে পারেন। সেটা সিনেট বানানোর ক্ষেত্রে। আর, সিনেট নিজেরা নিজেদের মধ্য থেকে ১৫ জনকে ঠিক করবে, যাঁরা প্রতিদিনের কাজকর্ম দেখবেন। কিন্তু, সিনেট-সিন্ডিকেটের বেলাতেও আমরা যাঁরা ইলেক্টরাল বডি, আমরা যাঁরা ভোট দিয়ে তাঁদেরকে সিনেটর বানাব, আমরা পই পই করে লিখে দেব: এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়; এগুলো আপনাদের কাজ; সিনেটে গিয়ে এগুলো করবেন। এর বাইরে যদি কিছু করতে হয়, এসে আমাদের (সকল শিক্ষকের সাধারণ সভার) কাছ থেকে শুনে যেতে হবে।
মূলনীতি বানাবে শিক্ষকসভা
তার মানে, মূলনীতি প্রণয়ন করতে শিক্ষকসভা। দল মত নির্বিশেষে সকল শিক্ষক। সিনেট-সিন্ডিকেট ঐসব মূলনীতি বাস্তবায়ন করবে। যদি ঠিকমতো বাস্তবায়ন না করে তাহলে শিক্ষকসভা [সকল শিক্ষক] যেকোনো সময় অধিবেশনে বসে তাঁদেরকে ‘রিকল’ করবে।
‘রিকল’ করার মানে হলো ‘সালাম’ দেওয়া। ঐ যে বলে না, “ভিসি-স্যার আপনাকে সালাম দিয়েছেন?” মানে আপনার নামে সমন জারি হয়েছে। হাজিরা দিতে হবে। সে রকম, শিক্ষকসভা থেকে তখন ‘সালাম’ দিব আমরা। সিনেটরদেরকে। এটাকে ইংরেজিতে বলে রিকল করা- মানে ওমুক সাহেব আপনাকে স্মরণ করেছেন। এটার বাংলা হচ্ছে যে তোমার জারিজুরি শেষ, তোমার এমপিগিরি শেষ। মানে তুমি আর আমার প্রতিনিধি না। তোমার প্রতিনিধিত্ব বাতিল।
শিক্ষকসভা তার নিজেরই নির্বাচন করা সিনেটকে এবং সিন্ডিকেটকে (এসব সংস্থার কোনো ব্যক্তি-সদস্যকে অথবা গোটা সংস্থাটাকে) বাতিল করে দিতে পারবে। যখন তখন। শুধু যদি শিক্ষকসভা মনে করে, “আমরা যা বলে দিয়েছিলাম তা ওনারা করছেন না।”
যাই হোক, এইটুকু বড়জোর করা যেতে পারে ভোটাভুটি। আর কোথাও ভোটাভুটি না।
অনুষদের ডিন প্রসঙ্গে
ডিন পদের মনে হয় প্রয়োজনই নাই। আমি নিশ্চিত না-সম্ভবত প্রয়োজনই নাই ডিন পদের। কী কাজ ডিনের?
অনুষদ বলে তো কিছু নাই বাস্তবে। অ্যানথ্রোপলজি-ওয়ালারা অ্যানথ্রোপলি পড়েন। গণযোগাযোগওয়ালারা গণযোগাযোগ পড়েন। কোনো লেনদেন নাই। অথচ একই জিনিস-সমাজ কাঠামো-আমিও পড়ি, সমাজবিজ্ঞানও পড়ে, অ্যানথ্রোপলজিও পড়ে। ইনফরমেশন সায়েন্স আমিও পড়ি, লাইব্রেরি-সায়েন্স বিভাগও পড়ে, ইনফরমেটিক্স-ওয়ালারাও একই জিনিস ফোকলোরও পড়ে, অ্যানথ্রোপলিজিও পড়ে [ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেনোলজি বিভাগ] পড়ে। কোনো লেনদেন নাই।
তাহলে কাজ কী ডিনের? আর, ডিনের যদি কিছু কাজ থাকেও তবে সেটা শিক্ষাগত লেনদেন ও শিক্ষাগত উৎকর্ষ সংক্রান্ত। প্রশাসনিক কোনো দায়িত্বের কোনো সেটা না। ডিন যদি বানাতেই হয়, সেটা একটা বডি হলেই ভালো। ধরা যাক, গোটা অনুষদের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ পনের জন প্রফেসর। তাঁরা হলেন ডিন। অনুষদের অভিভাবক। আর, যদি একজন ব্যক্তিকেই ডিন বানাতে হয়, তবে সেটা জ্যেষ্ঠ্যতা অনুসারে। ইলেকশন দিয়ে না।
ভোট মানেই ভোটে হারার ভয়। উনি যদি কোনো একটা ভালো কাজ কখনও ভুল করে করতেও চান ভোট হারানোর ভয়ে করতে পারবেন না। এই দিকটাও কিন্তু আছে। ফলে কোন ভোট দরকার নাই।
শিক্ষক-সমিতি দরকার নাই
শিক্ষক-সমিতিরও দরকার নাই। শিক্ষক-সমিতি মানে ‘নির্বাচিত প্রতিনিধিদের’ একটা কমিটি। তো, প্রতিনিধির কী দরকার! আমিই আমার প্রতিনিধি। ৮০০ শিক্ষক আছি। ১২০০ শিক্ষক আছি। আমাদের আবার প্রতিনিধি কী! বিপদ-আপদ ভালো-মন্দ যা হোক আসি সরাসরি গিয়ে বলব যে এটা করা যাবে না; এটা করতে হবে। আমি বলব। আরও পাঁচ জনকে বলব, চলেন সবাই মিলে যাই। কখনও দশ জন যাবে। কখনও পনের জন যাবে। কখনও বিশ জন যাবে। গিয়ে বলবে- ভিসিকে বলবে, ডিনকে বলবে, অন্যদেরকে বলবে, চেয়ারম্যানকে বলবে যে এটা করা যাবে না। এর জন্য তো সমিতির দরকার নাই।
আর সমিতি মানে তো আমার প্রতিনিধি। প্রতিনিধি মানে তো আমার খলিফা। খেলাফত তো নাই। আরব আমলের খেলাফত নাই। ওমরের খেলাফত নাই। তারপর ছিল তুরস্কের খেলাফত। সাম্রাজ্য। ঐ খেলাফত ছিল সাম্রাজ্য। ঐ খেলাফত দিয়ে আমার কী লাভ এখানে!
ঐ সমিতি আমার খলিফা হবে। হয়ে আমার উপর ছড়ি ঘুরাবে। ওরা হয়ে যাবেন নেতা। এগারো-বারো জন নেতা হন। বারো জন মিলে জাতির অমুক হয়েছে, জাতির তমুক হয়েছে- এই সব বিবৃতি দেবেন। কখনও এই দলের পক্ষে, কখনও ঐ দলের পক্ষে। এই প্রতিনিধির তো কোনো প্রয়োজন নাই। শিক্ষকদরে স্বার্থ রক্ষা করার দায়িত্ব সমিতির। ঐ স্বার্থ সমিতির সকল সদস্য মিলেই দেখবেন। আলাদা কমিটির কী দরকার?
শিক্ষক-সমিতি মানে কিন্তু সকল শিক্ষক। সমস্ত শিক্ষকই শিক্ষক-সমিতির সদস্য। আর, এখন সমিতি বলতে কী বুঝায়? একটি দলের মনোনীত কিছু শিক্ষকের একটা প্যানেল, যা নির্বাচিত হয়েছে, দলের অন্ধ অনুগত ভোটার-সদস্যদের সুনিশ্চিত ভোটে। এই প্যানেল একটি কার্যকর কমিটি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু, বাস্তব অবস্থার কারণে আমাদের প্রতিদিনের ভাষায় পরিস্থিতির ছাপ পড়েছে। ফলে, কার্যকর ঐ কমিটিটার নামই হয়ে গিয়েছে সমিতি। আর, আসল যে গোটা সমিতি, ঐ শিক্ষক-সমিতির কোন খবর নাই। আমরা সকল শিক্ষক শুধু বাৎসরিক ভোটটা দেব। এটুকুই আমাদের কাজ। বাকি সব দেখবে ঐ শিক্ষক-সমিতির কমিটি। আমাদের দরকার মূল সম্পূর্ণ শিক্ষক-সমিতি। আমাদের যা ভালো-মন্দ স্বার্থ রক্ষা করা দরকার, তা ঐ সমিতির সবাই মিলে করবে। আমাদের কোনো নেতা-কমিটির প্রয়োজন নাই।
আমাদের আর কী দরকার? দরকার- শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকদের- বিপুলবিস্তৃত ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক। হাই-স্পিডের ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক। সমস্ত হল, সমস্ত স্টুডেন্ট, সমস্ত ডিপার্টমেন্ট, সমস্ত বডি কানেক্টেড থাকবে ইমেইল দিয়ে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে। সবসময় অনলাইন। সমস্ত বিজ্ঞপ্তি-সভা-সিদ্ধান্ত এগুলো সবাই পেয়ে যাবেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে। ইয়াহু গ্রুপের মতো আমার সার্ভারে ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসভা’ থাক। সবাই এর সদস্য থাকবেন। ইমেইলে সবার রাবি-ঠিকানা থাকে (যেমন romenroy@ru.ac.bd)। এখানে প্রত্যেক শিক্ষক খোলামেলা আলোচনা করতে পারবেন। কোনো সেন্সরশিপ থাকবে না।
তাই যদি হয়, যদি অনলাইনে সবসময় আমরা সংযুক্ত থাকি, যদি আমি সমস্ত শিক্ষকদেরকে ডিপার্টমেন্টে এবং বাসায় নেট সংযোগ দিতে পারি, এই মুহূর্তে ডিপার্টমেন্টগুলোতে অন্তত যদি দিতে পারি, পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে ভেবে দেখুন। অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে….. নোটিশ কী আছে, সিদ্ধান্ত কী আছে, নতুন কাজ কী আছে আমি ইন্টারনেটে জানব। পিয়ন আসবে সতের বার, বারো হাত ঘুরে ফাইল আসবে-যাবে, অ্যাত্তো বড় একটা আমলাতন্ত্র আমরা আজীবন ঘাড়ে করে নিয়ে ঘুরব ঐ জমানা নাই।
অলরেডি ঐ জামানা উঠে যাচ্ছে দিন-দুনিয়া থেকে- আমাকেও তুলে ফেলতে হবে- খুব বেশি টাকা লাগে না। অলরেডি আমার একটা সার্ভার আছে। অলরেডি একটা লাইন আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই আছে। এগুলি আপনি করেন। সবসময় অনলাইনে সংযুক্ত থাকেন। আমার ব্যাপারে যদি আমার চেয়ারপার্সন খারাপ কাজ করে, আমি তখনই এসে আমার ঐ যে আলোচনা গ্রুপ-অল টিচার্স কমিউনিটি- যেটা ইয়াহু গ্রুপের মতো গ্রুপ, ঐ গ্রুপে আমি লিখব যে আজকে আমার ডিপার্টমেন্টের চেয়ারপার্সন এই অপকর্ম করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই কিন্তু জেনে যাবেন। মেইল খুললেই দেখতে পাবেন যে অমুক খাদেমুল, অমুক নিউটন এই ভুল কাজটা করেছেন চেয়ারম্যান হিসাবে। এইটা কী প্রেশার বুঝে দেখেন? চেয়ারম্যানের উপর কী প্রেসার পড়বে এইটা। মারা লাগবে না, ধরা লাগবে না। ছিঃ ছিঃ পর্যন্ত করা লাগবে না এর আগেই খবর হয়ে যাবে। আরে বাপ, উল্টা-পাল্টা করলে খবর হয়ে যাবে!
আর কী হবে? আমরা কমিউনিটি হতে পারব। শিক্ষকরা। একটা সত্যিকারের সম্প্রদায় হতে পারব। এখন কমিউনিটি নাই। এখন কেউ ‘রংপুর’, কেউ ‘নোয়াখালি’, কেউ ‘চিটাগাং’, কেউ ‘চাপাইনবাবগঞ্জ’। ঘটনা কী? পিছনে দল আছে। লাল-নীল-হলুদ আছে। আমরা খণ্ডিত। আমাদের বড় পরিচয় দলীয় পরিচয়। শিক্ষক পরিচয়টা বড় পরিচয় না। তো, এ রকম বিস্তৃত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, (ল্যান-ইন্টারনেট), ইয়াহু গ্রুপের মতো শিক্ষকসভার উন্মুক্ত সামাজিক বিনিময়ভিত্তিক ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদেরকে অন্ততপক্ষে একটা ই-কমিউনিটি দাঁড় করাতে হবে।
বাস্তাব-মানুষের এ রকম জীবন্ত নেটওয়ার্ক যদি থাকে, আমরা স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা, সহযোগিতা, পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা, প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা কয়েম করতে পারব। এটা সম্ভব। শিক্ষার্থীরাও যদি এরকম নেটওয়ার্কের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, অনলাইনে কানেক্টেড থাকে তাহলে আমাদের গোটা জ্ঞানের, বিজ্ঞানের, পড়াশুনার, বই সম্পর্কে খবরাখবরের একটা জগৎ তৈরি করা যাবে। ভাবেন তো, আমরা সবাই অলওয়েজ কানেক্টেড আছি। গোটা বিশ্ববিদ্যালয় কমিউনিটি, শিক্ষক এবং স্টুডেন্ট। এরকম একটা চমৎকার জিনিস আর কী আছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের দিক থেকে দেখলে স্বায়ত্তশাসন-স্বাধীনতার জন্য এগুলো আমাদের দরকার।
আর বাইরের কথা তো বললামই। রাষ্ট্র যেন নাক না গলায়। রাষ্ট্র যেন না ঢোকে। আর শিক্ষকদের রাজনীতি বন্ধ করে দেন। বন্ধ তো আছেই। ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। মিটিং-ফিটিং কিছু হয় না। অবস্থা এমন, সুযোগ পেলে এখন এ কথাও রাজনীতিওয়ালারা বলে ফেলবেন যে “আমি জীবনে কোনদিনও রাজনীতি করতাম না”। কিংবা বলে বসবেন, “শিক্ষক-রাজনীতি করে ভুল করেছিলাম”। দরকাল হলে কান ধরে দুঃখ প্রকাশও করবেন তাঁরা। সুতরাং, ওটা সমস্যা না। সমস্যা হলো, চিন্তার স্বাধীনতা থাকতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঐখানে কোনো আপস না। চিন্তার স্বাধীনতা। পড়াশুনার স্বাধীনতা। বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা। শিক্ষক তাঁর বিবেক ছাড়া, তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি ছাড়া আর কারও কাছে দায়বদ্ধ হবেন না। শিক্ষার্থীরাও তাই। এইখানে আপস করা যাবে না।
অন্তত বিশ্ববিদ্যালয়-বহির্ভূত শক্তিসমূহের হাত থেকে এই স্বাধীনতার নিশ্চয়তাটুকু দেয় তিয়াত্তরের আইন। এই নিশ্চয়তাটুকু রাখতেই হবে। শিক্ষকদের রাজনীতি বন্ধ করার নামে কেউ যদি এই স্বাধীনতা বন্ধ করার কথা ভাবেন, তাহলে সেটা আমাদের রুখতে হবে।
শিক্ষার্থীদেরও স্বাধীনতা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের সভা, সমাবেশ, সংগঠন, চিন্তা, মত-প্রকাশ, সংস্কৃতি-কর্মকাণ্ড ইত্যাদি-প্রভৃতি সবকিছু করার জন্য, করার মতো স্বাধীনতা থাকতে হবে। আমি আগেই বলেছি যে শিক্ষার্থীরা এখন স্বাধীনভাবে নিজেকেই নিজে চালাতে পারেন না। তাহলে, দুই দিন পরে এমএ পাশ করে তাঁরা কেমন করে দেশ চালাবেন? কেমন করে যোগ্য অফিসার হবেন? কেমন করে সুযোগ্য মন্ত্রী হবেন? ফলে এই প্রশ্ন আপস করা যাবে না।

সূত্র: কার্টুন মুভমেন্ট
পুনশ্চ: বাজার ও বিশ্ববিদ্যালয়
এ কথা তুলছি কেন যে এখানে এই স্বাধীনতাটুকু কিছুতেই নষ্ট করা যাবে না? ভয়ে। আশঙ্কায়। আমরা ঘরপোড়া গরু। সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাই। কখনও কখনও ভয় পাওয়াটাও খুব জরুরি। ভয় পেয়েছি জানলে সমস্যা চিহ্নিত করা যায়। ভয়টা কিসের, কোত্থেকে আসলো খুঁজে বের করা যায়। এই জন্য ভয় পেয়েছি। ভয় যদি অমূলক হয়, খুব ভালো। ভয় যদি মূলক হয়, তাহলেও খুব ভালো-রুখে দাঁড়াতে হবে।
ভয়টা কিসের? রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের আশঙ্কা কথা তো আগেই বলেছি। সাথে আছে বাজারের ভয়। স্বায়ত্তশাসন মানে শুধু সরকারের হস্তক্ষেপ থেকে বাঁচা কিন্তু নয়। স্বায়ত্তশাসন মানে বাজারের হস্তক্ষেপ থেকেও বাঁচা। শিক্ষা নিয়ে দোকানদারির হাত থেকেও বাঁচা।
যে জিনিস আইনত অস্তিত্বশূন্য, অনুভবত অদৃশ্য এবং বাস্তবত অগ্রহণযোগ্য, সেই জিনিস আইন করে নিষিদ্ধ করার জন্য এখন যাঁরা উঠে পড়ে লেগেছেন (বলে যাচ্ছেন, বলে যাচ্ছেন, বলে যাচ্ছেন; তাও আবার নির্দিষ্ট করে কিছু বলেন না; বলেন ঢালাওভাবে), তাঁদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য: আপনারা আসলে কী চান? যা নাই, তা চান না- এ সবের মানে কী? আপনারা কী চান আসলে? আসলে কি তাহলে নৈশ কোর্স চান? প্রভাতী কোর্স চান? পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা চান? শিক্ষা নিয়ে শুধু ব্যবসা করতে চান? পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বানাতে চান? নামে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে, কাজেকামে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হবে, সেই জিনিস চান? তাহলে আপনারা কী চান? বাজার এবং শিক্ষা একটা আরেকটার পরিপূরক হবে- এইটা আপনারা চান? শিক্ষা পণ্য হবে-এইটা চান? যে বড়লোক সে পড়তে পারবে, যে বড়লোক নয় সে পড়তে পারবেনা – এইটা চান?
এ কথাগুলো বলার অনেক লক্ষণ বাস্তব পরিস্থিতির ইতোমধ্যে আছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মানে কী? যার পয়সা আছে সে গ্র্যাজুয়েট হবে, যার পয়সা নাই সে গ্রাজুয়েট হবে না। পরিষ্কার। এরই মধ্যে শিক্ষার্থীদের ফি-ভর্তি-বেতন ইত্যাদি পড়ালেখার খরচ বাড়ানোর আলামত শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১২ টাকার ফি ২০০ টাকা দিতে হবে, ২০০ টাকার ফি ২০০০ টাকা দিতে হবে। এই পথে কি ছাত্র-রাজনীতিই মূল বাধা? এই পথে কি শিক্ষকদের রাজনীতিই বাধা? রাজনীতি থাকলে মিছিল-মিটিং-প্রতিবাদ- বিক্ষোভ হয়, এই চিন্তা থেকেই তাহলে আপনারা শিক্ষক-রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে চান?
মাস দুই-তিনেক আগে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। চৌদ্দই ফেব্রুয়ারিতে। পত্রিকায় খবর দেখে। অনাহুতভাবে। বিনা আমন্ত্রণে। এমনকি বিনা পরিচয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিভাগে আমি লেখাপড়া করেছি, সেই গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছিলেন। পত্রিকায় দেখেছিলাম তেরোই ফেব্রুয়ারিতে।
ওঁরা আন্দোলন করছিলেন ঐ ডিপার্টমেন্টে নৈশ মাস্টার্স কোর্স চালু করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকেরা ঐখানে এ রকম সান্ধ্য কোর্স চালুর চেষ্টা করছিলেন। এর প্রতিবাদে শিশখার্থীরা বলছেন যে আমরা এর আগে আইবিএ দেখেছি। কমার্স ফ্যাকাল্টিকে দেখেছি। আমাদের বন্ধুদেরকে দেখেছি, যারা নৈশ কোর্সের শিক্ষার্থী হন, যারা প্রাইচেট কোর্সের শিক্ষার্থী হন, যারা টাকা বেতন ফি দিয়ে ভর্তি হন, ওরাই হয়ে পড়েন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থী। বিভাগের প্রথম শ্রেণির নাগরিক আরকি। আর যারা নিয়মিত শিক্ষার্থী, যারা ১২ টাকা দিয়ে পড়েন, যারা ১২ হাজার ছেলের সাথে প্রতিযোগীতা করে ভর্তি হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারা হয়ে পড়েন দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী। বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। তারা বই পান না। বই পান ওই ওঁরা (যারা বেশি টাকা দেন)।
আরও অনেক অসমতা, আরও অনেক বৈষম্য তারা দেখেছেন বাণিজ্য-অনুষদের টাকা-পয়সার নৈশ-সন্ধ্যার কোর্সগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে। তারা আরও দেখেছেন যে ঐ সার্টিফিকেটের দাম বেশি হয়, আর এই সার্টিফিকেটের দাম কমে যায়। তাদের চাকুরি পেতে অসুবিধা হয়।
তো, আমি চৌদ্দই ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে গিয়ে দেখলাম তারা স্লোগান দিচ্ছেন। তারা মিছিল করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। জরুরি অবস্থার মধ্যে। টাকটা জরুরি অবস্থা। এগারো জানুয়ারি থেকে চৌদ্দই ফেব্রুয়ারি-কয় দিন? তারা শ্লোগান দিচ্ছিলেন, – ‘বাজার এবং শিক্ষা একসাথে চলে না’, ‘ব্যবসা এবং শিক্ষা একসাথে চলে না’, শিক্ষা সুযোগ না- অধিকার, অধিকার’। কোনো দল করেন না তাঁরা – আমি খোঁজ নিয়ে দেখলাম।
আমি গিয়েছিলাম তাদের সাথে সংহতি জানানোর জন্য। আমার কাছে মনে হচ্ছে একুশ শতকের বাংলাদেশের জন্য এটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। এটাই সবচাইতে মারাত্মক প্রশ্ন: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজার হবে, নাকি হবে না। অভিভাবকদের আয় নির্বিশেষে (ধনী-গরিব নির্বিশেষে) সবার জন্য শিক্ষার অবাধ সুযোগ (পারলে বিনা পয়সার অবাধ সুযোগ) কি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাখবে? নাকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দোকানদারিতে পরিণত হবে?
এইটা হচ্ছে একুশ শতকের বাংলাদেশের সবচেয়ে মারাত্মক প্রশ্ন। কেন? কারণ হচ্ছে, মনে রাখবেন, একটু খেয়াল করবেন যে বিশ্ববিদ্যালয় মানেই বাংলাদেশ ছিল। বাংলাদেশ- আন্দোলনের, বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠার ইতিহাস আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস এক-ই ইতিহাস। সরদার ফজলুল করিমের বই দেখবেন। আবদুর রাজ্জাকের সাক্ষাৎকার দেখবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনই বাংলাদেশ-আন্দোলন।
বাংলাদেশের শ্রমিক, বাংলাদেশের কৃষক, বাংলাদেশের আপামত মানুষ বাংলাদেশ বানিয়েছেন। কোনো সন্দেহ নেই। আব্দুর রাজ্জাক বহুকাল প্রশ্ন তুলেছিলেন। বাংলাদেশ যে একটা ‘জাতি’, এটা হয়ে উঠলো কেমন করে? একটা ‘নেশন’ কীভাবে ‘নেশন’ হয়? কিভাবে? মানুষ চান বলে। শুধু চান বলে, আর কিছু না। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোক চেয়ে যে আমরা বাংলাদেশ- ব্যাস, বাংলাদেশ হয়েছে। আর কিছু না।
আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আলাদা গুরুত্ব দিচ্ছি না। কিন্তু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য গুরুত্ব আছে। এবং সেই গুরুত্ব আজকের জমানায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ই বহন করে। আগামী দিনের বাংলাদেশ কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেমন হবে তার ওপরই নির্ভর করে।
এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কী ‘কলেজ’ হয়ে যাবে? সরকারি কলেজের মত? আপনি মনে মনে ধরেন, সরকারি কলেজগুলো স্বাধীন। অসুবিধা আছে কোনো ভাবতে? [আমরা চাই, কলেজগুলোই বরং স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠুক।] বাস্তবে স্বাধীন না। শিক্ষকরা সব কেরানি হয়ে আছেন। গিয়ে দেখেন। (ব্যতিক্রম আছে- অন্য হিসাব সেটা।) তাহলে যারা চান নানা কিছু নিষিদ্ধ-টিষিদ্ধ করতে, তাঁরা কি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ঐরকম কলেজ বানাতে চান? তাঁরা আসলে কী চান? বাংলায় বলতে হবে। ভেঙ্গে বলতে হবে। ঢালাও করে বললে হবে না।
বিজ্ঞাপনই সংবাদ: ‘দাগ নেই তো শেখাও নেই’
প্রসেফর ইয়াহিয়া ঢালাও বলে দিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কনসালটেন্সি করে। ইচ্ছা হলে এরা ‘গবেষণা’ করে বলতে পারতেন যে সংবাদপত্র সংবাদ তেমন ছাপে না, শুধু বিজ্ঞাপন ছাপে। সেটা তাঁরা বলবেন না। সেটা বলার মতো ‘ফান্ড’ নাই। ওগুলো বলার জন্য কেউ টাকা দেয় না।
সাংবাদিকের কাজ তো সংবাদ ছাপা, সংবাদ সংগ্রহ করা, যেমন আমার কাজ পড়ানো। আমি যদি না পড়িয়ে কনসাল্টেন্সি করি সেটা যেমন অপরাধ হয়, সংবাদ না ছাপিয়ে হকবর ছাপালে একই অপরাধ হয়। সংবাদপত্র মানে তো বিজ্ঞাপনপত্র। খুলে দেখেন। বিজ্ঞাপনই সংবাদ। টিভি চ্যানেল মানে বিজ্ঞাপনের চ্যানেল। বিজ্ঞাপন যেন লোকে দেখেন, তার জন্যই ‘খবর’ প্রচার করা হয়।
সুতরাং, আমাদের এই বিজ্ঞাপনী সুশীল সমাজ (সুশীল বণিক সমাজ) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কী চান, সেটা আগে আমাদেরকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে।
প্রফেসর ইয়াহিয়া নিজে ঐ রিপোর্টটা বানানোর জন্য টিআইবি’র কাছে কত টাকা নিয়েছেন এটা আমার জানতে হবে। এবং ঐ রিপোর্টটা লেখার জন্যে, ঐ ফরমায়েশি ‘গবেষণা’টা করার জন্য কতগুলো ক্লাস ওনাকে বাদ দিতে হয়েছে, আদৌ বাদ দিতে হয়েছে কিনা আমাকে জানতে হবে। ধরলে সবই ধরবেন। শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে ধরবেন, আর গোটা সমাজ বাজার হয়ে গেলেও, কোনো অসুবিধা বোধ করবেন না, তা তো হয় না।
আপনি বলবেন, রাজনৈতিক দলের তহবিলের হিসাব-নিকাশ চাই। আমি বলব, প্রথম আলোয় আয়ব্যায়ের হিসাব-নিকাশ চাই। টিআইবির হিসাব-নিকাশ চাই। টিআইবিতে প্রফেসর মোহাফফর আহমেদের বেতন কত জানতে চাই। টিআইবির বাজেট জানতে চাই। কে কে টাকা দেন? কোন দেশ টাকা দেয়? কেন দেয়? কত টাকা দেয়? কত খরচ হয়? টাকাগুলো কে পান? কারা পান? কিভাবে টিআইবি’র কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়? দুর্নীতি হয় কিনা? সব জানতে চাই। সুশীল পত্রিপত্রিকাতে এসব নিয়ে বড় বড় রিপোর্ট চাই। গ্রামীণফোনে কী হয়? কত টাকা লুটপাট হয়েছে? কারা কারা ঘুষ পেয়েছেন? টেলিটককে পঙ্গু করার জন্য গ্রামীণফোনের ভূমিকা কী ছিল জানতে চাই। এগুলো নিয়ে তো কোনো রিপোর্ট হয় না।
আপনি যদি বলেন যে পলিটিকাল পার্টির মূল নেতা দুই মেয়াদের বেশি সভাপতি-সেক্রেটারি পদে থাকতে পারবেন না, আমি বলব প্রথম আলোর সম্পাদকের সম্পাদকগিরির মেয়াদ কয় বছর? আমাদেরকে জানতেই হবে। কয় বছর তিনি সম্পাদক থাকবেন? এ যাবৎ তো আছেনই, যত দিন বেঁচে আছেন, বদলাবে বলে তো মনে হচ্ছে না। ডেইলি স্টারের মাহফুজ আনাম কবে বদলাবেন?
ওনারা যাবজ্জীবন সম্পাদক থাকবেন- কোনো অসুবিধা নাই। আর হাসিনা যাবজ্জীবন সভাপতি থাকলে পরে অসুবিধা। এটা অন্যায় কথা।
আমি হাসিনার প্রতি এ ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল নই মোটেই। খালেদার প্রতিও না। নিশ্চয়ই এতক্ষণে সেটা বোঝা গিয়েছে। যাবতীয় পলিটিকাল পার্টিকে আমি অন্ধত্বের আখড়া মনে করি। সাধারণভাবে। গণবিরোধী মনে করি। একদম গম্ভীরভাবে বলছি। ফলে, আমার কোনো সহানুভূতি তাঁদের প্রতি নাই।
আমি আরও জিজ্ঞাসা করব, প্রথম আলোতে সাংবাদিকদের গণতন্ত্র আছে? সাংবাদিকরা কি স্বাধীন? স্বাধীনভাবে লিখতে পারেন? ভিন্নমত প্রকাশ করতে পারেন? প্রথম আলোর পলিসি ঠিক করেন কারা? সামগ্রিক অর্থে, মিডিয়ার পলিসি ঠিক করেন কারা? সাংবাদিকরা? না। সম্পাদকবৃন্দ আর মালিকগণ। ঐ সেই আমরা আর মামুরা। আম্মুরা আবার আব্বুরা- মিডিয়ার। আমি জানতে চাই, সাংবাদিককে ডেকে কি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনারাই তো সবাই পত্রিকা বানাচ্ছেন, আপনাদেরকে নিয়েই তো প্রথম আলো চলে, তো আপনারাই বলেন, প্রথম আলোর পলিসি কেমন হওয়া উচিৎ। কোনো মিডিয়া এটা করে? পৃথিবীর কোনো দেশে এটা করা হয়? আমেরিকার ‘স্বাধীন’ মিডিয়া এটা করে? মনে রাখা দরকার: ওখানেও ডেমোক্রেসি নাই। ওখানেও জবাবদিহিতা নাই। ওখানেও স্বচ্ছতা নাই। ওখানেও সাংবাদিকের কোনো অধিকার নাই। সব সংস্কার করবেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে আর পলিটিক্যাল পার্টির উপরে- এটা তো হবে না।
এগুলোই কিন্তু ইস্যু। গোটা দেশের ভালোমন্দের ক্ষেত্রে এগুলো তো মহাগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সুতরাং, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার তো করতেই হবে। আমরা সেটা বহুদিন ধরেই চাচ্ছি। কিন্তু, এবার আমরা সবার আগে মিডিয়ার সংস্কার চাই। আমরা সুশীল সমাজেরও সংস্কার চাই। আমরা গোটা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ারই সংস্কার চাই।
ইদানিং সিগারেটের বিজ্ঞাপন ‘নিষিদ্ধ’ হয়েছে। আমরা দাবি করব, সংবাদপত্রে খোদ বিজ্ঞাপনই নিষিদ্ধ করতে হবে। কেন বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে? কোন আইনে? কোন যুক্তিতে? ওটা তো নিউজ-পেপার, তাই না? ‘নিউজ’ এর কাগজ। বিজ্ঞাপনপত্র তো নয়!
আপনার পয়সা আছে, কড়ি আছে, মেশিন আছে, টেকনোলজি আছে। আপনি বিজ্ঞাওনের জন্য আলাদা পেপার বানান না। এ্যত্তো বড়ো করে বানান। রঙ-চঙ সব দেন ওইখানে অসুবিধা নাই। কয়জন পড়ে দেখি ওই পত্রিকা? বিজ্ঞাপনের যদি সত্যিকারের চাহিদা থাকে তাহলে পড়বেই, তাই না? কিনে পড়বে। আমার যদি প্রয়োজ থাকে খবর জানার যে কোন মাল কোথায় কিনতে পাওয়া যায়, তাহলে তো ওটা কিনে পড়ব আমি।
সুতরাং, বিজ্ঞাপনের জন্য আলাদা করে বিজ্ঞাপনপত্র বানান। বিজ্ঞাপনের জন্য আলাদা টিভি-চ্যানেল বানান-বিজ্ঞাপন চ্যানেল। কমার্সিয়াল টিভি চ্যানেল আলাদা করে বানান না! নিউজ চ্যানেলের মধ্যে বিজ্ঞাপন দেন কেন? নাটকের মধ্যে বিজ্ঞাপন দেন কেন?
আসলে কী হয়, জানেন তো? মিডিয়া তার পাঠক-দর্শক-শ্রোতাকে বেচে দেয়। বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বেচে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে গিয়ে বলে, এই দেখেন মার্কেট রিসার্চ, এই দেখেন বাজার জরিপ। অমুখ বিখ্যাত বাজার-গবেষণা-প্রতিষ্ঠান (তৈরিই আছে অলরেডি এগুলো) তারা সার্ভে দেখেছেন যে প্রথম আলো যারা কেনেন, তারা আপনার পণ্য/সেবার সম্ভাব্য খুব ভালো ক্রেতা। তাদের পয়সা আছে। তারা আপার ক্লাস। এবং আপনার পত্রিকার সার্কুলেশন চার লক্ষ। চার লক্ষ লোক আপনার পত্রিকা পড়ে। সুতরাং, এখানে আপনারা যদি বিজ্ঞাপন দেন, তাহলে আপনার বিজ্ঞাপন সার্থক হবে।
সার্থক হয়ও। তাঁর মানেটা কী? এই চার লক্ষ পাঠককে পত্রিকার মালিকেরা বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে গিয়ে বেচে দেন। অর্থাৎ, আপনি এবং আমি হচ্ছি প্রথম আলোর আসল প্রোডাক্ট- সেলস প্রোডাক্ট। তার আসল পণ্য ‘নিউজ’ না। তার আসল প্রোডাক্ট প্রথম আলোও না। আমাদেরকে বেচেই মিডিয়া বড়লোক হয়। [পণ্য হিসেবে আমাদের মালিক, মিডিয়ার মালিক, বিজ্ঞাপনের মালিক, আর বিজ্ঞাপনী পণ্যের মালিক সবাই একই শ্রেণির লোক। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থে শ্রেণিগত দিক দিয়ে।]
সঙ্গে অন্যান্য সুবিধার দিকও আছে বৈকি। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জন করা, ব্যবসার জন্য সামগ্রিক একটি ইতিবাচক বাতাবরণ তৈরি করার কাজে মিডিয়াকে লাগাতে পারা, নিজের নিজের কমার্শিয়াল-কর্পোরেট হাউসের সুনির্দিষ্ট স্বার্থ রক্ষা করা, শ্রেণিগত স্বার্থ রক্ষা করা এগুলো তো সব আছেই। সংক্ষেপে এই হচ্ছে মিডিয়ার পলিটিকাল ইকোনমি।
সুতরাং, এক্ষুনি স্বাধীন মিডিয়া কমিশন চাই। এই কমিশনের কাজ হবে মিডিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা- প্রতিদিন। সারাবছর ধরে। বিদ্যমান নামকাওয়াস্তে প্রেস কাউন্সিল চাই না। এই মিনমিনে প্রেস কাউন্সিল দিয়ে কিচ্ছু হয় না। আমরা চাই একটা স্বাধীন মিডিয়া মনিটরিং কমিশন। যে কমিশন সারা বছর ধরে প্রতিদিন মিডিয়া পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) করবে। মিডিয়া কী রিপোর্ট করেছে, কী রিপোর্ট করে নি; কী চেপে গিয়েছে, কী সামনে তুলে এনেছে; কেন আনল, কেন আনল না- এইসব তারা দেখবেন, বুঝবেন, সবাইকে জানাবেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য যথাযথ জায়গায় সুপারিশ করবেন। ব্যাপক জানাজানি, আলাপ আলোচনা হলে মিডিয়ার বিদ্যমান অবস্থার ওপর সত্যিকারের চাপ আসবে। পরিবর্তনের চাপ। এই কমিশনের কাছে আমি (পাঠক) নালিশ করতে পারব। এটা হবে রাষ্ট্রীয়-সাংবিধানিক মর্যাদার, স্বাধীন, শক্তিশালী একটা কমিশন। এই কমিশনের কাছে মিডিয়ার জবাবদিহি করতে হবে। ব্যাখ্যা করতে হবে তারা কী করেছেন, কেন করেছেন।
শুধু তালিকাভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের লেখাই নয়, পাঠকের লেখাও মিডিয়ায় ছাপতে হবে। যদি না ছাপেন তাহলে লিখিতভাবে জানাতে হবে। কেন ছাপলেন না সেটাও জানাতে হবে বৈকি। কী দোষ ঐ লেখার। আপনার যে লেখা পছন্দ হয় ঐ লেখা ছাপবেন, যে লেখা পছন্দ হয় না ঐ ছাপবেন না। মাঝখান থেকে যে লেখা আপনি ছাপবেন ঐ লোক হয়ে যাবে বুদ্ধিজীবী, আর যে লেখা আপনি ছাপবেন না ঐ লোক হয়ে যাবে মূর্খ- এটা কোন খেলা? এটা কোনো ধরনের সুশীল আচরণ? (এটা শুধু বাংলাদেশের মিডিয়া নিয়ে প্রশ্ন না, সারা দুনিয়ার মিডিয়া নিয়ে প্রশ্ন। খুব ন্যায্য প্রশ্ন, গোড়ার প্রশ্ন)
এগুলো নিয়ে আপনি আলাপ তুলবেন না, অথচ আপনি গোটা সমাজ সংস্কার করবেন, রাজনৈতিক দল বদলে ফেলবে, রাষ্ট্র বদলে ফেলবেন, নির্বাচন কমিশন বদলে ফেলবেন। অন্যদিকে শুধু বাজারটা বদলাবেন না। কর্পোরেট সেক্টরকে বদলাবেন না। আর, ভাব নিবেন আপনি বাংলাদেশের মঙ্গল করছেন।
বাচ্চাদেরকে ছবি আঁকা শেখাতে হবে। দায়িত্ব কার? সার্ফ এক্সেল – এর। ‘দাগ নেই তো শেখাও নেই’। সার্ফ এক্সেলের ‘পার্টনার’ কে? কখনো প্রথম আলো, কখনও দ্বিতীয় আলো, কখনও অন কোনো মিডিয়া। ঘোষিত অংশীদার। ব্যবসায়িক অংশীদার। সুতরাং কে কার পার্টকার সেটা বেস পরিষ্কার। গোপন করার কিচ্ছু নাই। বাচ্চাদেরকে অংক শেখাতে হবে। স্কুলগুলো শেখাতে পারে না। [অকার্যকর ইস্কুল। ব্যর্থ বিদ্যালয়]। তাহলে শেখাবে কে? প্রথম আলো শেখাবে। অঙ্ক। ভাগ্যিস, বড়দের অঙ্ক শেখানোর প্রকৃত হিসাবটা এখনো বুঝে ফেলেনি অবুঝ বাচ্চারা।
হাসির একটা গল্প আছে। গৃহশিক্ষক এক দিন সন্ধ্যায় ‘বেয়াড়া’ দুই বাচ্চাকে অঙ্ক করাচ্ছিলেন। তো, এই দুই বাচ্চা আবার অঙ্ক না করার ক্ষেত্রে তুলনারহিত সফলতা অর্জ করেছে ততদিনে। এই শিক্ষক দায়িত্ব নিয়েছেন ‘বিশেষ দায়িত্ব’ হিসেবে। শিখিয়েই ছাড়বেন অঙ্ক। তো , গল্পের ছলে তিনি বাচ্চাদেরকে চাঁদ-তারা-কাশা-গ্রহ-নক্ষত্র দেখাচ্ছেন। বাচ্চারা খুশি। এই স্যার ভালো। শিক্ষক এখন বাচ্চাদের বলছেন, ঐ দেখ কত সুন্দর দুইটা তারা, আর তার পাশেই আরও তিনটা তারা। আচ্ছা বল তো, তাহলে কয়টা তারা হলো? বাচ্চারা বিভ্রান্ত। দুই সেকেন্ড অতিক্রান্ত। তখন ছোট বাচ্চাটা বড় বাচ্চাকে বলছে, ‘বলিস নে ভাই, স্যার কিন্তু অঙ্ক করাতিছে!” ত, গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা দেখিয়ে দেখিয়ে প্রথম আলো জাতিকে অঙ্ক করাচ্ছে। কী অঙ্ক করাচ্ছেন তারা, সেটা অবশ্য আমাদের খতিয়ে দেখাটা উচিৎ হবে।
অঙ্কের গণিত তো আছেই। ব্যবসারও গণিত আছে। বাণিজ্যেরও তো গণিত আছে। গণিত আছে প্রচারণার। আছে তারকা-বুদ্ধিজীবী-বীজগণিতও। এইচএসবিসি’র মতো সত্যিকারের ব্যাংকিং-গণিতও আছে। ওখানে আবার হাইকোর্টও আছে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড। গ্রামীণফোনের গণিতও আছে।
আপনি গণিত শেখানোর উৎসব করবেন। ওখানে গ্রামীণ ‘ডিজুস’ আপনার পার্টনার হবে। আপনার-আমার বাচ্চারা ডিজুসের প্রথম আলোর পট্টি মেরে, টিশার্ট ইউনিফর্ম পরিধানপূর্বক গণিত উৎসবে হাজির হবে। প্রথম আলোতে ফটো যাবে। আপনি প্রফেসর আব্দুল্লাহ আবু সাইদ হবেন। আপনি বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাবেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়া প্রতিযোগিতা হবে। সেই প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণী হবে (ঢাবি) চারুকলার বকুলতলায়। ওখানে কী হবে?
গণিতের ফাঁকে ফাঁকে, বিজ্ঞাপনী ব্রেকের মধ্যে, বাচ্চারা সবাই নেসক্যাফে খাবে। [ব্রিটিশদের চা-খাওয়ানোর কথা আমাদের তবু মনে পড়বে না।] হাতে হাতে নেসক্যাফের মগ যাবে মাগনা মগ। ছোটবেলায়ই ঘুষ। মাগলা নেসক্যাফে। মাগনা মগ। এবং ঐ মগওয়ালা ছবি পরের দিনের পত্রিকায়। বাচ্চা খুশি। আপনিও খুশি। বাচ্চা মানুষ হচ্ছে। ডিজুস হচ্ছে। নেসক্যাফে হচ্ছে। গণিতটা পরিষ্কার। আগামী দিনের কর্পোরেট-ক্রেতা হয়ে উঠছে আজকের গণিতের বাচ্চারা। এটা হচ্ছে গোটা সমাজকে বাজার বানানোর রাস্তা।
তো, ওনারা সব সংস্কার করবেন। কিন্তু বাজার সংস্কার করবেন না। মিডিয়া সংস্কার করবেন না। এইটা তো হয় না। এই জন্যেই আমরা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিপুল তহবিলে সমৃদ্ধ, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মিডিয়া পরিবীক্ষণ কমিশন চাই। সেখানে আমরা প্রচুর এক্সপার্টের প্যানেলে বানিয়ে কাজ করব। বিপুল সংখ্যক কর্মীর প্যানেল। সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা সেখানে কাজ করবেন। শিখবেন। এক হাজার দুই হাজার লোকের প্যানেলে সারা বছর কাজ করবে। মিডিয়া কী করছে, কী করছে না।
আপনারা সারাবছর সবার সবকিছু দেখে বেড়াবেন, মনিটরিং করে বেড়াবেন, আর আমরা আপনাকে মনিটরিং করব না? এ তো বিপজ্জনক কথা। এমনিতেই আপনারা বিশাল ক্ষমতাধর। আপনারা দিনকে রাত, রাতকে দিন বানাতে পারেন। আপনারা বললে কানসাটের রাব্বানী বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে যায়। (হয়ে যায় যায় ভাব। পরে এমপি নির্বাচনে ফেল!) আপনি বললে মনে হয় বাগমারার এমপি আবু হেনা ছাড়া মৌলবাদ থেকে বাঁচার উপায় নাই। আবার, আপনি বললে দুই দিন পর মনে হয়, ঐ একই আবু হেনার নিজেরই জঙ্গি-সংযোগ আছে। তাই না? সুতরাং, মিডিয়াকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রীয় কমিশনের কাছে জবাবদিহি করতেই হবে।
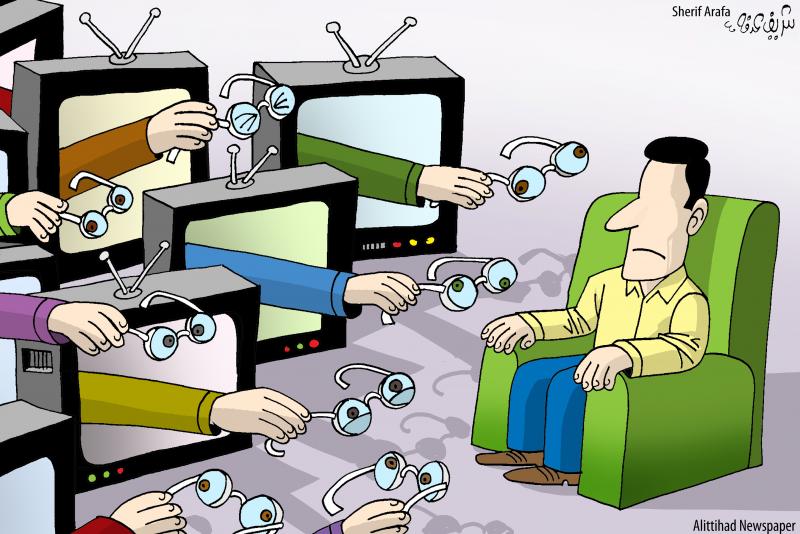
সূত্র: কার্টুন মুভমেন্ট
সক্রিয়তা ছাড়া কোনো পথ খোলা নাই
এই তো আলাপ। সবশেষে একটা সতর্কবাণী। বাজার-বিশ্ববিদ্যালয়-রাষ্ট্র-সমাজ ও মিডিয়া সম্পর্কে আজকে আমরা অনেক গড় পর্যবেক্ষণ এখানে হাজির করেছি। এসব পর্যবেক্ষণের পক্ষে বিস্তারিত নথিপত্র হাজির করা দরকার। এসব নিয়ে ভুরিভুরি পত্রপত্রিকা-ছোটকাগর-চটি-পুস্তিকা-প্রবন্ধ উৎপাদন করা দরকার। কেউ একা এসব কাজ করা সম্ভব নয়। অনেক লোক, অনেক শিক্ষার্থী, অনেক পাঠক, অনেক শিক্ষক মিলে যদি কথা বলে শুরু করেন, যদি গুছিয়ে শান্তভাবে কথা বলেন, যদি নিজের কাজের দায়িত্ব নিজে নেন, নিজের কথাটুকু যদি অন্তত নিজে বলেন, তাহলেই বিশ্ববিদ্যালয় বদলাবে; সমাজ বাদলাবে।
সমাজ পরিবর্তন হোক, বিশ্ববিদ্যালয় বদলাক, এগুলো আমরা চাই। শুধু অমুক সরকার চায় বলে যদি আমরা আজকে এটা চাই, তাহলে আমাদের জন্য সমূহ বিপদ হবে। এরকম চাপানো সংস্কারের চাপে আমাদের মূলধন যেটুকু আছে অন্তত, সেটুকুও গাপ হয়ে যাবে। সংস্কার আমরা চাই। কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু, মৌলিক একটা প্রশ্নে আমরা কক্ষনো সংস্কার চাই না। সেটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নে। আমার অক্ষমতাই আমার স্বাধীনতার সীমা। এর জন্য শিক্ষকদের এবং শিক্ষার্থীদের, শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকদের সক্রিয়তা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নাই।
এই তো! সবাইকে ধন্যবাদ এ রকম একটা বিরক্তিকর বকর-বকর অনুগ্রহ করে শোনার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ। আর, ধন্যবাদ দেওয়ার আসলে কী আছে? এটা তো আজকে আমরা সবাই মিলে আয়োজন করেছি। ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নাই আসলে। যারা শ্রোতা, তারা তো আমরাই। ঠিক না? এবং আমরা আসলে এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলতে চাই বলেই তো এখানে এসেছি। ফলে, আমরাই আয়োজন। আমরাই শ্রোতা। আজকে আমি বক্তা। কালকে আরেক জন বক্তা হবেন। তবু, ধন্যবাদ।
আপনাদের প্রশ্ন-আলোচনা-মন্তব্য থাকলে মঞ্চে এসে করবেন।
অন্তঃটীকা
১. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১২৩ নম্বর ক্লাস রুমের চাবি।
২. ‘অন্য কোনো রকম বিঘ্ন’ বলতে এখানে ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে দেশ জুড়ে জারিকৃত জরুরি অবস্থা-জনিত চরম আতঙ্কের পরিবেশকে বোঝানো হচ্ছে। এখানে উপস্থাপিত আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয় জরুরি অবস্থার মাত্র চার মাসের মাথায়। ভুলে গেলে ভুল হবে, ‘জরুরি’ বিঘোষিত রাষ্ট্রযন্ত্রের তখন রীতিমতো নওজোয়ান তেজ। বাঘ আর হরিণেরা এক ঘাটে নাকানিচুবানি খাচ্ছে। বাচ্চারা গোয়েন্দা সংস্থার নাম মুখস্ত করছে। আতঙ্কে অজগর সাপ গড়াগড়ি রাস্তায়। ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া কুমির আত্মপ্রকাশ করছে ডোবায়। এখনকার খোলামেলা গণতান্ত্রিক পরিবেশ এসে আতঙ্কের সেই দমবন্ধ সময়কে সত্যিকারের অর্থে অনুভব করা সহজ নয়। সেটা ছিল ঘোরতর অন্ধকার কাল।
৩. সামরিক-বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। তাদের অনেকেই সেইদন শ্রোতাদের মধ্যে বসে ছিলেন। আলোচনার পরদিন তো এদের একজন আমাকে স্বতঃস্ফূর্ত গলায় ফোন করে জানিয়েছিলেন, তিনি আমার আলোচনা থেকে উপকৃত হয়েছে। এটা ছিল গোয়েন্দাদের পর্যবেক্ষণ, প্রশংসা, জিজ্ঞাসাবাদ, অত্যাচার, কৃতজ্ঞতা জানানো এবং দুঃখপ্রকাশ করার কাল।
৪. ‘ক্ষমতা’ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানতম চাবি-শব্দ। ছোট্ট একটু নমুনা-বাক্য দিই: ‘অগণতান্ত্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চললে এমন সন্ত্রাস-চাদাবাজি-টেন্ডারবাজি- অস্ত্রবাজি চলতেই থাকবে। নির্বাচিত ছাত্র-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দিতে পারলেই শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গল হবে’। (মুহম্মদ আবদুস সোবহান, ২০১০: ১৬; মোটা হরফ সংযোজিত। এরকম নিদারুণ বিবৃতিতে ‘ক্ষমতা’ বলতে কী বোঝায়, তা সহজেই অনুমেয় ‘গণতান্ত্রিকভাবে’ যে ছাত্ররা ‘ক্ষমতা’ আবেন, তাঁরাই হবেন বৈধ ক্ষমতার অধিকারী, ক্ষমতার বাকি সব ‘অবৈধ’ দাবিদারকে তাঁরা আইনসম্মতভাবে নিকাশ করে দেবেন খোদ রাষ্টড়যন্ত্রের ‘বৈধ’ বাতাসে, রাষ্ট্রীয় লু হাওয়ার ঝাপ্টায়। তাতে যে অস্ত্রবাজি বন্ধ হয় না সে কথা ডাকসু, চাকসু, রাকসু, জাকসুর ইতিহাস দেখলেই যথেষ্ট বোঝা যায়। ছাত্র সংসদ মানেই আরও সন্ত্রাস, লাশ।
৫. অনেকেই আছেন, যারা স্নেহ করেন, প্রশ্রয় ও উৎসাহ দেন, চমৎকার সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। সংখ্যায় এঁরা ন্যূন নন মোটেও। বিশেষ কোনো দলের লোকও নন। তথাপি, সকলে নির্দলীয়ও নন। এদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। বলাটা নিতান্তই বাহুল্য।
তথ্যসূত্র
বাকুনিন, মিখাইল (১৮৭১)। হোয়াট ইজ অথরিটি’। পিঅ্যানার্কি।
বাকুনিন, মিখাইল (১৯৫৩)। পাওয়ার এন্ড অথরিটি’। জিপি ম্যাক্সিমফ সম্পাদিত, দি পলিটিক্যাল ফিলসফি অব বাকুনিন। ইলিনয়: ফ্রি প্রেস
সেন, দীনেশচন্দ্র (২০০৮)। রামায়নী কথা । প্রথম প্রকাশ: ১৯০৪। ঢাকা: পড়ুয়া
সোবহান, মুহম্মদ আবদুস (২০১০)। ‘শিবিরের হামলা দেশকে অস্থিতিশীল করার পরিকল্পনারই অংশ’। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহম্মদ আবদুস সোবহানের বিশেষ সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার গ্রহণ: বাঁধন অধিকারী। কালের কণ্ঠ, ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১০।




