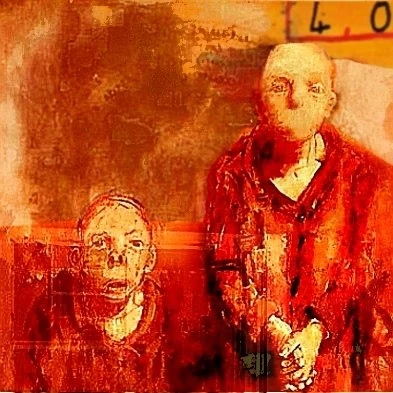- অনুবাদ: আরিফ রেজা মাহমুদ
[রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে ফ্যাসিবাদের আগমন ঘটে গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই ইতালিতে ফ্যাসিবাদ একটি স্বতন্ত্র মতাদর্শ হিসেবে আবির্ভূত হয়, এবং জার্মানিসহ অন্যান্য দেশেও এর প্রসার ঘটে। ইতালির স্বঘোষিত ফ্যাসিস্ট নেতা, বেনিতো মুসোলিনির শাসনামলে ফ্যাসিবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করা হয়। তখনকার সাথে বর্তমান দুনিয়ায় ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলোর একটি বড় তফাৎ হচ্ছে, এখন আর কোনো ফ্যাসিবাদী শক্তিই নিজেকে ফ্যাসিবাদী বলে ঘোষণা করে না। বরং ফ্যাসিবাদ কথাটিকে বিরোধী শক্তিগুলোই ব্যবহার করে থাকে কর্তৃত্ববাদী, স্বৈরশাসনকে বোঝানোর জন্য। আবার কেবল কর্তৃত্ববাদী, স্বৈরশাসন হলেই তা ফ্যাসিবাদ নয়। গেল শতাব্দীর ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন, ফ্যাসিবাদকে ‘ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া একনায়কত্ব’ হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু এথেকে ফ্যাসিবাদের চিন্তা-মতবাদের আকর ও পাটাতন বোঝা সম্ভব হয় না। আমাদের দেশেও ফ্যাসিবাদ কী সে ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট তাত্ত্বিক বোঝাপড়া তৈরির চেষ্টা সামান্যই হয়েছে। ফলে ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিবাদী মতাদর্শ চিহ্নিত করাও সবসময়ই সম্ভবপর হয়ে উঠে না। সে উদ্দেশ্য নিয়েই অরাজ ফ্যাসিবাদের বোঝাপড়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক দলিলসমূহ লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করছে। তারই অংশ হিসেবে মুসোলিনির ১৯৩২ সালে প্রকাশিত Doctrine Of Fascism রচনাটির অনুবাদ প্রকাশ করছে অরাজ। ইতালীয় ভাষায় এই রচনার শিরোনাম La dottrina del fascismo। কথিত আছে, পুরো রচনাটি মুসোলিনির নামে প্রকাশিত হলেও এর প্রথম অংশটুকু Fundamental Ideas ইতালীয় দার্শনিক জিওভান্নি জেনতিল্লের লেখা। আর Political and social doctrine অংশটুকু মুসোলেনির, যা লিখিত হয় ১৯২৭ সালে। Doctrine Of Fascism রচনাটির ফ্যাসিবাদী সরকারি কর্তৃপক্ষ প্রণীত ইংরেজি সংস্করণের অনুবাদক ব্রিটিশ লেখক জেন সোয়ামস। বর্তমান বাংলা অনুবাদে ফ্যাসিবাদী প্রকাশনার রাষ্ট্রীয় সংস্থা Ardita Publishers কর্তৃক Fascism: Doctrine and Institutions সংকলনে প্রকাশিত সংস্করণকে (১৯৩৫) অনুসরণ করা হয়েছে। অরাজের পাঠকদের জন্য লেখাটি অনুবাদ করেছেন আরিফ রেজা মাহমুদ। — সম্পাদক]

সকল সুস্থিত রাজনৈতিক ধারণার ন্যায়, ফ্যাসিবাদও কর্ম ও চিন্তার সমন্বিত রূপ, যার মধ্যে নিহিত আছে এমন এক মতবাদ, যা একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক শক্তিসমূহের অন্তর্গত বলয়ে উদ্ভূত এবং আভ্যন্তরীণভাবে কার্যকরী। সুতরাং, ফ্যাসিবাদের একটি রূপগত বিন্যাস রয়েছে যা কালিক ও স্থানিক ঘটনাপ্রবাহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; তবে এর পাশাপাশি একটি আদর্শবাদী অন্তর্বস্তুও বর্তমান, যা একে চিন্তার ইতিহাসের উচ্চতর স্তরে সত্যরূপে ব্যক্ত করে।
বিশ্বে আত্মিক প্রভাব বা প্রভুত্ব বিস্তার, অর্থাৎ একের ব্যক্তিগত ইচ্ছার দ্বারা অপরের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ, কেবলমাত্র তখনই সম্ভব, যখন কর্মক্ষেত্রের স্বল্পস্থায়ী ও বিশেষ বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয়, এবং সেই স্বল্পস্থায়ী বাস্তবতার অন্তরে নিহিত চিরন্তন ও সার্বজনীন বাস্তবতার উপলব্ধি থাকে। মানুষকে জানার জন্য ‘মানবসত্তা‘কে জানতে হয় এবং মানবসত্তাকে জানার জন্য অপরিহার্য হলো বাস্তবতা ও তার বিধিবিধান সম্পর্কে গভীর বোধ।
রাষ্ট্র বিষয়ক কোনো ধারণাই প্রকৃতপক্ষে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না, যদি তা মৌলিকভাবে জীবন–দর্শনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে প্রতিফলিত না হয়। সেটা হতে পারে দার্শনিক প্রক্রিয়াজাত ধারণা কিংবা প্রত্যক্ষ অন্তর্দৃষ্টি, যুক্তিনির্ভর কাঠামোর মধ্যে বিবর্তিত একটি ভাবতাত্ত্বিক পদ্ধতি অথবা বিশ্বাসভিত্তিক একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে কেন্দ্রীভূত অভিজ্ঞান; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই, অন্তত সম্ভাব্যভাবে, তা বিশ্বের প্রতি একটি সংহত জৈবিক ধারণার প্রকাশমাত্র।
ফ্যাসিবাদের বহু ব্যবহারিক রূপ—যেমন দলীয় সংগঠন, শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো ও শৃঙ্খলার ধারণা—কে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব কেবল তখনই, যখন সেগুলোকে জীবনের প্রতি এর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিচার করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি একটি আধ্যাত্মিক মনোভাব। ফ্যাসিবাদ পৃথিবীকে কেবল এমন কোন উপরিতলীয় ও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না, যেখানে মানুষ একটি স্বতন্ত্র, স্ব–কেন্দ্রিক, প্রকৃতির বিধি–নির্ধারিত সত্তা হিসেবে প্রতিভাত হয় এবং যা জীবনকে পরিচালিত করে ক্ষণস্থায়ী আত্মকেন্দ্রিক সুখের প্রবৃত্তি দ্বারা। ফ্যাসিবাদ কেবল ব্যক্তি নয়, বরং জাতি ও রাষ্ট্রকে দেখে; এমন এক বাস্তবতাকে চিহ্নিত করে, যেখানে ব্যক্তি ও প্রজন্মসমূহ এক নৈতিক বিধানের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ; যাদের মধ্যে রয়েছে একটি অভিন্ন ঐতিহ্য এবং একটি নির্ধারিত ঐতিহাসিক মিশন।
এই মিশনের লক্ষ্য হচ্ছে এমন এক উচ্চতর জীবন নির্মাণ, যা বদ্ধ আত্ম–কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে এবং কর্তব্যনিষ্ঠার ভিত্তিতে গঠন করে এমন এক জীবন যা কাল ও স্থানের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। এই জীবনেই ব্যক্তি আত্মত্যাগ, স্বার্থপরতা থেকে সরে আসা, এমনকি মৃত্যুকে আলিঙ্গনের মাধ্যমে এক নিখাদ আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়, যেখানে তার ‘মানবিক‘ মূল্য নিহিত থাকে।
অতএব, এই ধারণাটি মূলত একটি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রকাশ, যা উনবিংশ শতাব্দীর বস্তুবাদী দৃষ্টিবাদের বিরুদ্ধে বিশ শতকের সাধারণ বৌদ্ধিক প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। দৃষ্টিবাদবিরোধী হলেও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন; এটি সংশয়বাদী নয়, নাস্তিক্যবাদীও নয়; আবার তা নি:সঙ্গ নৈরাশ্যবাদী কিংবা নির্বিকার আশাবাদীও নয়—যেমনটি সাধারণত দেখা যায় সেই সকল মতবাদে, যেগুলো জীবনের কেন্দ্রবিন্দুকে মানুষের বাইরে কোথাও স্থাপন করে, ফলে তার চরিত্র হয়ে পড়ে মূলত নেতিবাচক।
ফ্যাসিবাদ বরং বিশ্বাস করে যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ নিজেই তার বিশ্ব গঠনের সক্ষমতা ও কর্তব্য ধারণ করে। অর্থাৎ, জীবনের কেন্দ্রবিন্দু মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও নৈতিক সত্তার মধ্যেই নিহিত, বাইরের কোনো বহিরাঙ্গ বাস্তবতায় নয়।
ফ্যাসিবাদ চায় মানুষ হোক সক্রিয় এবং সে যেন তার সমস্ত শক্তি ও সচেতনতাকে কাজে লাগিয়ে কর্মে নিয়োজিত হয়। এটি প্রত্যাশা করে, মানুষ যেন সাহসিকতার সঙ্গে তার পথের প্রতিবন্ধকতাগুলোকে উপলব্ধি করে এবং সেগুলোর মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকে। ফ্যাসিবাদ জীবনকে একটি সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করে—এমন এক যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে একজন মানুষের উচিত নিজেকে প্রকৃত অর্থে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান অর্জনের যোগ্য করে তোলা। আর তা সম্ভব প্রথমত তখনই, যখন সে নিজেকে শারীরিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়, যেন সে হয়ে উঠতে পারে সেই ‘উপকরণ‘—যার মাধ্যমে সে উক্ত মর্যাদা অর্জন করতে পারে।
যে নীতি ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা–ই জাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং বিস্তৃত অর্থে সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রেও। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ফ্যাসিবাদ সকল প্রকার সংস্কৃতিকে (শিল্প, ধর্ম, বিজ্ঞান) উচ্চরূপে মূল্যায়ন করে, এবং শিক্ষার ব্যতিক্রমী গুরুত্বকে স্বীকার করে।
এই দর্শন অনুসারে, শ্রমেরও মৌলিক মূল্য রয়েছে। কারণ এর মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃতিকে আয়ত্ত করে এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মাত্রায় মানবিক জগৎ গড়ে তোলে।
এই ইতিবাচক জীবনচিন্তা মূলত একটি নৈতিক ধারণা। এটি বাস্তবতার সামগ্রিক ক্ষেত্রকেই পরিব্যাপ্ত করে, ঠিক যেমনটি করে সেই সকল মানবিক কার্যকলাপ, যার মাধ্যমে মানুষ বাস্তবতাকে আয়ত্তে আনে। কোনো কার্যই নৈতিক বিচারের আওতার বাইরে নয়; কোনো কর্মপ্রচেষ্টাই এমন নয়, যাতে নৈতিক উদ্দেশ্য একটি অন্তর্নিহিত মূল্য সংযোজনে ব্যর্থ।
ফলে, ফ্যাসিবাদ–অনুসারী যে জীবনচিত্র আঁকে, তা গম্ভীর, সংযমপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিকতায় পরিপুষ্ট; জীবনের সকল প্রকাশ ও কর্মকাণ্ড এমন এক বিশ্ববোধের মধ্যে অবস্থিত, যা নৈতিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং আধ্যাত্মিক দায়িত্ববোধের দ্বারা পরিচালিত।
ফ্যাসিবাদ সেই জীবনধারার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, যা কেবলমাত্র স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ–বিলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।
ফ্যাসিবাদী জীবনচিন্তা একটি ধর্মীয় দর্শন, যেখানে মানুষকে দেখা হয় এমন এক উচ্চতর বিধানের অন্তর্নিহিত সম্পর্কের প্রেক্ষিতে, যা ব্যক্তিসীমার অতীত—একটি বস্তুগত ইচ্ছাশক্তিতে পরিপুষ্ট, যা ব্যক্তি–অস্তিত্বকে অতিক্রম করে এবং তাকে একটি আধ্যাত্মিক সমাজের সচেতন সদস্যরূপে উন্নীত করে।
যাঁরা ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার ধর্মনীতিতে কেবল তাৎক্ষণিক সুযোগসন্ধানী কৌশল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না, তাঁরা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন যে—ফ্যাসিবাদ কেবল একটি শাসনব্যবস্থা নয়, বরং সর্বাগ্রে এটি একটি চিন্তাব্যবস্থা, একটি দার্শনিক বিন্যাস।
ফ্যাসিবাদী ইতিহাসবোধে মানুষ কেবলমাত্র তখনই মানুষ, যখন সে একটি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে—একজন পরিবার সদস্য, সামাজিক গোষ্ঠী, জাতি, ও সমগ্র ইতিহাস–প্রবাহের একটি কার্যকর অংশগ্রহণকারী হিসেবে, যেখানে প্রতিটি জাতি নিজস্ব অবদান রাখে। এই প্রেক্ষাপটে ভাষা, রীতি, সমাজজীবনের বিধিবিধান এবং ঐতিহাসিক দলিলপত্রে নিহিত ঐতিহ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাসের বাইরে মানুষ নিছক এক অস্তিত্বহীনতা।

এই কারণে, ফ্যাসিবাদ সমস্ত ব্যক্তি–স্বাতন্ত্র্যবাদী বিমূর্ততা, যা উনবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিবাদনির্ভর বস্তুবাদ থেকে উদ্ভূত, তার বিরোধিতা করে। একইভাবে, এটি প্রত্যাখ্যান করে ফরাসি বিপ্লব–পরবর্তী জ্যাকোবিন ঘরানার কল্পনাপ্রসূত ইউটোপিয়া ও ছকবদ্ধ সমাজ–নবীকরণ প্রচেষ্টাকে। ফ্যাসিবাদ বিশ্বাস করে না ১৮শ শতাব্দীর অর্থনৈতিক সাহিত্যের সেইসব ভাবনাকে, যেখানে মানুষের ‘পৃথিবীতেই সুখলাভ’–এর সম্ভাবনাকে চিত্রিত করা হয়েছিল। একইসঙ্গে, এটি প্রত্যাখ্যান করে সেই ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাসকেও, যেখানে ধারণা করা হয় যে, ভবিষ্যতের কোনো এক সময়ে মানবজাতি তার যাবতীয় সমস্যা ও সংকটের চূড়ান্ত সমাধানে পৌঁছে যাবে।
এই ভাবনা বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, কারণ অভিজ্ঞতা শিক্ষা দেয়—জীবন একটি অব্যাহত পরিবর্তন ও বিবর্তনের প্রক্রিয়া।
রাজনীতিতে ফ্যাসিবাদ বাস্তববাদে বিশ্বাসী; তার নীতিগত অবস্থান হলো এই যে, কেবল সেই সমস্যাগুলোকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত, যেগুলো ইতিহাস–প্রসূত বাস্তবতার স্বাভাবিক ফসল এবং যেগুলোর সমাধান সেই বাস্তবতার অভ্যন্তরেই নিহিত থাকে কিংবা নিজেই তার সমাধানের ইঙ্গিত প্রদান করে।
মানুষ কেবলমাত্র তখনই প্রকৃত অর্থে মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যখন সে নিজেকে এই বাস্তবতার প্রবাহে সম্পৃক্ত করে এবং এর অন্তর্নিহিত কার্যক্ষম শক্তিগুলোকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়।
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধিতা করে, ফ্যাসিবাদী জীবনদর্শন রাষ্ট্রের গুরুত্বকে সর্বোচ্চ মাত্রায় তুলে ধরে এবং ব্যক্তিকে কেবল তখনই স্বীকৃতি দেয়, যখন তার স্বার্থ রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে একীভূত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কারণ রাষ্ট্রই হলো ইতিহাসবদ্ধ মানবসত্তার নৈতিক চেতনা ও সর্বজনীন ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ।
ফ্যাসিবাদ সেই ধ্রুপদী উদারতান্ত্রিকতার বিরোধিতা করে, যা এক সময় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল এবং যার ঐতিহাসিক ভূমিকা শেষ হয়ে গিয়েছিল তখনই, যখন রাষ্ট্র জনগণের চেতনা ও ইচ্ছাশক্তির প্রতিফলনরূপে প্রতিষ্ঠা পায়।
উদারতন্ত্র ব্যক্তি–অধিকারকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রকে অস্বীকৃতি জানায়; পক্ষান্তরে, ফ্যাসিবাদ সেই রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আদর্শকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।
রাষ্ট্রের অধিকারকে ফ্যাসিবাদ এমন এক স্বরূপে বিবেচনা করে, যা ব্যক্তিসত্তার প্রকৃত সারবস্তুকে প্রকাশ করে। আর যদি স্বাধীনতা বাস্তব জীবনে মানুষের একটি গুণ হয়ে থাকে— যা কেবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উদারতন্ত্র কর্তৃক কল্পিত বিমূর্ত মানবপ্রতিমাদের জন্য সংরক্ষিত নয় —তবে ফ্যাসিবাদ স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নেয়; এবং এমন একমাত্র স্বাধীনতার পক্ষেই যা প্রকৃত অর্থে মূল্যবান: তা হলো রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ব্যক্তির স্বাধীনতা।
ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রধারণা একটি সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গি, যার বাইরে কোনো মানবিক কিংবা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, থাকলেও তা অর্থহীন। এই অর্থে, ফ্যাসিবাদ একটি সর্বাত্মকতাবাদী মতবাদ, এবং ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র একটি একীভূত ও সর্বসমন্বিত সংগঠন—যা সমস্ত মূল্যবোধকে ধারণ করে, ব্যাখ্যা করে, বিকশিত করে এবং জনগণের সামগ্রিক জীবনকে শক্তি ও দিশা প্রদান করে।
রাষ্ট্রের বাইরে কোনো ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর (রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক সংগঠন, অর্থনৈতিক ইউনিয়ন, সমাজবর্গ) অস্তিত্ব নেই। ফ্যাসিবাদ সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে, কারণ সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ধারণা অজ্ঞাত এবং যা ইতিহাসকে কেবলমাত্র শ্রেণিসংগ্রামের প্রেক্ষাপটে দেখে।
রাষ্ট্রীয় ঐক্য মানে যেখানে বিভিন্ন শ্রেণি একক অর্থনৈতিক ও নৈতিক বাস্তবতায় মিলিত হয়। একইভাবে, ফ্যাসিবাদ ট্রেড ইউনিয়নবাদকেও শ্রেণি–অস্ত্র হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে।
তবে যখন এই সংগঠনসমূহ রাষ্ট্রীয় পরিসরের আওতায় আসে, তখন ফ্যাসিবাদ স্বীকার করে যে সমাজতন্ত্র ও ট্রেড ইউনিয়নবাদের উত্থানের পেছনে বাস্তব প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনগুলোর যথোচিত মূল্যায়ন করা হয় রাষ্ট্রের কর্পোরেত–কাঠামোর মধ্য দিয়ে, যেখানে বিভিন্ন স্বার্থসমূহকে সমন্বিত ও সঙ্গতিপূর্ণ করা হয় রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ভিত্তিতে।
নানাবিধ স্বার্থ অনুযায়ী গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে ব্যক্তি শ্রেণি গঠন করে; তারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অনুযায়ী সংগঠিত হলে ট্রেড–ইউনিয়ন তৈরি করে; কিন্তু সর্বাগ্রে তারা রাষ্ট্র গঠন করে—রাষ্ট্র কোনো সংখ্যাগত বাস্তবতার সমষ্টি নয়, কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তির যোগফল নয়। এই কারণে ফ্যাসিবাদ সেই ধরনের গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে, যা একটি জাতিকে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে সমতুল করে দেখে এবং একে বৃহত্তম সংখ্যার অধীনস্ত করে তোলে।
বরং, যদি জাতিকে বিবেচনা করা হয় তার গুণগত দিক থেকে—পরিমাণগত নয়—তাহলে ফ্যাসিবাদই হয় ‘শুদ্ধতম গণতন্ত্র’; একটি ভাবধারা হিসেবে জাতি সবচেয়ে নৈতিক, সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সর্বাধিক সত্যরূপে পরিগণিত হয়, যা ব্যক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়—কখনো স্বল্পসংখ্যক, কখনো এমনকি এককের বিবেক ও ইচ্ছারূপে—এবং শেষে তা রূপ নেয় জনসাধারণের, একটি জাতির সমগ্র ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক গঠনে গঠিত জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত বিবেক ও ইচ্ছারূপে; যারা একক আত্মসচেতনতা ও অভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে আত্মিক বিকাশ ও গঠনের পথে এগিয়ে চলে।
জাতি এখানে কোনো বর্ণগোষ্ঠী নয়, নয় কোনো ভৌগোলিক সীমানা দ্বারা নির্ধারিত অঞ্চল; বরং এটি হলো একটি জনগোষ্ঠী, যারা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখে—একটি ভাবনাতাড়িত ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণ, যাদের মাঝে জীবনের ইচ্ছা, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, আত্মসচেতনতা ও ব্যক্তিত্বের উদ্ভব ঘটে।
যতদূর পর্যন্ত এই উচ্চতর ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্ররূপে রূপায়িত হয়, ততদূর পর্যন্তই তা একটি জাতিতে পরিণত হয়। জাতিই রাষ্ট্র সৃষ্টি করে—এই ধারণা একটি পুরাতন, প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, যা উনবিংশ শতকে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচারণার আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বরং, ফ্যাসিবাদী মতানুসারে, রাষ্ট্রই জাতিকে সৃষ্টি করে; রাষ্ট্র জনগণের মধ্যে নৈতিক ঐক্য সম্পর্কে চেতনা জাগিয়ে তোলে, তাদের ইচ্ছাশক্তি দান করে, এবং সেইসঙ্গে প্রকৃত জীবনের সূচনা ঘটায়।
জাতীয় স্বাধীনতার অধিকার কেবলমাত্র কোনো সাহিত্যিক কিংবা ভাববাদী আত্মসচেতনতা থেকে উদ্ভূত হয় না; বরং এর উৎস কোনো নিস্পৃহ ও অচেতন বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যেও নিহিত নয়। বরং, এই অধিকার গড়ে ওঠে একটি সক্রিয়, আত্মসচেতন, রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি থেকে—যা কার্যকর কর্মকাণ্ডে নিজেকে প্রকাশ করে এবং সেই অধিকারকে প্রমাণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। সংক্ষেপে, এই অধিকার উদ্ভব হয় একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থেকে, অন্ততপক্ষে সম্ভাব্য অবস্থান হিসেবে হলেও। বস্তুত, রাষ্ট্রই হচ্ছে সেই সর্বজনীন নৈতিক ইচ্ছার অভিব্যক্তি, যা জাতীয় স্বাধীনতার অধিকার সৃষ্টি করে।
রাষ্ট্রে উদ্ভাসিত একটি জাতি কেবলমাত্র ততক্ষণই জীবন্ত ও নৈতিক সত্তা, যতক্ষণ পর্যন্ত তা প্রগতিশীল থাকে।
নিষ্ক্রিয়তা মানেই মৃত্যু। অতএব, রাষ্ট্র কেবল কর্তৃত্ব নয়—যা শুধু শাসন করে আর ব্যক্তির ইচ্ছাসমূহের উপর আইনি রূপ ও আত্মিক মূল্য আরোপন করে, বরং রাষ্ট্র এক ধরনের ক্ষমতা যা সীমাহীনভাবে ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তিকে অনুভব করায় এবং মান্য করতে শেখায়। এইভাবে রাষ্ট্র তার বিকাশের জন্য অপরিহার্য সিদ্ধান্তগুলোর সার্বজনীনতা কার্যত প্রমাণ করে। এই প্রক্রিয়া স্বয়ং সংগঠন ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে—তা সম্ভাব্য হোক বা বাস্তব। এইভাবেই রাষ্ট্র মানব–ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে নিজেকে সমতুল্য করে তোলে, যার বিকাশ বাধাগ্রস্ত করা যায় না এবং যা আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে তার অসীমতাকে প্রমাণ করে।
ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র হল ব্যক্তিত্বের এক উচ্চতর ও অধিক শক্তিশালী প্রকাশ, তবে তা কেবল বাহ্যিক শক্তি নয়—বরং একটি আত্মিক শক্তি। এটি মানবের নৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবনের সকল রূপ ও প্রকাশের সমাহার।
এই কারণে, রাষ্ট্রের কার্যপরিধিকে কেবল আইন–শৃঙ্খলা রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না—যেমনটি উদারনৈতিক মতবাদে প্রত্যাশিত। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়, যা কেবল নাগরিকের তথাকথিত অধিকার চর্চার একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দেয়।
বরং ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র একটি অন্তর্নিহিতভাবে গৃহীত নৈতিক মানদণ্ড ও আচরণবিধি—একটি শৃঙ্খলা, যা ব্যক্তিমানুষের সমগ্র সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে; এটি যেমন ইচ্ছাশক্তিকে প্রভাবিত করে, তেমনই বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রকেও অনুপ্রাণিত করে।
এটি একধরনের কেন্দ্রীয় নৈতিক নীতি, যা সভ্য সমাজের নাগরিক হিসেবে মানুষের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান করে নেয়; এটি তার আত্মপরিচয়ের গভীরে প্রোথিত থাকে। এই নীতি কর্মনিষ্ঠ মানুষ ও চিন্তক, শিল্পী ও বিজ্ঞানী—সকলের হৃদয়জুড়ে বাস করে; এটি আত্মারও আত্মা।
সংক্ষেপে, ফ্যাসিবাদ কেবল আইনপ্রণেতা বা প্রতিষ্ঠান–প্রতিষ্ঠাতা নয়, বরং তা একাধারে একজন শিক্ষাগুরু এবং আত্মিক জীবনের উন্নয়নকারী। এর লক্ষ্য কেবল জীবনযাপনের বাহ্যিক রূপকে নয়, বরং তার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুকেও পুনর্গঠন করা—অর্থাৎ মানুষ, তার চারিত্রিক গঠন এবং তার বিশ্বাসকে পুনরায় নির্মাণ করা।
এই লক্ষ্য পূরণের জন্য, ফ্যাসিবাদ শৃঙ্খলা আরোপ করে এবং কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে, মানুষের আত্মার গভীরে প্রবেশ করে এবং সেখানে অবিসংবাদিত রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে।
এই আদর্শের প্রতীকস্বরূপ, ফ্যাসিবাদ “লিক্টর’স রডস”–কে তার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছে—যা ঐক্য, শক্তি এবং ন্যায়বিচারের প্রতীক।
রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ
১৯১৯ সালের মার্চ মাসে—যা আজ অনেক দূরবর্তী অতীত— মিলানে আমি Popolo d’Italia পত্রিকার পাতায় সেই বিপ্লবী হস্তক্ষেপবাদীদের যখন আহ্বান জানিয়েছিলাম— যারা ১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত ফ্যাসিবাদের কার্যক্রমের সূচনালগ্ন থেকেই আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছেন— তখন আমার মনে কোনো সুস্পষ্ট মতবাদগত কর্মসূচি ছিল না।
আমি একমাত্র যে মতবাদকে ব্যবহারিক অর্থে চিনতাম, তা ছিল সমাজতন্ত্র—যার সঙ্গে আমি ১৯১৪ সালের শীতকাল পর্যন্ত, প্রায় এক দশকব্যাপী, ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। আমার অভিজ্ঞতা ছিল একজন অনুসারী এবং পরবর্তীকালে একজন নেতা হিসেবে, কিন্তু তা মতবাদগত নয়—বরং ছিল কর্মনির্ভর অভিজ্ঞতা। সেই সময়ে আমার মতবাদ ছিল কর্মতৎপরতার মতবাদ।
১৯০৫ সালের পর থেকে সমাজতন্ত্রের কোনো একক, সর্বজনগ্রাহ্য মতবাদ বিদ্যমান ছিল না। যখন বার্নস্টাইনের নেতৃত্বে জার্মানিতে সংশোধনবাদী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে, এর পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত হয় এক বামপন্থী বিপ্লবী প্রবণতা, যা ইতালিতে কেবল প্রবচনের পরিসরে সীমাবদ্ধ থেকেছে, অথচ রাশিয়ান সমাজতন্ত্রের প্রেক্ষিতে সেটিই হয়ে উঠেছিল বলশেভিকবাদের পূর্বভূমিকা।
সংস্কারবাদ, বিপ্লববাদ, মধ্যপন্থা—এই পরিভাষাগুলোর প্রতিধ্বনিও আজ মৃতপ্রায়। অথচ ফ্যাসিবাদের বিশাল প্রবাহে এমন কিছু স্রোত খুঁজে পাওয়া যায়, যেগুলোর উৎস ছিল সোরেল, পেগি, লাগারদেলের মত গণসংগ্রামপন্থী সমাজবাদীদের চিন্তায়, এবং ১৯০৪ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে নতুন স্বরের প্রবর্তক ইতালীয় সিন্ডিক্যালিস্টদের কর্মধারায়।
এই নতুন স্বরটি সেই সময়ের ইতালীয় সমাজতন্ত্রকে দুর্বল ও অচেতন করে দেওয়া জিওলিত্তির দলের সঙ্গে অশুভ মেলবন্ধনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে উঠে এসেছিল। এই স্বরের প্রতিধ্বনি শোনা যায় অলিভেত্তির
Pagini Libere, ওরানোর Lupa, এবং এনরিকো লেওনের Divenirs Socials– এ।
১৯১৯ সালে যুদ্ধ–সমাপ্তির পর মতবাদ হিসেবে সমাজতন্ত্র মৃত হয়ে পড়ে। টিকে ছিল কেবল একটি প্রতিহিংসার অনুভূতি হিসেবে—বিশেষত ইতালিতে, যেখানে সমাজতন্ত্রের একমাত্র কৌশল ছিল যুদ্ধ–চাওয়া মানুষদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগানো এবং তাদের সেই যুদ্ধের দায়ভার বহনের জন্য বাধ্য করা।
The Popolo d’Italia পত্রিকাটি তার উপশিরোনামে নিজেকে ঘোষণা করেছিল “যোদ্ধা ও উৎপাদকদের দৈনিক মুখপত্র” হিসেবে। এখানে “উৎপাদক” শব্দটি তখনকার এক বিশেষ মানসিক প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ। ফ্যাসিবাদ কোনো পূর্বনির্ধারিত মতবাদ থেকে গড়ে ওঠেনি, টেবিলে বসে রচিত তাত্ত্বিক পরিকল্পনার ফল নয়; তা ছিল বাস্তব প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত এক কর্মচাঞ্চল্য—নিজেই ছিল কর্ম ও আন্দোলন। প্রাথমিক দুই বছর এটি কোনো দল ছিল না, বরং ছিল “দলবিরোধী” ও একটি আন্দোলন। আমি যে নাম দিয়েছিলাম আমাদের সংগঠনকে, তা–ই এর স্বরূপ নির্ধারণ করে দিয়েছিল।
তবে, কেউ যদি ইচ্ছা করে সেদিনকার সেই ভাঁজপড়া কাগজগুলো আবার পড়ে দেখে—যেখানে Italian Fasci di combattimento গঠনের বৈঠকের বিবরণ রয়েছে—তাহলে তিনি তাতে কোনো পূর্ণাঙ্গ মতবাদ খুঁজে পাবেন না। বরং তিনি দেখবেন একগুচ্ছ নির্দেশনা, পূর্বাভাস, ইঙ্গিত, যেগুলো সময়ের সাথে সাথে, তাৎক্ষণিক বাস্তবতার আবরণ সরিয়ে, কয়েক বছরের মধ্যেই পরিণত হয়েছিল পরিপূর্ণ মতবাদে—এমন এক রাজনৈতিক মতবাদ যা ফ্যাসিবাদকে অতীত ও সমসাময়িক অন্যান্য সব মতবাদ থেকে স্বতন্ত্র অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করেছিল।
যদি বুর্জোয়ারা—আমি তখন বলেছিলাম—ভাবেন যে তারা আমাদেরকে বজ্রনিরোধকের মতো ব্যবহার করতে পারবে, তবে তারা ভুল করছে। আমাদের জনগণের দিকে এগোতে হবে… আমরা চাই শ্রমিক শ্রেণি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে অভ্যস্ত হোক, যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালানো মোটেও সহজ কাজ নয়… আমরা লড়ব প্রযুক্তিগত ও নৈতিক পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধে… এখন যেহেতু শাসনব্যবস্থার উত্তরাধিকারের পথ উন্মুক্ত, আমাদের সাহস হারালে চলবে না। আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে; যদি বিদ্যমান শাসনব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করতে হয়, তবে সেই স্থান আমাদের নিতে হবে। উত্তরাধিকার লাভের অধিকার আমাদেরই, কারণ আমরাই জাতিকে যুদ্ধে প্রবেশ করতে বলেছিলাম এবং আমরাই তাকে বিজয়ের পথে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম… প্রচলিত রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের কাঠামো আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারে না; আমরা চাই বিভিন্ন স্বার্থের সরাসরি প্রতিনিধিত্ব… কেউ কেউ আপত্তি করতে পারেন যে এই কর্মসূচি গিল্ড ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ারই নামান্তর। তাতে কী! আমি চাই এই সমাবেশ জাতীয় সিন্ডিক্যালবাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অর্থনৈতিক দাবিসমূহকে গ্রহণ করুক…”
এটা কি আশ্চর্যজনক নয় যে ঠিক প্রথম দিন থেকেই, Piazza San Sepolcro তে, “গিল্ড” শব্দটি উচ্চারিত হয়েছিল—একটি শব্দ যা, ফ্যাসিস্ট বিপ্লব বিকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে, শাসনব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক আইনগত ও সামাজিক সৃষ্টিকে প্রকাশ করতে শুরু করে?
রোম অভিযানের পূর্ববর্তী কয়েক বছর এমন একটি সময়পর্বকে চিহ্নিত করে, যখন কর্মের প্রয়োজনে বিলম্ব ও সুচিন্তিত মতবাদ রচনার সুযোগ ছিল না। শহর ও গ্রামে চলছিল সংঘর্ষ। আলোচনা হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু এর থেকেও পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল—মৃত্যু। ফ্যাসিস্টরা জানতো কীভাবে মরতে হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ—যা অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত, টীকাসহ উপস্থাপিত—অনুপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু তার পরিবর্তে উপস্থিত ছিল আরও দৃঢ় কিছু—একটি বিশ্বাস।
তবুও, যদি কেউ বইপত্র, প্রবন্ধ, কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব, প্রধান ও গৌণ বক্তৃতার সাহায্যে সেই দিনগুলোর স্মৃতি পুনর্জীবিত করতে চায়, তবে সে দেখবে—যদি তার অনুসন্ধান ও নির্বাচনের যথাযথ দক্ষতা থাকে—যে যুদ্ধের মাঝখানেই মতবাদের ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছিল। বাস্তবেই, ওই সময়েই ফ্যাসিবাদী চিন্তাধারা অস্ত্রধারণ করেছিল, নিজেকে পরিশীলিত করেছিল, এবং সংগঠনের দিকে অগ্রসর হয়েছিল।
ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সমস্যা, কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার সমস্যা কিম্বা রাজনৈতিক, সামাজিক, বিশেষত জাতীয় প্রশ্নগুলো তৎকালীন সময়ে আলোচিত হচ্ছিল। একইসঙ্গে, দণ্ডমূলক অভিয়ানের সময় উদারবাদী, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, মাসনিক মতবাদ এবং Partito Popolare এর সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছিল। তথাপি, একটি প্রাতিষ্ঠানিক মতবাদের অভাবকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে কুপ্রবণ বিরোধীরা ফ্যাসিবাদকে মতবাদ গঠনে অক্ষম প্রমাণ করতে চেয়েছিল—ঠিক সেই সময়ে, যখন এই মতবাদই প্রবল উত্থানের সঙ্গে রচিত হচ্ছিল। শুরুতে, প্রতিটি নতুন মতবাদের মতোই, তা প্রকাশ পায় প্রচণ্ড নেতিবাচক ও মতবাদবিরোধী রূপে; পরে, গঠনমূলক তত্ত্বের মাধ্যমে একটি ইতিবাচক আকার গ্রহণ করে, যা পরবর্তীতে ১৯২৬, ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সালে ফ্যাসিস্ট শাসনের আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সংযুক্ত হয়।
ফ্যাসিবাদ এখন কেবল একটি শাসনব্যবস্থা হিসেবে নয়, একটি মতবাদ হিসেবেও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত। এর অর্থ হচ্ছে, ফ্যাসিবাদ—নিজস্ব সমালোচনাশক্তিকে আত্মপর্যালোচনা ও অপরের বিশ্লেষণে প্রয়োগ করে—নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র বিশ্বের সকল জাতির জন্য দুশ্চিন্তার উৎস হয়ে ওঠা বস্তুগত ও বৌদ্ধিক স্বার্থ–সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ অধ্যয়ন করেছে এবং নিজস্ব মানদণ্ডে বিচার করেছে, এবং এখন এসব সমস্যার মোকাবিলায় নিজস্ব নীতির দ্বারা পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত।
প্রথমেই, মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিকাশ–সংক্রান্ত বিষয়ে এবং বর্তমান সকল রাজনৈতিক বিবেচনার বাইরে ফ্যাসিবাদ মূলত অনন্ত শান্তির সম্ভাবনা বা কার্যকারিতায় বিশ্বাস করে না। সে কারণে ফ্যাসিবাদ আত্মোৎসর্গের বিপরীতে ভীরু ও আত্মসমর্পণমূলক নির্জীবতা ঢেকে রাখার মাধ্যম হিসেবে শান্তিবাদকে পরিত্যাগ করে। শুধু যুদ্ধই মানবিক শক্তিকে তার চূড়ান্ত উৎকটতায় পৌঁছে দিতে পারে এবং কেবল যুদ্ধই তাদের উপর মহত্ত্বের টীকা এঁকে দেয়, যারা সাহসের সঙ্গে এর মুখোমুখি হতে সক্ষম। অন্য সব পরীক্ষা অমূলক যা কখনোই একজন মানুষকে জীবন অথবা মৃত্যুর বিকল্পের মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারে না। এই কারণে, যে সকল মতবাদ বলে ‘শান্তি যেকোনো মূল্যে’—তা ফ্যাসিবাদের সঙ্গে অসঙ্গত।
একইভাবে ফ্যাসিবাদের চেতনার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ—যদিও কখনো বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপযোগী মনে হতে পারে—সেই সব আন্তর্জাতিকতাবাদী বা ‘লীগ–ভিত্তিক’ কাঠামো, যেগুলো ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে, জনগণের হৃদয় আবেগ, আদর্শবাদ বা বাস্তব বিবেচনায় গভীরভাবে আলোড়িত হলেই ভেঙে পড়ে।
ফ্যাসিবাদ ব্যক্তি–জীবনেও এই যুদ্ধবাদী মানসিকতাকে বহন করে। “আমার কিছু যায় আসে না“—যেটি ছিল ফ্যাসিবাদী স্কোয়াড সদস্যদের অহংকারী মন্ত্র এবং আহত সৈনিকের ব্যান্ডেজে লিখিত—এটি কেবল দার্শনিক স্তোইকবাদের প্রকাশ নয়; বরং এটি একটি জীবনদর্শনের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা কেবল রাজনৈতিক নয়, বরং একটি সংগ্রামী আত্মাকে প্রতিফলিত করে—যে আত্মা সকল ঝুঁকিকে গ্রহণ করে। এটি হলো ইতালীয় জীবনের এক নতুন রীতির প্রতীক।
ফ্যাসিবাদী ব্যক্তি জীবনকে গ্রহণ করে এবং ভালোবাসে; আত্মহত্যাকে সে ভীরুতার নিদর্শন হিসেবে প্রত্যাখ্যান ও ঘৃণা করে। তার কাছে জীবন মানে দায়িত্ব, উৎকর্ষ, বিজয়; জীবন হতে হবে মহান এবং পরিপূর্ণ—এটি হবে নিজের জন্য, তবে সর্বাগ্রে হবে অপরের জন্য—নিকটবর্তী ও দূরবর্তী, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য।
এই সমস্ত পূর্বধারণার ফলস্বরূপই ফ্যাসিবাদী শাসনের জনসমাজ নীতি গঠিত হয়েছে। ফ্যাসিবাদী ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে ভালোবাসে, তবে ‘প্রতিবেশী‘ শব্দটি কোনো অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য ধারণাকে নির্দেশ করে না। প্রতিবেশীকে ভালোবাসা মানেই এমন কোনো ভালোবাসা নয়, যা প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক কঠোরতাকে বাদ দেয়; আর এর মানে এই নয় যে, তা শৃঙ্খলা ও মর্যাদাগত পার্থক্য অগ্রাহ্য করে । ফ্যাসিবাদ ‘সর্বজনীন আলিঙ্গন’ জাতীয় কোনো মানবতাবাদী বিভ্রমকে গ্রহণ করে না।
জাতিসমূহের একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে ফ্যাসিবাদ অন্য জাতিকে চোখে চোখ রেখে সম্মুখীন হয়; সে সদা সতর্ক ও প্রহরায় নিয়োজিত; অন্যদের সমস্ত কর্মকাণ্ড গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের স্বার্থের যেকোনো পরিবর্তন লক্ষ্য রাখে; এবং সে কখনোই পরিবর্তনশীল ও প্রতারক বহিঃরূপের দ্বারা বিভ্রান্ত হয় না।
জীবন সম্পর্কে এই ধারণার জন্যই ফ্যাসিবাদ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ যে মতবাদ, অর্থাৎ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ—তাকে দৃঢ় ও সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মানবজাতির ইতিহাসকে কেবলমাত্র শ্রেণিসংঘর্ষ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদন–উপকরণের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করে, এবং অন্যান্য সকল সাংস্কৃতিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উপাদানকে উপেক্ষা করে। ফ্যাসিবাদ এই একমাত্রিক ও অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করে একটি বহুমাত্রিক, নৈতিক–আধ্যাত্মিকভাবে সংগঠিত জীবনের ধারণা প্রতিষ্ঠা করে।
অর্থনৈতিক জীবনের নানা উত্থান–পতন—যেমন কাঁচামাল আবিষ্কার, নতুন কারিগরি পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন—এসব যে গুরুত্বপূর্ণ, তা কেউ অস্বীকার করে না; কিন্তু এসব উপাদান এককভাবে মানব ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতে পারে—এই ধারণা নিছক অযৌক্তিক। ফ্যাসিবাদ বিশ্বাস করে—এখনও এবং সর্বদা—পবিত্রতা ও বীরত্বে; অর্থাৎ এমন সব কর্মে, যেখানে কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অর্থনৈতিক প্রেরণা কাজ করে না।
ফ্যাসিবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ এই মতবাদ মানুষকে কেবলমাত্র ইতিহাসের উপরিতলের পাপেটরূপে বিবেচনা করে, যা ঢেউয়ের তোড়ে কখনো দেখা যায় ও আবার মিলিয়ে যায়। অথচ গভীরে গেলে নির্ধারক শক্তি হিসেবে মানুষই গতিময় ও ক্রীয়াশীল থাকে।
ফলে, ফ্যাসিবাদ শ্রেণিসংঘর্ষের সেই অপরিবর্তনীয় ও অনিবার্য চরিত্রকেও অস্বীকার করে, যা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি বলে বিবেচিত। এইভাবে ফ্যাসিবাদ সমাজতন্ত্রের দুটো প্রধান মতাদর্শিক ভিত্তিতে আঘাত হানে।
অবশিষ্ট থাকে কেবল মানবসভ্যতার প্রাচীনতম একটি আবেগ—সমাজে এমন এক সম্পর্ক গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা, যেখানে নীচু শ্রেণির দুঃখ–দুর্দশা লাঘব পাবে। কিন্তু এখানেও ফ্যাসিবাদ সমাজতান্ত্রিক পন্থায় গঠিত অর্থনৈতিক বিবেচনাধর্মী সুখের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে—যা মনে করে, ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছালে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বজনের সর্বোচ্চ ভোগ–সুবিধা নিশ্চিত হবে।
ফ্যাসিবাদ এই বস্তুবাদী সুখ–ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনীতিবিদদের উপর ছেড়ে দেয়। এর অর্থ, ফ্যাসিবাদ ‘সমৃদ্ধি = সুখ‘ এই সমীকরণকে অস্বীকার করে—যা মানুষকে কেবলমাত্র ভক্ষণে তৃপ্ত জন্তু হিসেবে চিহ্নিত করে এবং জীবনকে নিছক এক প্রকার উদ্ভিদসুলভ অস্তিত্বে রূপান্তরিত করে।
সমাজতন্ত্রের সমালোচনার পর, ফ্যাসিবাদ তার আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে নেয় গণতান্ত্রিক মতবাদসমূহের পুরো কাঠামোকে এবং তাদের মৌলিক ভিত্তি ও কার্যকর প্রয়োগ—উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করে। ফ্যাসিবাদ অস্বীকার করে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বয়ং সমাজে নির্ধারক শক্তি হতে পারে; এটি প্রত্যাখ্যান করে সংখ্যার ভিত্তিতে শাসনের অধিকার, যা সাধারণত পর্যায়ক্রমিক নির্বাচনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।
ফ্যাসিবাদ ঘোষণা করে, মানুষের মধ্যে এক অপরিবর্তনীয়, সৃজনক্ষম এবং কল্যাণকর বৈষম্য বিদ্যমান, যেটিকে “সার্বজনীন ভোটাধিকার” নামক যান্ত্রিক ও বাহ্যিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমতায় পরিণত করা সম্ভব নয়।
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে বলা যেতে পারে এমন এক পদ্ধতি, যেখানে জনগণকে নিয়মিতভাবে এই বিশ্বাসে ভুলিয়ে রাখা হয় যে, তারা সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করছে; অথচ প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্ব অন্য শক্তির—প্রায়শই অদৃশ্য, জবাবদিহিহীন ও গোপন শক্তির—হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।
গণতন্ত্র হলো এমন এক রাজাহীন শাসনব্যবস্থা, যেখানে একাধিক রাজা সক্রিয়, যারা অনেক সময় একক স্বৈরশাসকের চেয়েও বেশি একচেটিয়া, স্বেচ্ছাচারী এবং বিধ্বংসী।
এই কারণেই ফ্যাসিবাদ—যদিও ১৯২২ সালের আগে তা প্রাসঙ্গিক কারণে প্রজাতন্ত্রপন্থী ছিল—‘রোম অভিযাত্রার আগেই সেই অবস্থান পরিত্যাগ করে। কারণ, ফ্যাসিবাদ তখন বুঝতে শুরু করে যে শাসনব্যবস্থার গঠনমূলক রূপ (রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র) আর মুখ্য বিষয় নয়।
এর কারণ, ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে স্পষ্ট হয় যে, অতীত ও বর্তমানের রাজতন্ত্র কিংবা প্রজাতন্ত্র—কোনোটিই “শাশ্বততার দৃষ্টিকোণ” থেকে বিচারযোগ্য নয়। বরং প্রতিটি শাসনব্যবস্থা কোনো একটি নির্দিষ্ট জাতির রাজনৈতিক বিবর্তন, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং মনস্তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশমাত্র।
ফ্যাসিবাদ রাজতন্ত্র বনাম প্রজাতন্ত্র—এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করেছে, যা নিয়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাগুলি দীর্ঘকাল ধরে কালক্ষেপন করেছে। তারা প্রতিটি ব্যর্থতার জন্য রাজতন্ত্রকে দায়ী করেছে এবং প্রজাতন্ত্রকে নিখুঁত শাসনব্যবস্থা হিসেবে প্রচার করেছে।
কিন্তু অভিজ্ঞতা শিক্ষা দেয় যে, কিছু প্রজাতন্ত্র নিজস্ব কাঠামোতেই প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বৈরাচারী, আবার কিছু রাজতন্ত্র সবচেয়ে সাহসী রাজনৈতিক ও সামাজিক পরীক্ষা–নিরীক্ষাকেও গ্রহণ করেছে।
রেনান, যিনি ফ্যাসিবাদের পূর্বাভাসপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছিলেন, তাঁর একটি দার্শনিক ধ্যান–চিন্তায় মন্তব্য করেন:
“যুক্তি ও বিজ্ঞান মানবজাতির সৃষ্টি, তবে সরাসরি জনতার মাধ্যমে কিংবা জনতার জন্য যুক্তির সন্ধান করা কল্পনাবিলাস মাত্র। যুক্তির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সকলের তা জানা অপরিহার্য নয়; আর যদি জানানো আবশ্যকই হয়, তবুও তা গণতন্ত্রের মাধ্যমে সম্ভব নয় — কারণ গণতন্ত্র যেন নির্ধারিত হয়েছে সমস্ত পরিশ্রমসাধ্য সংস্কৃতি ও উচ্চতর জ্ঞানের রূপ বিলুপ্তির পথে নিয়ে যেতে।
সমাজ কেবল ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্যই বিদ্যমান— এমন নীতিবাক্য প্রকৃতির পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়; কারণ প্রকৃতি কেবল প্রজাতির বিষয়ে চিন্তা করে এবং ব্যক্তিকে ত্যাগ করতেও প্রস্তুত।
তবে আশঙ্কাজনকভাবে গণতন্ত্রের চূড়ান্ত অর্থ দাঁড়ায় (যদিও আমি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করছি যে এর ভিন্ন ব্যাখ্যাও সম্ভব) এমন এক সমাজব্যবস্থা, যেখানে অবক্ষয়গ্রস্ত এক জনসমষ্টি চিন্তা বলতে আর কিচ্ছু অবশিষ্ট নেই কেবল জড় প্রবৃত্তিনির্ভর অশ্লীল ভোগ–বিলাস ছাড়া।’’
.
গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে ফ্যাসিবাদ প্রত্যাখ্যান করে রাজনৈতিক সমতার সেই অযৌক্তিক প্রচলিত মিথ্যাকে, যা প্রকৃতপক্ষে একটি সামষ্টিক দায়হীনতার অভ্যাস এবং সুখ–সমৃদ্ধি ও অনন্ত অগ্রগতির এক বিভ্রমময় কাহিনি।
কিন্তু যদি গণতন্ত্র বলতে এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝানো হয়, যেখানে জনগণকে রাষ্ট্রে প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয় না, তাহলে এই রচনার প্রণেতা ইতিমধ্যেই ফ্যাসিবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন একটি “সংগঠিত, কেন্দ্রীভূত, কর্তৃত্ববাদী গণতন্ত্র” হিসেবে।
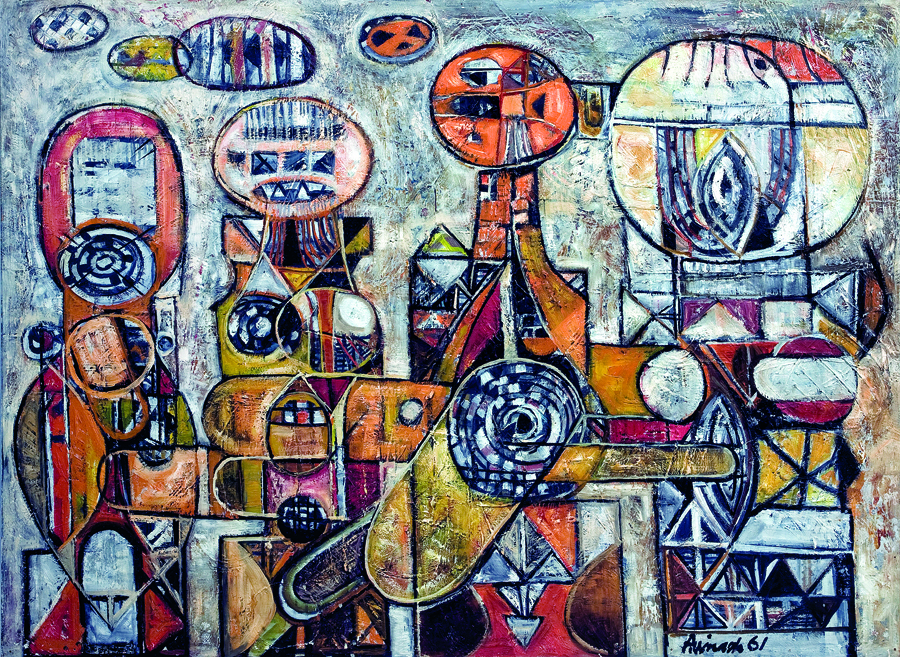
শিল্পী: অভিনাশ চন্দ্র
সূত্র: ফ্রিজি
ফ্যাসিবাদ নিঃসন্দেহে ও সম্পূর্ণভাবে উদারতন্ত্রের মতবাদগুলোর বিরোধী— রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে। উনবিংশ শতাব্দীতে উদারতন্ত্রের গুরুত্বকে যেমন সমকালীন বিতর্কের খাতিরে অতিরঞ্জিত করা উচিত নয়; তেমনি, সেই শতকে বিকাশ লাভকারী বহু মতবাদের মধ্যে একটিকে চিরকালের জন্য মানবজাতির ধর্মে পরিণত করাও সমীচীন নয়।
বাস্তবে, উদারতন্ত্র প্রকৃত অর্থে মাত্র পনেরো বছরের জন্য বিকশিত হয়েছিল। এটি জন্ম নিয়েছিল ১৮৩০ সালে, Holy Alliance এর প্রতিক্রিয়ায়, যারা ইউরোপকে ১৭৮৯ সালের চেয়েও পেছনের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিল। আর শিখর স্পর্শ করেছিল ১৮৪৮ সালে, এমনকি সেই সময়ে পোপ নবম পিয়াসও ছিলেন একজন উদারবাদী। কিন্তু সেই বছর থেকেই এর পতন শুরু হয়। যদি ১৮৪৮ হয় আলো ও কাব্যের বছর, তবে ১৮৪৯ ছিল অন্ধকার ও বেদনার বছর। রোমান প্রজাতন্ত্র ধ্বংস হয়েছিল আরেকটি প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্সের হাতে। সেই একই বছরে কার্ল মার্কস তাঁর বিখ্যাত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে সমাজতন্ত্রের বাণী প্রচার করেন।
১৮৫১ সালে নেপোলিয়ন তৃতীয় এক ‘অনুদারবাদী’’ অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ফ্রান্সের ক্ষমতা দখল করেন এবং ১৮৭০ সাল পর্যন্ত শাসন করেন, যতক্ষণ না এক ভয়াবহ সামরিক পরাজয়ের পর দেশজুড়ে গণ–আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করা হয়। বিজয়ী ছিলেন বিসমার্ক, যিনি উদারবাদ এবং এর প্রচারকদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন না। এটি একটি লক্ষণীয় বিষয় যে, পুরো উনবিংশ শতকে এত উচ্চ সভ্যতাসম্পন্ন জাতি হওয়া সত্ত্বেও জার্মানদের কাছে উদারতন্ত্র একটি অজানা ধর্ম ছিল, শুধু একবারের ব্যতিক্রম—যেটি ‘ফ্রাঙ্কফুর্টের হাস্যকর সংসদ’ নামে খ্যাত, যা মাত্র এক মৌসুম স্থায়ী হয়েছিল।
জার্মানি তার জাতীয় ঐক্য অর্জন করে উদারবাদের বাইরে এবং এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে। এই মতবাদ একেবারে সেই জার্মান স্বভাবের পরিপন্থী, যাদের রাজতান্ত্রিক মানসিকতা প্রবল, বিপরীতে উদারতন্ত্র ঐতিহাসিক ও যুক্তিসঙ্গতভাবে নৈরাজ্যের আঁতুড়ঘরমাত্র। জার্মান জাতীয় ঐক্যের তিনটি ধাপ ছিল ১৮৬৪, ১৮৬৬ ও ১৮৭০ সালের তিনটি যুদ্ধ, যার নেতৃত্বে ছিলেন ‘মোল্টকে’ ও ‘বিসমার্ক’–এর মতো তথাকথিত ‘উদারবাদী’রা।
ইতালীয় জাতীয় ঐক্য গঠনের ক্ষেত্রে উদারতন্ত্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নগণ্য, যা জুসেপ্পে ম্যাজিনি ও গারিবল্ডির অবদানের তুলনায় অনেকটাই কম, যাঁরা কেউই উদারবাদী ছিলেন না। যদি অনুদার নেপোলিয়ন তৃতীয় হস্তক্ষেপ না করতেন, তবে আমরা লম্বার্ডি পেতাম না; এবং অনুদার বিসমার্ক যদি সদোয়া ও সেডানে হস্তক্ষেপ না করতেন, তবে সম্ভবত ১৮৬৬ সালে ভেনিস বা ১৮৭০ সালে রোম দখল আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না।
১৮৭০ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত সময়কালটি এমন এক পর্বকে নির্দেশ করে, যা এমনকি উদারতন্ত্রের নতুন ধর্মের পুরোহিতদের কাছেও ছিল এক ধসযাত্রার কাল—সাহিত্যে ‘দেকাদেন্তবাদ’ এবং বাস্তবতায় ‘সক্রিয়তাবাদ’–এর দ্বারা আক্রমণে পর্যুদস্ত । এই ‘সক্রিয়তাবাদ’ বলতে জাতীয়তাবাদ, ভবিষ্যতবাদ, এবং ফ্যাসিবাদ।
উনবিংশ শতকের উদারতাবাদ, বহু জটিল ও অবিভাজ্য সমস্যার সঞ্চয় ঘটিয়ে, সেগুলোর সমাধান হিসাবে শেষ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী পথকেই বেছে নেয়। কোনো ধর্মই এরূপ নিষ্ঠুর আত্মত্যাগ দাবি করেনি। তবে কি উদারতাবাদের দেবতাগণ রক্তের জন্যই এত উদগ্রীব ছিলেন?”
এখন উদারতাবাদ তার মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে—সেই মন্দির, যা জনগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। কারণ, জনগণ অনুধাবন করেছে যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উদারতাবাদের যে সংশয়বাদ এবং রাজনীতি এবং নৈতিকতার ক্ষেত্রে এর যে উদাসীনতা—তা অতীতে যেমন বিশ্বকে বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দিয়েছে, ভবিষ্যতেও তেমনি সর্বনাশ ডেকে আনবে।
এই ব্যাখ্যা থেকেই প্রতীয়মান হয় কেন আমাদের সমসাময়িক কালের সকল রাজনৈতিক অনুশীলন ও প্রয়োগসমূহ উদারবাদবিরোধী। আর এই কারণে তাদের ইতিহাসচ্যুত করার প্রয়াস চরম আজগুবি —যেন ইতিহাস কেবলমাত্র উদারতাবাদ ও তার অনুগতদের জন্য সংরক্ষিত কোনো সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র; যেন উদারতাবাদই সভ্যতার চূড়ান্ত পরিণতি, যার গণ্ডি অতিক্রম করার আর কোনো সম্ভাবনাই অবশিষ্ট নেই।
সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং উদারবাদের প্রতি ফ্যাসিবাদী প্রত্যাখ্যানকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা অনুচিত, যা ফ্যাসিবাদকে ১৭৮৯ সালের পূর্ববর্তী কোনো ঐতিহাসিক অবস্থানে বিশ্বকে পুনঃস্থাপনের সমর্থক বলে প্রতিভাত হয়—ঐ বছরটিকে সাধারণত গণতান্ত্রিক–উদারবাদী শতাব্দীর সূচনাবর্ষ হিসেবে গণ্য করা হয়। ইতিহাস কখনও পশ্চাদগামী হয় না। ফ্যাসিবাদী মতবাদ দেমেস্ত্রকে তার পয়গম্বররূপে বিবেচনা করে না। রাজতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র অতীতের বিষয়; তেমনি অন্ধচার্চপূজাও। মৃতপ্রায় এবং বিলুপ্ত হয়েছে সামন্তীয় বিশেষাধিকার ও সমাজের অন্তরীত, পারস্পরিকভাবে বিচ্ছিন্ন বর্ণব্যবস্থার বিভাজন। ফ্যাসিবাদী কর্তৃত্ববাদের ধারণার মধ্যেও পুলিশের দমনমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্য নেই।
একটি দল যখন কোনও জাতিকে ‘সর্বাত্মকভাবে‘ শাসন করে, তা ইতিহাসে নতুন এক প্রবাহের সূচনা। পূর্বে এর কোনো তুলনামূলক উদাহরণ পাওয়া যায় না। উদারতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মতবাদসমূহের ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে ফ্যাসিবাদ কেবলমাত্র সেই উপাদানগুলোকে গ্রহণ করে, যেগুলো এখনো প্রাণবন্ত এবং কার্যকর।ইতিহাসের ‘অর্জিত বাস্তবতা’ হিসেবে যেটি টিকে আছে ফ্যাসিবাদ তাকে সংরক্ষণ করে; বাকি সবকিছু প্রত্যাখ্যান করে। অর্থাৎ, এটি এমন কোনো মতবাদের ধারণাকে গ্রহণ করে না, যা সর্বকালীন এবং সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য। যদি মেনে নেওয়া হয় যে উনবিংশ শতাব্দী ছিল সমাজতন্ত্র, উদারতন্ত্র ও গণতন্ত্রের শতাব্দী, তবু তা এই ধারণা দেয় না যে বিংশ শতাব্দীও সেই একই মতাদর্শ দ্বারা চিহ্নিত হবে। রাজনৈতিক মতবাদসমূহ ক্ষণস্থায়ী; জাতিসমূহ টিকে থাকে। এই বাস্তবতার আলোকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে এটি কর্তৃত্বের শতাব্দী, ডানপন্থিতার দিকে গমনরত একটি ফ্যাসিবাদী শতাব্দী। যদি উনবিংশ শতাব্দী ছিল ব্যক্তির শতাব্দী (যেহেতু উদারতন্ত্র ব্যক্তিবাদকে অনুষঙ্গ করে), তবে আমরা বিশ্বাস করতে পারি এটি ‘সমষ্টির’ শতাব্দী—অতএব রাষ্ট্রের শতাব্দী।
একটি নতুন মতবাদ তার নিজস্ব রচনায় পূর্ববর্তী মতবাদগুলির মধ্য থেকে এখনো কার্যকর উপাদানসমূহ গ্রহণ করাই যৌক্তিক। কোনো মতবাদ সম্পূর্ণ নতুন, দীপ্তিমান ও অভূতপূর্ব রূপে জন্মায় না। কোনো মতবাদই একেবারে মৌলিক বলে দাবি করতে পারে না। প্রতিটি মতবাদই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মতবাদের সঙ্গে ইতিহাসগতভাবে যুক্ত। যেমন, মার্ক্সীয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র সংযুক্ত হয়ে আছে ফুরিয়ে, ওউয়ন এবং সাঁ–সিমঁ–র কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে; যেমন, উনবিংশ শতাব্দীর উদারতন্ত্রের উৎপত্তি নিহিত আছে অষ্টাদশ শতকের আলোকায়ন আন্দোলনে; আবার গণতান্ত্রিক মতাদর্শ উদ্ভূত হয়েছে এনসাইক্লোপেডিস্টদের চিন্তাধারা থেকে। প্রতিটি মতবাদই মানব ক্রিয়াকলাপকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে চায়; কিন্তু এই কার্যকলাপসমূহ আবার বিপরীতমুখে মতবাদকে প্রভাবিত করে, নতুন প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে রূপান্তরিত করে কিংবা তাকে অতিক্রম করে যায়। সুতরাং, একটি মতবাদ হতে হবে এক প্রকার ‘জীবন্ত কর্ম’, কেবল শব্দসমূহের প্রদর্শন নয়। এই কারণেই ফ্যাসিবাদে রয়েছে একটি প্রায়োগিক ধারা, রয়েছে তার ক্ষমতার ইচ্ছা, বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা, সহিংসতার প্রতি মনোভাব এবং তার নিজস্ব মূল্যবোধ।
ফ্যাসিবাদী মতবাদের কেন্দ্রীয় ভিত্তি হলো রাষ্ট্র সম্পর্কিত তার ধারণা—রাষ্ট্রের স্বরূপ, কার্যাবলি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি। ফ্যাসিবাদের কাছে রাষ্ট্র হল পরম; ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সত্তাগুলি আপেক্ষিক। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত অস্তিত্ব কেবল তখনই স্বীকৃত, যতক্ষণ তারা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেখানে উদারতান্ত্রিক রাষ্ট্র কেবল ফলাফল রেকর্ড করার সীমিত ভূমিকায় নিজেকে আবদ্ধ রাখে, ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র সেখানে সমাজের বস্তুগত ও নৈতিক উন্নতির খেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং তার দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র সজাগ, সক্রিয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন; এই কারণেই তাকে ‘নৈতিক রাষ্ট্র‘ হিসেবে বর্ণনা করা যায়।
১৯২৯ সালে শাসনব্যবস্থার প্রথম পঞ্চবার্ষিক সম্মেলনে আমি বলেছিলাম— “ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র কোনো রাত্রি–প্রহরীর মতো নয়, যে কেবল নাগরিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন; কিংবা এটি এমন কোনো কাঠামোও নয়, যার একমাত্র উদ্দেশ্য একটি নির্দিষ্ট মাত্রার ভৌত কল্যাণ ও তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান—এই কাজ তো পরিচালনা পর্ষদও করতে পারে। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র কেবলমাত্র রাজনৈতিক নয়, এমনকি বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নাগরিক ও জাতির বহুবিধ কার্যক্রমের প্রতি নির্লিপ্তও নয়। ফ্যাসিবাদ যে রাষ্ট্র ধারণা লালন ও বাস্তবায়ন করে, তা একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সত্তা, যার লক্ষ্য জাতির রাজনৈতিক, বিচারিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের রূপায়ন; আর এই সংগঠন আত্মারই প্রকাশ, যার উৎস ও বিকাশ একধরনের আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রতিফলন।
রাষ্ট্র কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয় না, বরং জাতির আত্মাও সংরক্ষণ করে ও উত্তরাধিকারসূত্রে তা হস্তান্তর করে—যা গঠিত হয় দীর্ঘ ইতিহাসে তার ভাষা, রীতি, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে। রাষ্ট্র কেবল বর্তমান নয়; এটি অতীত, এবং সর্বোপরি ভবিষ্যতেরও প্রতীক। ব্যক্তির ক্ষণস্থায়ী জীবনের সীমা অতিক্রম করে রাষ্ট্র জাতির অন্তর্নিহিত নৈতিক চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে। রাষ্ট্রের অভিব্যক্তির রূপ বদলাতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকে।
রাষ্ট্র নাগরিকদের নাগরিকচেতনায় শিক্ষিত করে, তাদের মিশনের প্রতি সচেতন করে, ঐক্যের আহ্বান জানায়; রাষ্ট্রের বিচার তাদের পারস্পরিক স্বার্থকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে; রাষ্ট্র ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জ্ঞানের বিজয়—বিজ্ঞান, শিল্প, আইন ও মানবিক সংহতির ক্ষেত্রসমূহে—হস্তান্তর করে; রাষ্ট্র মানুষকে আদিম গোত্র–জীবন থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে মানবিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ রূপ—সাম্রাজ্যিক শাসনের দিকে নিয়ে যায়।
রাষ্ট্র ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করে তাদের স্মৃতি, যারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বা এর আইন মান্য করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন; রাষ্ট্র ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্তরূপে তুলে ধরে সেই সকল অধিনায়কের নাম, যারা এর ভূখণ্ড সম্প্রসারণ করেছেন, এবং সেই প্রতিভাবানদের নাম, যারা একে খ্যাতি এনে দিয়েছেন। রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধা যখন কমে যায়, আর ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত বিচ্ছিন্নতা ও কেন্দ্রবিমুখ প্রবণতা যখন আধিপত্য বিস্তার করে, তখন জাতির পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।”
১৯২৯ সালের পর থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সর্বত্র এই সত্যগুলোকেই তুলে ধরেছে ও জোরদার করেছে। রাষ্ট্রের গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথাকথিত যে ‘সঙ্কট’ চলছে, তা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এবং রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাধান সম্ভব। কোথায় গেলেন সেই জুল সিমোঁর ছায়া, যিনি উদারবাদের সূচনালগ্নে ঘোষণা করেছিলেন— “রাষ্ট্রের উচিত নিজেকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং ইস্তফা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে”? কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ম্যাককালকরা, যারা বলেছিলেন যে ‘রাষ্ট্রের উচিত শাসন থেকে নিজেকে বিরত রাখা’?
আর ইংরেজ দার্শনিক বেন্থাম, যিনি বিশ্বাস করতেন যে শিল্পের একমাত্র চাহিদা রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয়তা; অথবা জার্মান চিন্তাবিদ হাম্বোল্ট, যিনি মনে করতেন ‘সেরা সরকার’ সেই যা ‘আলসে’? আজকের দিনে রাষ্ট্রের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অবিরাম, অপরিহার্য এবং জোরালো হস্তক্ষেপের প্রেক্ষিতে তাঁরা কী বলতেন?
নিশ্চয়ই একথা সত্য যে দ্বিতীয় প্রজন্মের অর্থনীতিবিদগণ রাষ্ট্রহীনতার প্রশ্নে প্রথম প্রজন্মের মতো কঠোর ছিলেন না, এবং এমনকি অ্যাডাম স্মিথ–ও—যদিও অনেক সতর্কতার সঙ্গে—রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনার একটি সামান্য পথ উন্মুক্ত রেখেছিলেন।

শিল্পী: আভো ঘারিবিয়ার
সূত্র: ফাইন আর্ট আমেরিকা
যেখানে উদারবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতীক, ফ্যাসিবাদ সেখানে শাসনব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। তবে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক সৃষ্টিরূপে চিহ্নিত; এটি প্রতিক্রিয়াশীল নয়, বরং বিপ্লবাত্মক। কারণ এটি এমন কিছু সার্বজনীন সমস্যার সমাধান পূর্বাভাস দেয়, যেগুলো অন্যান্য স্থানে ইতোমধ্যেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠেছে।
উদাহারণ স্বরূপ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে—দলগুলোর বিভাজন, সংসদের ক্ষমতা দখল, আইনসভাগুলোর দায়িত্বহীনতা; অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে—বাণিজ্য ইউনিয়ন ও পেশাভিত্তিক সংগঠনগুলোর ক্রমবর্ধমান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, যেগুলোর দ্বন্দ্ব ও সমঝোতা শ্রম ও পুঁজি—উভয় ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে; এবং নৈতিক ক্ষেত্রে— দেশবাদের নৈতিক আদেশ পালনে শৃঙ্খলা, কর্তব্যপরায়ণতা ও আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিপন্ন করে।
ফ্যাসিবাদ চায় একটি শক্তিশালী ও জৈবিক রাষ্ট্র, যার ভিত্তি হবে জনগণের বিস্তৃত সমর্থনের ওপর। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও শাসনের দাবি করে, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই; এটি তার কর্পোরেত কাঠামো, সামাজিক ও শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে। জাতির সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি—যেগুলো নিজ নিজ সংগঠনে সংগঠিত—রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই প্রবাহিত হয়।
একটি রাষ্ট্র, যা লাখো মানুষের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যারা তার কর্তৃত্ব স্বীকার করে, তার কার্যকলাপ অনুভব করে এবং তার লক্ষ্যসাধনে আত্মনিয়োগে প্রস্তুত—সে রাষ্ট্র কোনো মধ্যযুগীয় স্বৈরশাসকের অত্যাচারী রাষ্ট্র নয়। এটির সাথে ১৭৮৯ সালের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনো একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মিল নেই। ব্যক্তি–মানুষকে চূর্ণ করার পরিবর্তে, ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র তার শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে; যেমন একটি রেজিমেন্টে একজন সৈনিক তার সহযোদ্ধাদের মাধ্যমে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে বরং বহুগুণে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র জাতিকে সংগঠিত করে, তবে ব্যক্তি–মানুষের জন্য যথাযথ কর্মকাণ্ডের পরিসরও বজায় রাখে। এটি অনাবশ্যক বা ক্ষতিকর স্বাধীনতাকে হ্রাস করেছে, কিন্তু যে স্বাধীনতাসমূহ অপরিহার্য, সেগুলিকে সংরক্ষণ করেছে। এ বিষয়ে ব্যক্তি নিজে বিচারক হতে পারে না; কেবল রাষ্ট্রই এই বিচার করার অধিকার রাখে।
ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র সাধারণভাবে ধর্মীয় অভিব্যক্তিগুলোর প্রতি নিরাসক্ত নয়, এবং এটি ইতালীয়দের বিশেষ ও ইতিবাচক ধর্ম—রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রতিও নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে না। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মতত্ত্ব নেই, তবে একটি নৈতিক বিধিব্যবস্থা রয়েছে। ফ্যাসিবাদ ধর্মকে আত্মার গভীরতম প্রকাশগুলোর অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করে, এবং এই কারণেই এটি কেবল ধর্মকে শ্রদ্ধা করে না, বরং তা রক্ষা করে ও সংরক্ষণ করে। ফরাসি বিপ্লবের চরম পর্যায়ে কনভেনশনের সময় রোবসপিয়ের যেভাবে নিজের মতো করে একটি “ঈশ্বর” দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন, ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র তেমন কোনো প্রয়াস গ্রহণ করে না; আবার বলশেভিকপন্থীরা যেভাবে মানুষের আত্মা থেকে ঈশ্বরকে মুছে ফেলতে চায়, তেমন নিষ্ফল প্রচেষ্টাও এটি করে না। বরং ফ্যাসিবাদ আত্মসংযমী সাধক, সাধু এবং বীরদের ঈশ্বরকে যেমন শ্রদ্ধা করে, তেমনি সরল ও আদিম হৃদয়ের সাধারণ জনগণের ঈশ্বরকেও সম্মান জানায়—যাঁর উদ্দেশে তারা প্রার্থনা করে।

ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র শাসন করার এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রোমান ঐতিহ্য এক শক্তিশালী চেতনারূপে প্রতিফলিত হয়েছে। ফ্যাসিবাদী মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা কেবল ভূখণ্ডগত, সামরিক বা বাণিজ্যিক নয়; বরং তা একাধিক মাত্রায় আত্মিক ও নৈতিকও বটে। একটি সাম্রাজ্যবাদী জাতি—অর্থাৎ যে জাতি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে অন্য জাতিগুলোর নেতৃত্ব দেয়—সে এক বর্গমাইল ভূখণ্ড দখল না করেও অস্তিত্বশীল হতে পারে। ফ্যাসিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চেতনার মধ্যে—অর্থাৎ জাতির সম্প্রসারণমূলক প্রবণতার মধ্যে—তাদের প্রাণশক্তির প্রকাশ দেখতে পায়। বিপরীত প্রবণতা, যা জাতীয় স্বার্থকে কেবলমাত্র স্বদেশের সীমায় সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, তাকে ফ্যাসিবাদ অবক্ষয়ের লক্ষণ হিসেবে গণ্য করে। যে জাতিগুলো পুনরুত্থিত হয়, তারা স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ধারণ করে; পক্ষান্তরে, যে জাতিগুলো পতনের পথে, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো ত্যাগের মনোভাব। ফ্যাসিবাদী মতবাদই এমন একটি মতবাদ, যা এমন এক জাতির প্রবণতা ও অনুভূতির সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ—যেমন ইতালীয় জাতি, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী বিদেশি দাসত্বে নিষ্ক্রিয় থাকার পর এখন বিশ্বমঞ্চে নিজেদের পুনরুজ্জীবিত করে প্রতিষ্ঠা করছে।
কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ মানেই শৃঙ্খলা, প্রচেষ্টার সমন্বয়, দায়িত্ববোধের গভীরতা এবং আত্মত্যাগের মানসিকতা। এই বাস্তবতা ব্যাখ্যা করে শাসনব্যবস্থার বহু ব্যবহারিক কার্যক্রম, রাষ্ট্রের বিভিন্ন শক্তির গতিপথ এবং সেই কঠোরতাকেও, যা প্রয়োগ করতে হয় তাদের বিরুদ্ধে—যারা বিংশ শতকের ইতালির এই স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য অভিযাত্রাকে প্রতিহত করতে চায়, উনবিংশ শতকের পরিত্যক্ত মতাদর্শকে উসকে দিয়ে। এই মতাদর্শসমূহ আজ সর্বত্র বর্জিত, যেখানে বৃহৎ রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের সাহসী পরীক্ষাগুলো পরিচালিত হচ্ছে।
কোনো যুগেই মানুষ আজকের মতো কর্তৃত্ব, দিকনির্দেশনা ও শৃঙ্খলার জন্য এত গভীর তৃষ্ণা প্রকাশ করেনি। যদি প্রতিটি যুগেরই একটি নিজস্ব মতবাদ থাকে, তবে অসংখ্য লক্ষণ এটিই নির্দেশ করে যে আমাদের যুগের মতবাদ হলো ফ্যাসিবাদ। এর প্রাণশক্তির প্রমাণ হলো—এটি এক বিশ্বাসকে উদ্দীপিত করেছে; এবং সেই বিশ্বাস যে মানুষের আত্মাকে জয় করেছে, তার প্রমাণ হলো—ফ্যাসিবাদ আজ দেখাতে পারে তার আত্মোৎসর্গকারী বীর ও শহিদদের।
ফ্যাসিবাদ এখন বিশ্বব্যাপী সেই সর্বজনীনতা অর্জন করেছে, যা প্রতিটি মতবাদ লাভ করে, যখন তা আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে মানব চিন্তার ইতিহাসে একটি বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।