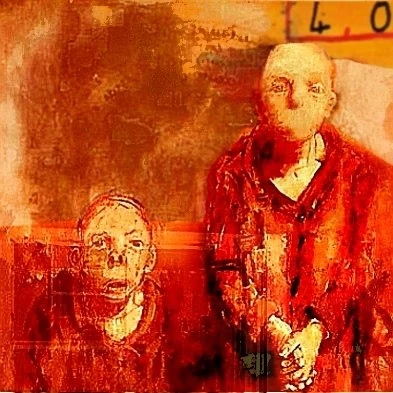- অনুবাদ: আবদুল্লাহ বুবুন
[বর্তমান সময়ে গোটা বিশ্বেই বুদ্ধিত্তিক ও একাডেমিক অঙ্গনে ফরাসি উত্তর–আধুনিক বা আরও স্পষ্ট করে বললে উত্তর–কাঠামোবাদি চিন্তার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্যণীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী প্রেক্ষাপটে গোটা বিশ্ব দুটি সুপার পাওয়ারে ভাগ হয়ে যখন বৈশ্বিক প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তার প্রভাব পড়ে বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনেও। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী শক্তি, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র। এই দুই শক্তিকে কেন্দ্র করেই সম্রাজ্যের প্রয়োজনেই বিকাশ লাভ করতে থাকে নানা বুদ্ধিবৃ্ত্তিক ও ভাবাদর্শিক চিন্তাধারা। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমরা দেখতে পাই ফরাসি বামপন্থী দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে একটা নতুন বাঁকবদলের। এই নতুন দার্শনিক গোষ্ঠীদের এখন প্রায়শই উত্তর–কাঠামোবাদী, উত্তর–আধুনিকতাবাদী নানা তকমায় চিহ্নিত করা হয়। এই নতুন দার্শনিক গোষ্ঠীর মধ্যে আমরা একদিকে যেমন দেখতে পাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি ভরসা হারিয়ে ফেলার ব্যাপারটি, অন্যদিকে জনপরিসরে রাজনৈতিক বিতর্ক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার প্রতি অনাগ্রহ। বিপ্লবী রাজনীতির কৌশল, কর্মপন্থার বদলে তাদের বিশ্লেষণের কেন্দ্রে চলে আসে রাষ্ট্র, ক্ষমতা, ভাষা ও সংস্কৃতি। এই দার্শনিক গোষ্ঠী এসে আধুনিকতাবাদের যাবতীয় মেটান্যারেটিভ বা মহাবয়ানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। মার্ক্সবাদকেও তারা দেখেন এক মহাবয়ান হিসেবে। ফলে স্বভাবতই মার্ক্সবাদের গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ তাদের ব্যবচ্ছেদের লক্ষ্য হয়ে উঠে। ১৯৮৫ সালে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ একটি গবেষণাপত্র প্রস্তুত করে ফরাসি এই নতুন দার্শনিক, বুদ্ধিবৃত্তিক গোষ্ঠীদের নিয়ে। সিআইএর মূল্যায়নে এই নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক বাঁকবদল একদিকে যেমন ফ্রান্সে সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত প্রভাব খর্ব করতে সাহায্য করবে একই সাথে মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রতিবন্ধকতা হিসেবেও কাজ করবে। ২০১১ সালে সিআইএ এই প্রতিবেদনটির একটি সেন্সরড ভার্শন প্রকাশ করে তথ্য অধিকার আইনের আওতায়। মূল প্রতিবেদনটি পড়তে এই লিংকে ক্লিক করুন। ২০১৭ সালে ওপেন কালচার নামক একটি অনলাইন পোর্টাল সিআইএর এই প্রতিবেদনটির উপর একটি পর্যালোচনা প্রকাশ করে। বর্তমান নিবন্ধটি সেই পর্যালোচনারই অনুবাদ। – সম্পাদক]
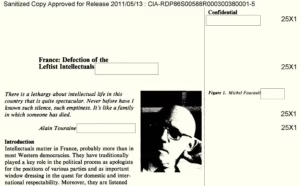
ছবি: সিআইএর প্রতিবেদনের একটি পাতা
দর্শনের মতো একটি শাস্ত্রের সরকারি নীতি–নির্ধারণ তথা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে তেমন কোন প্রভাব থাকতে পারে, তা আমরা সাধারণত মনে করি না৷ কেননা, সরকারের কার্যক্রমকে সদা প্রভাবিত করা নির্ধারকগুলোর (মধ্যবিত্তের টিকে থাকার উদ্বিগ্নতা বা উচ্চবিত্তের স্টক নিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা কিংবা দারিদ্র্যের সদা উপস্থিতি) অবস্থান দর্শনের আলোচ্য বিষয় থেকে অনেক দূরে। তবে আমাদের এই অনুমান সবসময় সত্য নাও হতে পারে। বিভিন্ন সময়ে যখন চিন্তাশীল ও পড়ুয়া ব্যক্তিরা রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী কিংবা সিনেটর হয়েছেন, তখন ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা, লিও স্ট্রস, জার্গেন হাবারমাস কিংবা জন রলসের (যিনি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন) মতো দার্শনিকদের ধ্যানধারণা রাষ্ট্রনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। ঐতিহাসিকভাবে খুব কম দার্শনিকই জার্মান চিন্তক কার্ল স্মিটের মতো প্রভাবশালী ছিলেন; যদিও তার প্রভাবের স্বরূপ ছিল সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক৷ এছাড়া রয়েছে জন লক, জাঁ জ্যাক রুশো, থমাস হবস, অ্যারিস্টল এবং সক্রেটিস, যারা রাজনীতিতে বিভিন্ন সময়ে বহুমুখী প্রভাব রাখা দার্শনিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।
তবে যখন আমরা উত্তর–আধুনিকতাবাদের সাথে জড়িত ফরাসি বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের (যার কেন্দ্রে ছিলেন মিশেল ফুকো, রোলা বার্থ, জাক লাকাঁ, দেরিদাসহ আরও অনেকে) দিকে তাকাই, তখন রাষ্ট্রনীতিতে তাদের তেমন সরাসরি প্রভাব দেখা যায় না। অধিকাংশ সময়ই এইসব লেখকরা গুরুত্বহীন ও প্রভাবশূন্য বলে বিবেচিত হয়। দায়ী করা হয় তাদের ভাষাকে, যা বামঘেষা একটি অভিজাত বুদ্ধিবৃত্তিক বলয় ব্যতীত অন্য কেউ বুঝতে পারে না। এই বক্তব্য সম্ভবত কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—যেখানে ক্ষমতাকে প্রায়শই তত্ত্বায়িত করা হলেও খুব কম সময়ই মূলধারার প্রকাশনায় ক্রিটিক করা হয়৷ তবে এই আলাপ ফ্রান্সের ক্ষেত্রে সত্য নয়। অন্তত সিআইএ তা–ই মনে করে। কমিউনিজম ও অ্যান্টি–আমেরিকানিজমের বিরুদ্ধে নিজেদের দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের অংশ হিসেবে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে ফরাসি দর্শনের প্রভাবকে এই সংগঠনটি খুব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং তাদের এই দীর্ঘমেয়াদী অনুসন্ধান নথিবদ্ধ করতে ১৯৮৫ সালে তারা একটি গবেষণা প্রবন্ধ তৈরি করে৷
সম্প্রতি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় করা একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে এই নথির একটি পরিশোধিত অনুলিপি “ফ্রান্স: ডিফেকশন অব লেফটিস্ট ইন্টেলেকচুয়াল” নামে প্রকাশিত হয়েছে। বিস্ময়করভাবে, এই নথি উত্তর–কাঠামোবাদী চিন্তকদের রাজনৈতিক অভিমুখকে ইতিবাচকভাবে দেখেছে। ইয়ানোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রফেসর ও র্যাডিকেল হিস্ট্রি ও দি পলিটিক্স অব আর্ট–এর লেখক গ্যাব্রিয়েল রকহিল ফরাসি উত্তর–কাঠামোবাদ সম্পর্কিত সিআইএর মূল্যায়নকে এল এ রিভিউ অব বুকের জন্য সামারাইজ করেছেন এভাবে:
“…গুপ্ত সাংস্কৃতিক যোদ্ধারা (সিআইএ) মূলত প্রশংসা করেছে দুটি পরিবর্তনকে৷ এক, উত্তর–কাঠামোবাদী বাঁকবদলের মাধ্যমে ফরাসি বুদ্ধিজীবী মহলের সমালোচনার মূখ্য লক্ষ্যবস্তু যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে চলে যায়। বৃহত্তর বামপন্থী বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতায় ধীরে ধীরে স্ট্যালিনবাদ ও মার্ক্সবাদ নিয়ে অনাগ্রহ দেখা যায়; র্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবীরা জনপরিসরের বিতর্ক থেকে ক্রমশ দূরে সরে আসে; এবং তাত্ত্বিক অবস্থানের জায়গা থেকে সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক দল থেকে দূরে সরে আসতে থাকে। অপরদিকে ডানপন্থীদের মধ্যে মতাদর্শগত সুবিধাবাদী হিসেবে পরিচিত “নিউ ফিলসফারস” ও “নিউ রাইট” বুদ্ধিজীবীরা গণমাধ্যমে মার্ক্সবাদ বিরোধী একটি হাইপ্রোফাইল স্মিয়ার ক্যাম্পেইন শুরু করে।“
সিআইএ এজেন্টরা তাদের প্রতিবেদনে লিখেছেন, “মার্ক্সবাদ ও সোভিয়েত বিরোধিতার এই উদ্দীপনা ফ্রান্সে কারও পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মার্কিন নীতির কোনো বিরোধিতা গড়ে তোলাকে কঠিন করে তুলবে।” ফরাসি সংস্কৃতি ও সরকারের ওপর “নিউ লেফট বুদ্ধিজীবীদের” প্রভাব এতটাই প্রবল ছিল যে, তারা ধারণা করেছিল, “প্রেসিডেন্ট [ফ্রাঁসোয়া] মিতেরঁ সাম্প্রতিক সময়ে মস্কোর প্রতি যে তাৎপর্যপূর্ণ শীতলতা দেখিয়েছেন, তার পেছনে কিছুটা হলেও এই সর্বব্যাপী বৌদ্ধিক মনোভাব ভূমিকা রেখেছে।“

রকহিল লিখেছেন, এই গবেষণায় ফ্রান্সের নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক মহলের প্রভাব সম্পর্কিত (সিআইএর অভিমত অনুযায়ী) যে চিত্র উঠে এসেছে, তা আগের প্রজন্মের “দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর সময়ের বামঘেঁষা বুদ্ধিজীবীদের” থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন“। ওই প্রজন্মের বুদ্ধিজীবীরা “মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করতো” এবং আমেরিকান গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিল। জঁ–পল সার্ত্রে এমনকি “প্যারিসে সিআইএ স্টেশন অফিসার এবং ডজনখানেক আন্ডারকভার এজেন্টের পরিচয় ফাঁস” করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলে এবং এই কারণে তিনি সিআইএ এর “নিবিড় নজরদারি“-তে ছিলেন। সার্ত্রে সিআইএর কাছে একটি গুরুতর সমস্যারূপে বিবেচিত ছিলেন। তবে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে একই সংস্থা বিজয়োল্লাসে ঘোষণা করেছিল, “এখন আর কোনো সার্ত্রে নেই, নেই কোন গিদে।” তারা লিখেছিল, “কমিউনিস্ট পণ্ডিতদের সর্বশেষ গোষ্ঠী নিজেদের শিষ্যদের তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েছিল, কিন্তু তখন কারোরই আর মার্ক্সবাদের পক্ষে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার মানসিকতা ছিল না।” এ কারণে স্নায়ু যুদ্ধের শেষ পর্বে “সব রাজনৈতিক ধারার বুদ্ধিজীবীদের মাঝেই মতাদর্শ থেকে সরে আসার একটি বড় প্রবণতা” লক্ষ করা যায়।
“স্ট্যালিনবাদী কাল্ট”–এর একেবারেই অসমর্থনযোগ্য একনায়কতান্ত্রিক দমন–পীড়ন এবং ওয়াশিংটন কনসেনসাস ও তার দ্বারা সৃষ্ট বহুজাতিক কর্পোরেটবাদের অবশ্যম্ভাবী হিসেবে হাজির হওয়ার বাস্তবতা এক ধরনের ক্লান্তিতেই যেন আচ্ছাদিত করেছিল চারদিক। কমিউনিজমের পতনের সময়ে মার্কিন দার্শনিকরা প্রলয় তথা কিয়ামতের ভাষা ব্যবহার করছিল—এন্ড অব হিস্ট্রি। একইসাথে, তারা উদযাপন করছিলেন ওই যুগান্তকারী ঘটনাকে যাকে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা আখ্যায়িত করেছিল সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে “উদার গণতন্ত্রের” জয় হিসেবে। ফুকুয়ামার বই দ্য এন্ড অব হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ম্যান শিরোনামের মাধ্যমেই এই বিস্ময়কর তত্ত্বকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। অর্থ্যাৎ, আর কোনো বিপ্লব হবে না। হার্ভার্ডের চিন্তক স্যামুয়েল হান্টিংটন এই সময়কে তাই “সমাপ্তির যুগ” বলে ঘোষণা করেছিলেন ঠিক যেই সময়ে “শিল্পের সমাপ্তি,” “প্রকৃতির সমাপ্তি,” ইত্যাদি নানা অতিরঞ্জিত তর্কের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। আর সিআইএ–র মতে, বার্লিন প্রাচীর পতনের ঠিক আগের কয়েক বছরে ফ্রান্সের অতীতে শক্তিশালী দার্শনিক বামপন্থীরা “এক ধরণের ঔদাসীন্যে আক্রান্ত” হয়েছিল৷
এই প্রতিবেদনে সিআইএ উত্তর–কাঠামোবাদী দার্শনিকদের জনমতকে সমাজতন্ত্র থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া এবং “মার্ক্সবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি জনসাধারণের মনোভাবকে কঠোরতর করে তোলার” জন্য কৃতিত্ব দেয়ার পাশাপাশি আরও লিখেছিল যে “উত্তর–কাঠামোবাদী দার্শনিকদের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে এবং তারা শিগগিরই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরাসরি বড় কোন প্রভাব রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।” তাদের এই বক্তব্য কি সঠিক ছিল? যদি আমরা বহু–কথিত “পরিচয়বাদী রাজনীতি”–র সমালোচকদের গুরুত্ব দিয়ে দেখি, তবে এই প্রশ্নের উত্তর হবে: একেবারেই না। আবার, যারা উত্তর–আধুনিক দর্শন এবং সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি প্রভাবশালী বামপন্থী চিন্তাধারা ও আন্দোলনকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন, তারা যুক্তি দিতে পারেন যে, সিআইএ তাদের সিদ্ধান্তে অদূরদর্শী ছিল। হয়তো স্নায়ু যুদ্ধের কয়েক দশকের কূটকৌশলে গড়ে ওঠা দ্বৈততাবাদী (Manichean) দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তারা এমন এক রাজনীতির কথা কল্পনা–ই করতে পারেননি, যা একইসঙ্গে আমেরিকান ও সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে পারে।

তবুও মতাদর্শ থেকে সরে আসার অর্থ মোটেও রাজনীতি থেকে সরে আসা নয়। বলা যেতে পারে, গোয়েন্দাদের মাঝে এই অদ্ভুত গবেষণা প্রবন্ধটি প্রচারিত হওয়ার তিরিশ বছর পর ফুকোর “বায়োপাওয়ার” কিংবা দেরিদার পরিচয় (আইডেন্টিটি)-কে প্রবলেম্যাটাইজ করা ধারণাগুলো আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর (যদিও আমরা সবসময় তাদের কাজ পড়ি না বা পুরোপুরি বুঝি না)। তবে সংস্থাটি উত্তরাধুনিক চিন্তার সর্বব্যাপী প্রভাব আগে থেকে অনুমান করতে না পারলেও তারা এই দার্শনিক ঐতিহ্যকে কখনোই অস্পষ্ট কিংবা তুচ্ছ জটিল বাক্যবিন্যাস হিসেবে বাতিল করে দেয়নি। রকহিল লিখেছেন, “যদি কেউ ধরে নেয় যে, বুদ্ধিজীবীরা ক্ষমতাহীন কিংবা আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান কোনো গুরুত্ব বহন করে না, তবে মনে রাখবেন, সমসাময়িক বিশ্বরাজনীতির অন্যতম প্রভাবশালী ক্রীড়ানক আপনার ধারণার সঙ্গে একমত নয়। এই সদ্য প্রকাশিত প্রতিবেদনটি বুদ্ধিজীবীদের ক্ষমতার একটি স্মারক হয়ে থাকবে।“