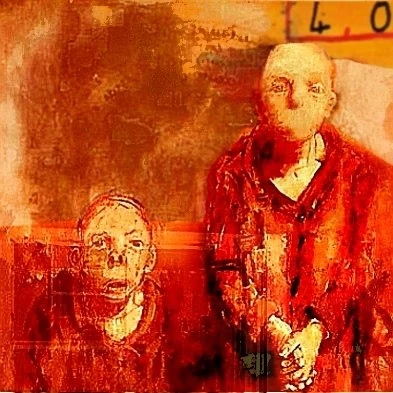- তৌহিদুল ইসলাম
[ইতালিয়ান দার্শনিক জর্জিও আগামবেনের Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life বইটি ইতোমধ্যেই আমাদের পাঠকের কাছে পরিচিত। বইটিতে আগামবেন তার হোমো সাকের ধারণার একটি বিস্তর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হাজির করেন। আগামবেন দেখান আধুনিক রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতা কীভাবে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। ফুকো যেখানে জৈবক্ষমতার ধারণা হাজির করে আমাদের দেখান আধুনিক রাষ্ট্র জৈবক্ষমতার নিয়ন্ত্রণের দ্বারা আমাদের কীভাবে আমাদের জীবন রক্ষা করে চলে, আগামবেন সেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার একটা বিশেষ দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আগামবেন দেখান আধুনিক রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতা তার নিজের প্রয়োজনেই তার ব্যতিক্রমী অবস্থার তৈরি করে, যেই ব্যতিক্রমী অবস্থার মধ্য দিয়ে কাউকে ঠেলে দেয়া হয় রাষ্ট্রীয় ও আইনি সুরক্ষার বাইরে। পরিণত করা হয় হোমো স্যাকারে। আগামবেনের মতে হোমো স্যাকার হলো সেই জীবন যাকে যে কেউই হত্যা করতে পারে, এবং এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কোনো বিচার বা শাস্তির সম্মুখীন তাকে হতে হয় না। তৌহিদুল ইসলাম তার এই লেখায় আগামবেনের এই বইটির উপর কিছু নোক্তা হাজির করেন, যা আগামবেনের মূল ধারণার একটা সংক্ষিপ্ত টীকা আকারে দেখা যেতে পারে – সম্পাদক]
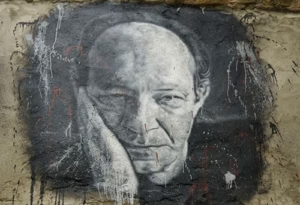
১.
গ্রিক zoe এবং bios দুইটাই প্রাণ বা জীবন অর্থে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক। প্রথমটা ব্যবহৃত হতো জীবের জীবন অর্থে। অর্থাৎ, যেখানে জীবন তার খুৎনিবৃত্তির স্তর অতিক্রম করে নাই। খাওয়া, পড়া, বেঁচে থাকার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে, থাকে বায়োস। যার অর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক জীবন। বাংলার তন্ত্রে একটা কথা প্রচলিত আছে– “পাশবদ্ধ ভবেৎ জীব, পাশমুক্ত ভবেৎ শিব“। গ্রিক জো’কে আমরা বলতে পারি এই জীব। যে নানা পাশে বদ্ধ আছে বলে কল্পনা করা হয়। গ্রিক জো বা জীবের এই বায়োসে রূপান্তর তখনই সম্ভব যখন সে সমাজে প্রবেশ করে, রাজনৈতিকতায় অভিষিক্ত হয়। নিজের অধিকার, ভালো মন্দের নৈতিক ধারণা, আইন সম্পর্কে সচেতন না হয়ে জীবন ধারণ করতে পারে না। জো আর বায়োস জীবনের দুই প্রান্ত মনে হলেও এখানে একটা সরলরৈখিক রূপান্তরের ধারণা আছে। সেই রূপান্তর ঘটে জো বা জীবের। জীব থেকে সে নাগরিক হয়ে ওঠে।
২.
এরিস্টটলের “Politics” থেকে জো এবং বায়োসের এই আলোচনায় আগামবেন মিশেল ফুকোর হিস্টরি অব সেক্সুয়ালিটিতে এ বিষয়ে একটা তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করেন, যেখানে ফুকো দেখান, আধুনিক সময়ে রাষ্ট্র কীভাবে তার যন্তরমন্তর আর হিসাবনিকাশের মাধ্যমে এই জো বা জীবের জীবন একটা কাঁচামাল হিসেবে হাজির হয় যার থেকে জন্ম আধুনিক বায়োপলিটিক্সের বা জৈবরাজনীতির। ফুকো বলেন, “For millennia man remained what he was for Aristotle: a living animal with the additional capacity for political existence; modern man is an animal whose politics calls his existence as a living being into question.”
৩.
ফুকো এখানে চিহ্নিত করেন আধুনিক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে তার প্রক্রিয়াটিকে। যে প্রক্রিয়ার গোঁড়ায় আমরা দেখতে পাবো ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডের চালানো ভায়োলেন্স যা এই জীবের রক্তমাংসে নানাবিধ নামচিহ্নের টোকেন গেঁথে দিচ্ছে। তাকে নানা বর্গে ভাগ করে রেখে দেয়া হচ্ছে নানাবিধ খোপে, খাঁচায়। আর পুরো প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে এমন একটা সর্বব্যাপী আয়োজনের ভিতর দিয়ে যে মানুষ সজ্ঞানেই নিজেকে সঁপে দিচ্ছে সেই জ্ঞানের বেদিতলে। ফুকো এই প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করেন ইউরোপীয় রাষ্ট্র কাঠামোর টেরিটরিয়াল স্টেট থেকে পপুলেশন স্টেটে রূপান্তর হিসেবে। আগে যেখানে রাষ্ট্র কিছু কাল্পনিক রেখার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে এবং সার্বভৌমত্বকে চিহ্নিত করতে ব্যবহার করতো টেরিটরি ধারণা, সেই রাষ্ট্রের নতুন কেন্দ্র হয়ে হাজির হলো জনগণ নামের নতুন বর্গ যা রাষ্ট্রের ক্ষমতা চর্চার এবং ক্ষমতাকে পুনরুৎপাদন করার নতুন উপকরণ। এই ক্ষমতা ক্রমেই এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছালো যা একই সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিকাশের মাধ্যমে মানুষের জীবন বাঁচানোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলো, আবার একই সঙ্গে হলোকাস্টের মত নারকীয় ঘটনারও জন্ম দিলো।
৪.
আগামবেন বলেন, এই জৈবক্ষমতার উদ্বোধনের মাধ্যমে মানুষের আচার–আচরণ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া ক্যাপিটালিজমের বিকাশও সম্ভবপর হতো না।
আগামবেন হানা আরেণ্ডের হোমো লেবারানের উল্লেখ করে দেখান যে ফুকোর আগেই আরেন্ডের চিন্তায় বায়োপাওয়ারের ডিসিপ্লিনারি প্রক্রিয়া এবং আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের ওপর তার প্রভাবের নজির থাকলেও সেইটার সঙ্গে টোটালিটারিয়ান ক্ষমতার সম্পর্ক নিয়ে আরেন্ড তেমন সচেতন ছিলেন না। আবার ফুকোও তার জৈবক্ষমতার বিশ্লেষণে তার সমসাময়িক সময়ের উদাহরণগুলি খুব বেশি টানেননি। এর মাধ্যমে আগামবেন দেখাতে চান যে জৈবক্ষমতা এবং বেয়ার লাইফের সম্পর্ক এতই আচ্ছাদিত যে পশ্চিমা চিন্তকরা খুব রেয়ারলি তার টিকি ধরে টান দিতে পেরেছেন।
৫.
এই আচ্ছাদিত বিষয়টিকে নিরাবরণ করতে আগামবেন বলেন, হোমো সাকেরে তার কাজ হলো ক্ষমতার আইনি–প্রতিষ্ঠানগত এবং জৈবরাজনৈতিক মডেলের ছেদবিন্দুটির ব্যবচ্ছেদ। কারণ সার্বভৌম ক্ষমতা গঠিতই হয় বেয়ার লাইফকে রাজনৈতিক জগতে অন্তর্ভূক্ত করার ভিতর দিয়ে। অথবা, সার্বভৌম ক্ষমতার আদি কাজটিই হলো এই জৈবরাজনৈতিক দেহের নির্মাণ। আগামবেনের মতে, এই অর্থে সার্বভৌম ব্যতিক্রম আর জৈবরাজনীতি সমান বয়সী। arcana imperii.
তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন পশ্চিমা রাজনীতি নিজেকে গঠনই করে বেয়ার লাইফকে বর্জনের (যা একই সঙ্গে অন্তর্ভূক্তিকরণও বটে, বর্জনের অন্তর্ভূক্তিকরণ!) ভিতর দিয়ে।
৬.
এরপর আগামবেন একটা দুর্দান্ত কাজ করেন। জো এবং বায়োসের দ্বৈততা থেকে তিনি পশ্চিমা চিন্তার একটা কেন্দ্রীয় অধিবিদ্যক প্রবণতার সঙ্গে একে মিলিয়ে দেখেন। এরিস্টটল যেইভাবে জো থেকে বায়োসে রূপান্তরকে জীবের রাজনৈতিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া হিসেবে হাজির করেন, একইভাবে আগামবেন দেখান, পশ্চিমা অধিবিদ্যার খুব কেন্দ্রীয় প্রবণতা হলো কণ্ঠস্বর থেকে ভাষায় পৌঁছানো। যেখানে ভাষা হলো সেই এলাকা যা মানুষকে মানুষ করে তোলে। মানুষ একই সঙ্গে মানুষ হয়ে ওঠে ভাষা ও রাজনৈতিকতায়। আগামবেন বলেন: The question “In what way does the living being have language?” corresponds exactly to the question “In what way does bare life dwell in the polis?” তার মতে, পশ্চিমা অধিবিদ্যার সহি বড় আদি ও আসল সুরত হইলো রাজনীতি যার মারেফতে জীব ও ভাষার (logos) সম্পর্কে মুসাবিদা হয়। জীব বা বেয়ার লাইফের রাজনীতিকরণের মাধ্যমেই মানবের চূড়ান্ত অধিবিদ্যক গন্তব্য নিহিত। যেহেতু আধুনিক জমানায় ক্ষমতা নিজেকে জাহির করে বেয়ার লাইফকে রাজনৈতিক স্ফিয়ারে নিয়ে আসার মাধ্যমে, তাই এর মাধ্যমে আধুনিকতা পশ্চিমা অধিবিদ্যার গোপন পারপাসই সার্ভ করে। জার্মান জুরিস্ট কার্ল শ্মিটের বিপরীতে তিনি বলেন, পশ্চিমা রাজনীতির মৌলিক ক্যাটাগরি বন্ধু/শত্রু দ্বৈততা না, বরং বেয়ার লাইফ/ রাজনৈতিক অস্তিত্ব, জো/বায়োস, এক্সক্লুশন/ইনক্লুশনের স্ট্রাকচারে নিহিত। আগামবেন বলেন, রাজনীতি আছে কারণ মানুষ হইলো সেই জীবিত জন্তু যে ভাষার ভিতরে ঢুকে নিজেকে তার বেয়ার লাইফ থেকে আলাদা করে, তার বিপরীতে দাঁড় করায় এবং একই সাথে, নিজেকে নির্ণয় করে সেই বেয়ার লাইফের সাপেক্ষে একটা অন্তর্ভূক্তিমূলক এক্সক্লুশনের মাধ্যমে।
৭.
এই যে বেয়ার লাইফ, যারে নিয়ে এত কাহিনি, সেই হইলো আগামবেনের এই বইয়ের নায়ক। তথা প্রটাগনিস্ট। এই বেয়ার লাইফই হলো হোমো সাকের (পবিত্র মানব), যাকে হত্যা করা জায়েজ কিন্তু কুরবানি দেয়া জায়েজ না। আধুনিক রাজনীতিতে এই প্রটাগনিস্টকে কীভাবে ব্যবহার করা হয় সেটাই, আগামবেন বলেন, এই বইয়ের মূল কাজ। রাষ্ট্রে যেমন সব মানুষের একটা আইনি অস্তিত্ব থাকে যার ভিত্তিতে সে কিছু অধিকার ভোগ করে কিন্তু হোমো সাকেরের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হলো তাকে হত্যা করা জায়েজ।
৮.
আগামবেনের মতে, আধুনিক রাষ্ট্রে এই জৈবরাজনীতির ট্রান্সফর্মেশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যে এখানে বেয়ার লাইফ বা হোমো সাকের আর কেবলমাত্র একটা ব্যতিক্রম হিসেবে থাকে না, বরং এটা নিজেই একটা নিয়ম হয়ে ওঠে। যেইটাকে আগামবেন বলেন, ইরিডিউসিবল ইনডিসটিঙ্কশন। অর্থাৎ, যে কারো যেকোনো সময়ে হোমো সাকের হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এটা কেবলমাত্র আর প্রান্তের একটা বিষয় না, বরং আধুনিক রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীয় বিষয়।
৯.
আগামবেন আধুনিক গণতন্ত্রকে দেখেন এই বেয়ার লাইফকে তাঁর রাজনৈতিক বলয়ে ইন্টিগ্রেশনের দীর্ঘ ধারাবাহিক সংগ্রামী প্রক্রিয়া হিসেবে। যার মাধ্যমে বেয়ার লাইফের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু সেই গণতন্ত্রের পক্ষেও তার যে অন্তর্গত এপোরিয়া সেটাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয় না। বরং, বেয়ার লাইফ একটা বধযোগ্য ক্যাটাগরি হিসেবে বর্তমান থাকে। আধুনিক গণতন্ত্রের টোটালিটারিয়ানিজমের সঙ্গে সহবতে এটা প্রমাণিত হয়েছে নাজিবাদ ও ফ্যাসিবাদের সময়ে, বিশেষ করে হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, যেখানে মানুষকে তার সকল মানবিক মর্যাদা থেকে ছিন্ন করে একেবারে আক্ষরিক বেয়ার লাইফে পরিণত করা হয়েছিল।

১০.
আগামবেনের মতে, গণতন্ত্র এবং টোটালিটারিয়ানিজমের মধ্যে একটা সলিডারিটি আছে, এই দুই ব্যবস্থার সকল ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পার্থক্যসমেতই। এই ব্যর্থতা আগামবেনের মতে পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসের ব্যর্থতা যেখানে জো আর বায়োস, কণ্ঠ এবং লোগোসের মধ্যে রূপান্তরের কোন সম্পর্ক তৈরি করতে পারেনি, যা এই ক্ষতকে নিরাময় করতে পারে। বেয়ার লাইফের এক্সক্লুশনারি ইনক্লুশনকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা রাজনীতি থেকে বের হতে না পারলে এর কোন সমাধান নেই।
১১.
কার্ল শ্মিটের– সার্বভৌম হলো সেই যে ব্যতিক্রম কী হবে সেটাকে ঠিক করে–এই কথা, আগামবেনের মতে নতুন না। তার মতে, সার্বভৌম কে কিংবা কীভাবে সে সার্বভৌম হয়ে ওঠে এটা নিয়ে চিন্তা করা যথেষ্ট না, বরং পুরো রাজনৈতিক পরিসরের বিষয়টিকেই আমলে নিতে হবে। যা সার্বভৌমত্বের জুরিডিকাল, ইন্সটিটিউশনাল ধারার চিন্তায় করা হয় না।
১২.
ওয়াল্টার বেঞ্জামিন বুঝেছিলেন কীভাবে ব্যতিক্রম নিজেই নিয়ম হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতি আমলে নিতে আগামবেন রাষ্ট্রের গঠনের আদি উৎপত্তির যে কাঠামো সেটার দিকে নতুনভাবে নজর দিতে বলেন। নৈরাজ্যবাদী ও মার্ক্সবাদীদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, তারা এই কাঠামোটিকে গুরুত্ব না দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার যে গোপন সূত্র (acranum iperiii) তাকে অবজ্ঞা করে, যেন সিমুলাক্রা এবং আইডিওলজির বাইরে রাষ্ট্রের আর কোন সাবসট্যান্স নাই। বরং, তারা এমন এক শত্রুকে সনাক্ত করে যার কাঠামো নিজেরাই বুঝতে পারে না, এবং তাদের রাষ্ট্রতত্ত্ব এমন একটা ডুবোচর যেখানে বিপ্লবের জাহাজডুবি ঘটে। এই ডুবোচরকে আগামবেন বলেন, যা মার্ক্সিস্ট রাষ্ট্রতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়— দ্য স্টেট অব এক্সসেপশন বা প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র, যাকে দেখা হয় রাষ্ট্রহীন সমাজে অভিযাত্রার একটা ট্রান্সিশনাল পর্ব হিসেবে।
শেষে এসে আগামবেন বলেন বর্তমানে সমাজবিজ্ঞান কিংবা নৃবিজ্ঞানের যে সকল চিন্তার ক্যাটাগরি আছে সেগুলো নতুন ভাবে পর্যালোচনা ছাড়া, ক্ষমতার সঙ্গে বেয়ার লাইফের সম্পর্কের বিষয়টিকে স্পষ্ট করে বোঝা আমাদের জন্য সম্ভব হবে না।