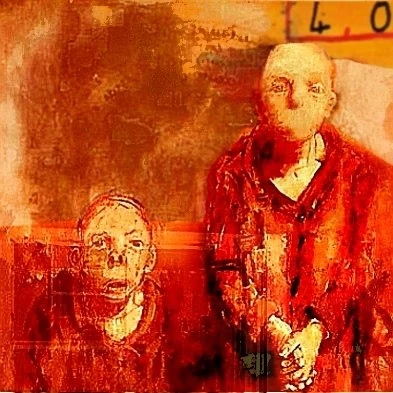- নিসর্গ নিলয়
১
আমার মতে, হেটেরোসেক্সুয়াল পুরুষদের নিজেদের নারীবাদী দাবি না করাই উত্তম। বর্তমানে লিবারেল রাজনীতির প্রভাবে এই চল আমরা বৈশ্বিক উত্তরের সমাজে দেখি। যদি ধরে নেই নারীবাদ একটি প্রয়োজনীয় দার্শনিক ও রাজনৈতিক ধারা, তবে তিনটি কারণে এই প্রবণতা থেকে দূরে থাকা উচিত। প্রথমত, নারীবাদের প্রয়োজনীয়তা হেটেরোসেক্সুয়াল পুরুষের তৈরি বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থাকে (heteropatriarchy) চ্যালেঞ্জ করতে গিয়েই উদ্ভূত। তাদের বিশ্বদর্শনে (ontology) যে নারী বিষয়ক ধারণা রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে সাম্যবাদী হয়ে গেছে, তা আমরা বলতে পারি না। দ্বিতীয়ত, বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষ নিজেকে নারীবাদী বলে দাবি করতে পারে, যা আদতে নারীবাদী এক্টিভিজমের জন্য ক্ষতিকর। তৃতীয়ত, নারীবাদের প্রতি সমালোচনামূলক অবস্থান নেওয়ার অনেক জায়গা রয়েছে। একটি বড় সমালোচনা হল, সমসাময়িক নারীবাদ অনেক ক্ষেত্রেই নারীবাদী দৃষ্টিকোণে পুরুষের ইতিবাচক অবস্থান কী হবে, তা বলতে পারে না।

উক্ত অবস্থান থেকে আমি বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সমসাময়িক ও পরবর্তী নারীবাদী এক্টিভিজম নিয়ে এই লেখাটি লিখছি। এই লেখাতে আমি দেখাবো, কীভাবে সমসাময়িক নারীবাদী এক্টিভিজমের প্রতি একটি পরিমার্জিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যায় এবং কেন তা জরুরী। এই লেখাতে আমি মূলত বলছি, জুলাই–গণঅভ্যুত্থান–পরবর্তী বাংলাদেশে নারীবাদী এক্টিভিজম বৈশ্বিক পরিস্থিতির তুলনায় এমন এক অনন্য অবস্থানে এসেছে যেখানে পূর্ববর্তী নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার পৃথকভাবে ভাবার এবং বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার সুযোগ এসেছে। সুতরাং, যেসকল (হেটেরোসেক্সুয়াল) পুরুষ এই নারীবাদকে সমর্থন করতে চায়, তাদের কিছু করণীয় আছে এবং আমি তার একটি প্রস্তাবনা আলাপ করছি। এই লেখার দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশের নারীবাদী এক্টিভিজমের একটি সার অবস্থা ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করেছি। তৃতীয় অংশে জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও পরবর্তী সময়ে নারীবাদী এক্টিভিস্টরা কী ধরনের সম্ভাবনা তৈরি করেছেন তা ব্যাখ্যা করেছি। চতুর্থ অংশে নারীবাদী এক্টিভিজমের সামনে উপস্থিত কিছু চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছি। পঞ্চম অংশে আমি উল্লিখিত প্রস্তাবনা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি।
২
বাংলাদেশের নারীবাদী এক্টিভিস্টদের দুইটা ধরন মূলত চোখে পড়ে। এক) শহুরে অধিকারভিত্তিক নারীবাদী, দুই) কিছুটা গ্রাম–স্বীকার–করা উন্নয়নভিত্তিক নারীবাদী। উল্লেখ্য, এর বাইরে ক্রিটিকাল ঘরানার নারীবাদী যে নেই—তা নয়। তবে, তাদেরকে ব্যক্তি হিসেবে গুণে গুণে আলাদা করা সম্ভব। যে দুটি ধরনের কথা উল্লেখ করলাম, তাদের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য থাকলেও একটা বিষয়ে খুবই মিল—পশ্চিমা নারীবাদী আন্দোলনের ধারাবাহিকতার সাথে তাদের কাজকর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ। অবশ্য স্বীকার করতেই হয়, আমাদের সবকিছুই শেখায় পশ্চিম। তবে অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের মতই নারীবাদেরও পশ্চিম থেকে বের হওয়ার চিত্র ধীরে ধীরে বাড়ছে। সে বিষয়ে পরে যাচ্ছি। এই পশ্চিমকেন্দ্রিকতার কারণে উন্নয়নভিত্তিক নারীবাদীরা মূলত ক্ষমতায়ন নিয়ে আগ্রহী ছিলেন ও আছেন বহুদিন ধরেঃ যেমন মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধ (আইনগত ক্ষমতায়ন), স্যানিটারি ন্যাপকিন ও কনডম ব্যবহার (স্বাস্থ্যগত ক্ষমতায়ন), স্কুলে যাওয়া (শিক্ষাগত ক্ষমতায়ন), ক্ষুদ্রঋণ (আর্থিক ক্ষমতায়ন) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই ক্ষমতায়নের ধারণা ধরে নিচ্ছে যে উল্লিখিত সামাজিক কাঠামোগত পরিবর্তনগুলো ঘটালে নারীরা সমাজে ক্ষমতার ভাগ পাবে।
অন্যদিকে শহুরে অধিকারভিত্তিক নারীবাদীরা নারীর দেহ–মন–ভাষা–চেতনা সম্পর্কিত অধিকারের দিকে বেশি মনোযোগী। এই অধিকারগুলো নারীর দেহ (physical body) থেকে শুরু করে রাজনীতি (political body) পর্যন্ত তরজমা করা যেতে পারে। তাদের আগ্রহের বিষয় তাই সম্মতি (মূলত যৌনসম্মতি), যৌননির্যাতন, মবিলিটি, উপস্থাপন (যেমনঃ পোশাক) ইত্যাদি। এই ধারার উল্লেখযোগ্য কিছু আন্দোলনের মধ্যে চোখে পড়ে মি–টু আন্দোলন, পোশাকের অধিকার নিয়ে বিভিন্ন আন্দোলন, ‘মেয়েরা রাত দখল কর’ আন্দোলন, কনসেন্ট সচেতনতা, ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি।
উভয় ক্ষেত্রেই কিছু এক্টিভিটি ও চিন্তাগত মিল দেখা যায়। প্রথমত, এই দুই ধরনের নারীবাদই একটা জিওপলিটিক্স অব নলেজে আক্রান্ত। খেয়াল করলে দেখা যাবে ডেভেলাপমেন্ট ইন্টারভেনশনগুলোও আমাদের স্থানীয় ধারণাপ্রসূত না, কোন না কোন ভাবে সেই ফাইভ স্টেজ অব ডেভেলাপমেন্টের পশ্চিমা ধারণারই বাহক। তেমনি, অধিকারগুলোর ধারণাও আমাদের স্থানের বিচারে আসে নাই, এগুলো পশ্চিমা অধিকারের ধারণা। প্রসঙ্গত, অনেকে এ কথা শুনলে বলতে পারেন যে, ‘পশ্চিমা ধারণার অধিকারকে সমালোচনা করার মাধ্যমে আসলে নারীর অধিকারের সার্বজনীন একটি দাবিকেই আটকে দেওয়ার চেষ্টা এটি।’ আমি মোটেও সে উদ্দেশ্যে বলছি না, বরং আমার দাবি এর বিপরীত। পশ্চিমা জেন্ডার বা যৌনতার অধিকারের ধারণা একটা কাঠামোর ভেতরে আটকানো, একটা রক্ষণশীল কলোনিয়াল সংস্কৃতির ধারক। যেমন, পশ্চিমা সেক্সুয়াল ফ্রিডমের আলোচনার মধ্যেও আমরা খুঁটে খুঁটে ভিক্টোরিয়ান মোরালিটিকে খুঁজে পাবো, যেখানে কোর্টশিপের ব্যাপারটা পুরোপুরি পুরুষকে বহন করতে হয়, এবং নারীকে নির্জীব ও বাধ্যগত (docile) অংশগ্রহণকারী হিসেবে সাংস্কৃতিকভাবে নির্মাণ করা হয়। আবার, আসিরীয়, মেক্সিকান প্রাচীন দেবদেবীদের জেন্ডার ফ্লুইডিটি পশ্চিমা কলোনিয়াল শাসকরা ধরতে পারে না। ফলত, জেন্ডার বা যৌনতার অধিকার বিষয়েও তা সীমাবদ্ধ হয়।
দ্বিতীয়ত, নারীর মাঝে যে হায়ারার্কি থাকতে পারে এবং এই হায়ারার্কির কারণে প্রান্তিক নারীর যে এসব আন্দোলন কোন কাজে আসতে না–ও পারে, সে বিষয়টি উভয় ঘরানাই এড়িয়ে যায়। যেমন, উন্নয়নভিত্তিক নারীবাদীদের ইন্টারভেনশনগুলো শহুরে আর্থসামাজিক শ্রেণীর জীবনধারণা থেকে উদ্ভূত সমস্যা–সমাধানের ধারণা থেকে প্রসূত। একটা গ্রামের মেয়ের ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ কোন সমস্যা যে থাকতে পারে, অথবা সেই ইন্টারভেনশন যে গ্রামের মেয়েটির জন্য সমাধানের বদলে নতুন জটিলতা ডেকে আনতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা তাদের প্রস্তাবনায় কম ধরা পড়ে। আবার, অধিকারভিত্তিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেসব ধ্যানধারণা ও উপায় ব্যবহার করে আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেগুলো সব শ্রেণীর মানুষের কাছে পরিষ্কার না–ও হতে পারে। তখন তা শুধু শহুরে অভিজাতের সুবিধা বজায় রাখা ছাড়া আর কিছু করে না। যেমনঃ যে মেয়ের কোন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অংশ নেওয়ার সুযোগ নেই, সে তার নির্যাতনের কথা কীভাবে মি–টু করবে তা বোধগম্য না। এছাড়া, যে নারী জানেই না যে সে নির্যাতিত হচ্ছে, তার পক্ষে এসব অধিকারের বাহাস বোঝাই সম্ভব না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর খুবই বীভৎস একটি উদাহরণের কথা আমার শোনা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের চরাঞ্চলে একাডেমিক কাজে যাওয়া আমার এক অগ্রজের কাছে শুনেছিলাম, সেখানে ধর্ষণ বলে কোন ধারণাই নেই। সেখানে একে বলা হয় ‘জোর করা’। মেয়েদের সাথে এই ‘জোর করা’ হলে তার তেমন কিছু করার নাই, বড়জোর সালিশ ডেকে বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হয়। এই শব্দবন্ধ প্রমাণ করে যে, সেখানকার নারীর জীবনধারণায় এই ‘জোর করা’ প্রসঙ্গটি ‘মেনে নেওয়ার’ বিষয়, সেখানে ‘নির্যাতনের’ ধারণাটি তর্কসাপেক্ষে অনুপস্থিত।
তৃতীয়ত, উভয় ক্ষেত্রেই হেটেরোপ্যাট্রিয়ার্কি এবং কর্তৃত্ববাদের চূড়ান্ত রূপ তথা রাষ্ট্রের সাথে নারীবাদী এক্টিভিজমের কোন বিরোধ নেই। উল্লিখিত এক্টিভিজমে অংশ নিয়েও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদের পক্ষে থাকা যায়। যেমন: আওয়ামী কর্তৃত্ববাদী সরকার যখন ’নারীর ক্ষমতায়ন’–কে প্রচার করে, তখন তার পক্ষে থেকে রাষ্ট্রের সঙ্গে নারীমুক্তির পথের বিরোধকে এড়িয়ে যাওয়া যায়। গত ১৫ বছরের ঘটনা আমলে নিলে এটি ভালো উদাহরণ। সুতরাং, এরকম পরিস্থিতিতে নারীবাদী এক্টিভিস্টরা কর্তৃত্ববিরোধী গোষ্ঠী দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হবেন এটা স্বাভাবিক। সেটা হয়েছেনও। তবে এসব বিরোধের মোড় ঘুরিয়ে ঐতিহাসিক একটি অধ্যায় সূচনা করেছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান।
৩
স্পষ্টত, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে দেশের কোন নির্দিষ্ট সংগঠন, দল বা সংস্থা নয়, বরং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী সরকারের পতন ঘটে। এতে রাষ্ট্রকাঠামোর কোন পরিবর্তন না ঘটলেও অবশ্যই তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এসময়ে নারীবাদীদেরকেও কোন একটা পক্ষ নিতে হতো, এবং তারা তা নিয়েছেন। ঘরানাগত পার্থক্য, এক্টিভিজমগত পার্থক্যের বেড়া পার করে তাদের সামনে বিশাল প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছিল, তারা কি রাষ্ট্রীয়–সরকারি কর্তৃত্ববাদের পক্ষে না বিপক্ষে? উল্লেখ্য, অধিকাংশ নারীবাদীই এসময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন গণঅভ্যুত্থানের বড় একটি শক্তি হিসেবে। গণঅভ্যুত্থানের একটি বিখ্যাত ছবি আছে। কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট দিয়ে লাঠি হাতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিলে বের হচ্ছেন এক হিজাব পরিহিতা (যাকে ইসলামিক চিন্তাধারার প্রতীক হিসেবে অনেকে বিবেচনা করেন) এবং এক প্যাণ্ট–শার্ট পরা (যাকে লিবারেল–মডার্ন চিন্তাধারার প্রতীক হিসেবে অনেকে বিবেচনা করেন) তরুণী। জুলাই গণঅভ্যুত্থান তাদের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি, জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশী নারীবাদীদের অবস্থানকে আরও রাজনৈতিক করেছে। রাজনীতির ময়দানে কর্তৃত্ববাদবিরোধী নারীবাদীদের নতুন একটি অবস্থান তৈরি করেছে। যে নারীবাদীরা আওয়ামী সরকারের পক্ষ নিয়েছেন, তাদের আওয়ামীলীগকে বাঁচাতে গিয়ে নারীবাদী অবস্থানের বদলে কর্তৃত্ববাদী বয়ানেই ব্যস্ত হয়ে যেতে হবে। ফলে তারা যে আদতে নারীর জীবন–দর্শন–রাজনীতির চিন্তায় চিন্তিত নয় বরং রাষ্ট্রীয় এপারেটাসের মোলায়েম অংশ মাত্র, সেটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে মুনমুন শারমিন শামস, তসলিমা নাসরীন প্রমুখের সাম্প্রতিক বক্তব্যগুলোকে আমলে নেওয়া যায়।
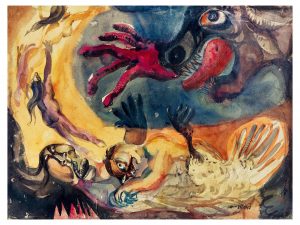
এই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের ফলে নারীবাদী এক্টিভিস্টরা পূর্বে উল্লিখিত সংকটগুলি ছাড়াও উন্নয়নভিত্তিক নারীবাদীদের প্রথাগত রৈখিক উন্নয়নের বয়ান এবং অধিকারভিত্তিক নারীবাদীদের শহরকেন্দ্রিকতা থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ পেয়েছেন। উন্নয়নের ধারণা যে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রযন্ত্র নির্ধারণ করে তা এখন জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী এক্টিভিস্টদের কথায় বারবার উঠে আসছে। তারা হয়ত ভবিষ্যতে এধরনের উন্নয়নকে আরও কাটাছেঁড়া করে পর্যালোচনা করবার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলন এখন শুধু শহুরে নারীর জীবনে সীমাবদ্ধ থাকবে না বলে আশা করা যায়।
৪
দুর্ভাগ্যের বিষয়, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামো যেমন রাতারাতি কৃষক–শ্রমিকবান্ধব হয়ে যায়নি, তেমনি নারীদের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা কিংবা মুক্তিও ডেকে আনেনি। সদ্য শেষ হওয়া ঈদুল ফিতরে আমরা দেখতে পেলাম দীর্ঘদিন ধরে বেতন না পাওয়া গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলন। একইভাবে, নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্দোলন চলমান। এর কোন রাজনৈতিক সমাধানের বা সমঝোতার পথে পৌঁছাতে আমরা পারিনি। আরও ভীতিকর বিষয়, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারীদের অংশগ্রহণের বিভিন্ন বয়ান লুপ্তপ্রায়। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীদের অংশগ্রহণের ন্যারেটিভ এবং গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অংশগ্রহণ হারিয়ে গেছে কিংবা দাবিয়ে রাখা হয়েছে বলে অনেক নারী গণঅভ্যুত্থানকারী অভিযোগ করেন। এছাড়া, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বাইরে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারীদের অংশগ্রহণের অনেক আখ্যান রয়েছে যেগুলো হয়ত উপযুক্ত অন্বেষণের অভাবে অব্যক্তই থেকে যাবে। একটা ছোট্ট ঘটনা আমার চোখে পড়েছিল। সেটা স্মৃতি থেকে লিখছি। কোন এক মেয়ের একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস ছিল অনেকটা এরকমঃ জুলাইয়ের সময় তিনি ঘরে বসে বসে দেখছেন তাঁর ছাত্রলীগ দেবর বাসার সবাইকে হুমকিধামকি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে আন্দোলনে যাওয়া যাবে না। মেয়েটি আরও সন্দেহ করছিলেন যে দেবর নিশ্চয়ই ছাত্রদের উপর হামলায় অংশগ্রহণ করছেন নিয়মিত। তাই তিনি সেদিন দেবরের রাতের খাবারের সাথে জামালগোটা (ল্যাক্সেটিভ) মিশিয়ে দেন। পরেরদিন দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখেন যে দেবর বাসা থেকে বের হচ্ছে না ‘শরীর খারাপ’ বলে। এতে তিনি বেজায় আমোদিত হন। এই ঘটনায় মেয়েটি সরাসরি রাস্তায় নেমে যুদ্ধ না করেও একজন যোদ্ধা। কিন্তু রাস্তার ময়দানে যতটুকু ডকুমেন্টেশন ছিল, এইধরনের আখ্যানের তত ডকুমেন্টেশন আমরা করে উঠতে পারিনি, বা পারব না।
এছাড়া, বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী ক্ষমতা পুনর্গঠনের অলিখিত সমঝোতার স্বার্থে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারীবাদী এক্টিভিস্টদের সরাসরি বিরোধিতা করেনি। এক্ষেত্রে ডানপন্থী রক্ষণশীল, বিশেষ করে ইসলামিস্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর কথা উল্লেখ করবো। এসব গোষ্ঠী সরাসরি নারীর অধিকার ও এজেন্সিকে অস্বীকার করে, নারীবাদের কথা তো বলা বাহুল্য। গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই এসব গোষ্ঠীগুলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভাগ বসাচ্ছে, বা বসানোর জন্য সমঝোতা করছে। ফলত, এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো নারীবাদী এক্টিভিস্ট এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারীর অংশগ্রহণকে যতভাবে সম্ভব ততভাবে বিস্মৃত করবার চেষ্টা করছে। এই চেষ্টার প্রতিফলন হিসেবে আমরা নারী অধিকার সম্পর্কিত নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনার বিরোধিতা করতে দেখি। আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনগুলোয় নারী নেতৃত্ব উঠে আসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে দেখি– ব্যক্তিগত জীবনের সমালোচনা, চরিত্রহনন বা চিরাচরিত ‘নারী নেতৃত্ব ভালো নয়’ আলাপের মধ্য দিয়ে।
৫
এমতাবস্থায় জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশি নারীবাদী এক্টিভিস্টদের জন্য যে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। একটি হেটেরোপ্যাট্রিয়ার্কাল সামাজিক অবস্থায় নারীবাদী এক্টিভিস্টদের সহযোদ্ধা ও সমর্থক হিসেবে আমাদের মত পুরুষদের করণীয় কী? এক্ষেত্রে আমি চারটি কাজসংবলিত একটি প্রস্তাবনা দিচ্ছি। এই চারটি কাজ হলো উপলব্ধি (realization), দালিলিক প্রমাণ সংরক্ষণ (documentation), যোগাযোগ (communication) এবং সমন্বিতকরণ (integration)।
প্রথমত, সাংস্কৃতিক, জৈবিক ও মানসিক গড়নে স্বকীয়তা থাকলেও পুরুষ হিসেবে আমরা নারীর থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বাইনারি পোল না। নারী দৈহিক এবং ধারণাগতভাবে আমাদের আত্ম ও সমষ্টির অংশ। অথচ পুরুষ হিসেবে আমরা নারীকে বুঝে ওঠার কতটা চেষ্টা করি সেটা প্রশ্নের বিষয়। কেননা, হেটেরোপ্যাট্রিয়ার্কাল সমাজ আমাদের এই বাইনারি বজায় রাখতে উৎসাহিত করে। ফলে নারীর ভাষা, নারীর মনস্তত্ব এবং নারীর সামাজিক–রাজনৈতিক লড়াই আমরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই। নারীর বিশ্বদর্শন বুঝতে গেলে আমাদের এই ধারণাগত বাইনারি থেকে বের হতে হবে। এই কাজটি করতে গেলে পুরুষ হিসেবে আমাদের নিজেদের মনস্তত্ব বোঝার সুযোগ এবং কর্তব্য রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, গণঅভ্যুত্থানে নারীর অংশগ্রহণ, বয়ান, রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদির দালিলিক প্রমাণ সংরক্ষণ জরুরি, যার কারণ আগেই উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব এড়াতে বিভিন্ন পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করতে পারি, যেমনঃ থিক ডেস্ক্রিপশন, ডায়ালগ, টেক্সচুয়াল বিশ্লেষণ ইত্যাদি।
তৃতীয়ত, উপলব্ধির অভাবের কারণে আমরা অধিকাংশ সময়ে নারীর সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হই। ঘরে মা–বোন থাকা সংক্রান্ত বিভিন্ন বুলি ছাড়লেও (যা হেটেরোপ্যাট্রিয়ার্কিকেই পুনরুৎপাদন করে), আমরা কতটুকুই বা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি? কতটুকু বা আমরা শুনি মায়ের দুঃখ, প্রেমিকার অনুভূতি? আরও বড় পরিসরে চিন্তা করলে– কতটুকু যোগাযোগ আমরা স্থাপন করতে পেরেছি নারীবাদী এক্টিভিজমের সাথে, তাদের অবস্থা ও অবস্থানের আলোচনার সাথে? নারীবাদের প্রতি সমালোচনামূলক আলোচনায় থেকেও সেই যোগাযোগ করতে কী বাধা আছে? সেটা আমরা যতক্ষণ না এক্টিভিস্টদের সাথে আমাদের যোগাযোগ বাড়িয়ে তাদের কথা শোনার চেষ্টা করি, ততক্ষণ জানা সম্ভব না।
চতুর্থত, এই যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীবাদী এক্টিভিস্টদের সঙ্গে সমন্বয়সাধন বাড়ানো যায়। প্রথাগত এক্টিভিজমের বাইরে নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনলাইন ইভেন্ট, লেখালেখি ইত্যাদি কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এক্টিভিস্টদের এসকল আয়োজনে অংশগ্রহণ করা যায়। তাদের সঙ্গে মতামত না মিললেও– সেখানে তারা কী বলতে চান, কার্যক্রমগুলো কেমন বা তার ভালো দিক কিংবা সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী– সেগুলো ভাবা যায়। এসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক তৈরি করা সম্ভব।
প্রশ্ন হলো, আমার মত অবস্থান থেকে যারা এসবে আগ্রহী হবেন তাদেরকে নারীবাদী এক্টিভিস্টরা মেনে নিবেন কিনা? বাংলাদেশে ‘নিঃস্বার্থ’ ও ‘প্রভু–দল–সংগঠন–ভক্ত’ রাজনৈতিক এক্টিভিজমের যে প্রচলন, তা থেকে তারা যে মুক্ত– এ কথা তো সহজে বলার মত যথেষ্ট তথ্য উপাত্ত নেই। তারা আমাদের কতটুকু গ্রহণ করবেন? এ দায়ভার নারীবাদীদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।