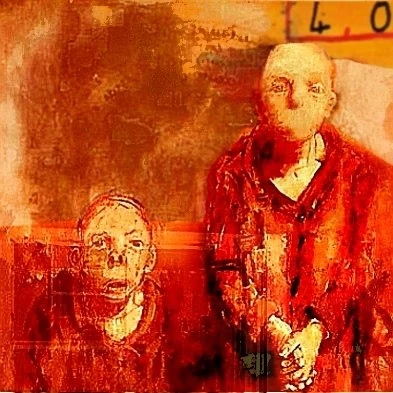- অনুবাদ: তানিয়াহ্ মাহমুদা তিন্নি

ফ্যাসিবাদীরা ইতালি এবং জার্মানিতে রক্তপাতহীনভাবে বিপ্লবের দাবি করে। তবে প্রাপ্ত নথি কেবল এ দুটি দেশের নয় বরং আরও অনেকগুলো দেশের ক্ষেত্রেই তাদের এই ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন করে। তবে যাই হোক, এই দেশগুলোতে ‘অতিমানবের’’ উত্থানের পেছনের গল্প পাঠকদের জন্য চিন্তা উদ্রেগকারী হতে পারে।
ইতালিতে মুসোলিনি বিজয়ী জনপ্রিয় সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি হিসেবে রোম দখলের পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে নি। রোম দখলের যাত্রা মঞ্চস্থ হওয়ার সময় ইতিহাসের এই ‘নায়ক’ নিজেকে অনেক দূরে সুরক্ষিত রেখেছিল। তার অর্থের জোগানদার ছিল সেসময়ের পুঁজিবাদীরা। পুঁজিবাদীদের অফুরন্ত অর্থের সাহায্যে সে ভাড়াটে কালো শার্ট বাহিনী জড় করে যারা বিপ্লবী মজুর এবং কৃষকদের বিরুদ্ধে অসংখ্য সন্ত্রাসী হামলা পরিচালনা করে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উদারনৈতিক, কিন্তু দুর্বল ও আতঙ্কিত বুর্জোয়া সরকারের হাত থেকে কালো-শার্টধারী ভাড়াটে সৈন্যরা ক্ষমতা দখল করতে পারেনি। বরং নিয়মিত সৈন্যরাই, মুসলিনিকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। কারণ মুসলিনিই নিজেকে বিপ্লবী গণআন্দোলনের সবথেকে ভয়ঙ্কর এবং নির্মম শত্রু হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। নিয়মিত সেনাদের কাছ থেকে সম্মতি লাভের পরই কেবল রোমের উদ্দেশ্যে ফ্যাসিবাদীদের পদযাত্রা শুরু হয়। নিয়মিত সেনারা যদি ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত তাহলে হয়ত কখনোই এই ‘রক্তপাতহীন বিপ্লব’ সংঘটিত হত না। ইতালির জনগনকেও মুসলিনির মতো একনায়কের শাসনের মত দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হত না।
উদারনৈতিক বুর্জোয়া সরকার বিপ্লবী পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ ছিল। ফলে শোষক শ্রেণি—বিশেষত ভূস্বামী এবং পুঁজিবাদী—এই দুই দল বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করতে পুরাতন সরকারকে নতুন আরেকটি দক্ষ সরকার দ্বারা প্রতিস্থাপিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একইসাথে তারা এমন একটি সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছিল যারা শাসক শ্রেণির আরও বেশি অধীনস্ত হয়। নিয়মিত সৈন্যরা তাদের নিজেদের লোকের তত্ত্বাবধানেই ছিল। কিন্তু একটি বিপ্লবী পরিস্থিতিতে সাধারণ সৈনিকদের উপর ভরসা করা যায় না। এ কারণেই নিয়মিত সৈনিকদের উপর একটি জনপ্রিয় বিপ্লবী আন্দোলন দমনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ নির্ভরযোগ্য ছিল না। জনগনের কিছু অংশ অবশ্যই প্রতিবিপ্লবী হয়ে উঠতে পারে। ছদ্ম-সিন্ডিকালিস্ট প্রোপাগাণ্ডা এবং জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেম ফ্যাসিবাদের উদ্দেশ্যই পূরণ করছিল। মধ্যবিত্ত বিদ্রোহী এবং প্রান্তিক শ্রমিকেরা মুসলিনির ভাড়াটে কালো-পোশাকের সৈন্যদের তালিকাভুক্ত ছিল। মুসলিনিকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছিল কারণ প্রতি-বিপ্লব জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সম্ভবনা ছিল। অবশ্যই, সে তার ‘সুপারম্যান’ ইমেজ দ্বারা কোন নোংরা কাজ করাতে আগ্রহী ছিল না। এই কাজের জন্য তো নিয়মিত সৈন্যদেরকেই মজুত রাখা হয়েছিল।
সেই পরিস্থিতিতেই মুসোলিনির পক্ষে ‘ক্ষমতা দখল’ করা সম্ভব হয়েছিল। তখন থেকেই নিয়মিত সেনারা তার রক্ষা এবং পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে, কখনও কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় নি। ক্ষমতা তাঁর পায়ে এসে লুটিয়ে পড়েছে। তবুও শেষ সময়ে এসে প্রচণ্ড ভীতিকর পরিস্থিতিতে পড়েছিল। রোমের পথে পদযাত্রার সময়ও সে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব প্রদানের ঝুঁকি নেয়নি। যখন মহানায়কের বীরত্বগাঁথা মঞ্চস্থ হচ্ছিল তখনও নায়ক মিলানে শান্তিতে ঘুমাচ্ছিলেন। রোম দখলের পর, তাঁর বিশ্বস্ত কিছু লেফটেন্যান্ট টেলিফোনে তাকে সুসংবাদ দেয় এবং দৃশ্যপটে আবির্ভূত হতে বলে। এমনকি তখনও সে নিজেকে ঝুঁকিতে ফেলতে আগ্রহী ছিল না। আসলে সে কোন অলৌকিকতায় বিশ্বাসী ছিল না। অবশেষে, জেনারেল স্টাফের কাছ থেকে খবর পাওয়ার পরই কেবল সে রোমজয়ী হিসেবে একটি ঘুমন্ত গাড়িতে করে পদযাত্রায় অংশ নেয়।
তখন পর্যন্ত বিপ্লব রক্তপাতহীন ছিল। কিন্তু এই করুণ-কৌতুকের পটভূমি যথেষ্ট রক্তাক্ত ছিল। হাজারো শ্রমিক গণহত্যার সম্মুখীন হয়েছিল। শ্রমিকরা সহিংসতা শুরু করেনি। তারা কেবল কাজ হারিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করেছিল। কারণ পর্যাপ্ত লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে ফ্যাক্টরি মালিকেরা কারখানা বন্ধ করে দেয়। শান্তিপূর্ণভাবে ফ্যাক্টরি চালাতে দিলেই বরং সত্যিকারের রক্তপাতহীন বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হত। সেটা করতে দেওয়া হয়নি। বরং শ্রমিকদের উপর সংঘটিত সহিংসতা চালানো হচ্ছিলো যা এমনকি দেশের প্রতিষ্ঠিত আইন কানুনের খেলাপ। শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বাঁধা দেওয়া হচ্ছিল, যা কিনা পুঁজিবাদীরাও করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা দেশের কারখানার চাকা চলমান রাখতে চেয়েছিল যাতে শ্রমিকদের জীবিকা অর্জনের উপায় থাকে। তাহলে হয়ত দেশের অর্থনীতিও পঙ্গু হয়ে পড়বে না।
ক্ষমতা গ্রহণের পর মুসোলিনি নতুন রাজত্বে সকল ভিন্নমত দমনের উদ্দেশ্যে গণহারে সহিংসতা চালায়। ফ্যাসিবাদের বিজয়কে কোনভাবেই বিপ্লব তো বলা যাবেই না, এমনকি তা রক্তপাতহীনও নয়। এটি পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত শাসন ব্যবস্থার থেকে কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। সেকারণেই সব সময় রক্ত ঝরানোর প্রয়োজন নাও হতে পারে। অন্যদিকে বিপ্লবী জনগণের প্রতিরোধ ছিল নিরস্ত্র। ফলে সহিংসতা ঘটানোর জন্য অনেক রক্তপাতের প্রয়োজনই হয়নি। কিন্তু অসংখ্য নারী-পুরুষকে সারা জীবনের জন্য জেলে বন্দী করা তলোয়ারের আঘাতে রক্তাক্ত করার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। পাশাপাশি, জনসাধারণের একটি অংশের কথাও মাথায় রাখা জরুরি যারা হত্যা এবং গণহত্যার শিকার হয়েছেন।
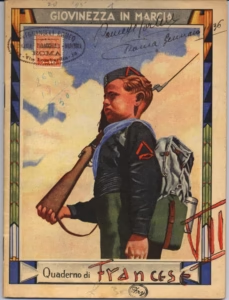
এবার জার্মানির প্রসঙ্গে কথা বলা যাক। হিটলার ‘সাংবিধানিকভাবে’ ক্ষমতায় এসেছেন এই ভ্রান্তি দূর করা দরকার। কিংবদন্তি চরিত্র সম্পর্কে এ ধরনের বয়ান স্বাভাবিক। প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান উচ্ছেদ করার মধ্য দিয়ে হিটলারের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করা হয়েছিল। সে সংবিধান লঙ্ঘন করেনি। তার কর্মচারী এবং পৃষ্ঠপোষকেরা তার জন্য এ কাজটি করেছিল। সে ওয়েইমার সংবিধানকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিজের ক্ষমতা গ্রহণকে উদযাপন করেছিল। যা কিনা ইতোমধ্যেই জুনকার-মিলিটারিস্ট পল ভন হিন্ডেনবার্গ পরিচালিত ‘রিপাবলিকান সরকার’ ধ্বংস করেছিল। জার্মানিতেই ইতালির মতোই পুঁজিবাদীদের মদদপুষ্ট অর্থপ্রাপ্ত এজেন্টদের দ্বারা ফ্যাসিবাদী শক্তি ক্ষমতায় আসে। ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত শাসকদের বিনা প্রতিরোধেই তারা সফল হয়। তারা যে জনপ্রিয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল তা রাষ্ট্রীয় দমননীতির দ্বারা মুখ থুবড়ে পড়ে এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম করে। ক্ষমতায় যাওয়ার এই পন্থার সঙ্গে সহিংসতার গল্প জড়িয়ে রয়েছে। এই সহিংসতা তারা ঘটিয়েছে যারা ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত শাসকদের শত্রু হিসেবে স্বীকৃত, শুধুমাত্র তাদের সাথে যোগসাজশই নয়, বরং তাদের থেকে প্রকৃত সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।
হিটলার নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিজয়ী হয়ে সরকার প্রধান হয়। ফলে, সে ছিল জনগণের পছন্দ। সে ক্ষমতায় এসেছে ‘জনপ্রিয় সমর্থন’ পেয়ে। এই সত্য কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? এর ব্যাখ্যা পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ভেতরেই রয়েছে। হিটলারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে ১৯৩৩ সালে যে নির্বাচন হয়েছে তা লজ্জাজনক একটি ঘটনা। সে ইতোমধ্যেই হিন্ডেনবার্গের অনুগ্রহে চ্যান্সেলর হয়েছিল, যা কিনা জার্মানির সামরিকতন্ত্রী শাসকের প্রতিনিধিত্বকারী। ফলে এই মহানায়ক এমন সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন যেখান থেকে তিনি সুকৌশলে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পথ তৈরি করতে সক্ষম ছিলেন। তারপরেও সে পরাজিত হয়েছিল।
একমাত্র বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল দুটো শ্রমিক পার্টি। এই দুই পার্টি সম্মিলিতভাবে আগের নির্বাচনে প্রায় ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এই দুই দলকেই ‘আইনি’ দমন এবং বেআইনি সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী মাঠ থেকে উধাও করার পরই নতুনভাবে আবার নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তখনও ‘সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক’ পার্টিকে নামেমাত্র টিকিয়ে রাখা হয়েছিল এবং কাজ করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিকে পুরোপুরি দমন করা হয়েছিল। এটা সে সময় ঐ দেশের তৃতীয় বৃহত্তম পার্টি যাদের সংসদে ১০০টির মত সিট ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির উপর দমনপীড়ন এটাই প্রমাণ করে যে ফ্যাসিস্টদের ‘গণতান্ত্রিক বিজয়’ মঞ্চস্থ করতে গেলে তার পূর্বেই গণতন্ত্র ধ্বংস করতে হবে। সেসময়কার গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিস্ট নেতাদের প্রত্যেকে ছিলেন হয় জেলে, নয়তো লুকিয়ে। এই দলের সদস্যরা ফ্যাসিবাদীদের ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের সম্মুখীন হয়েছিল। এমনকি সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্যরাও সমান আতঙ্কিত ছিল। পোলিং বুথগুলো ফ্যাসিবাদী গুণ্ডাদের নজরদারির আওতায় ছিল। ফলে, সাধারণ মানুষের জন্য কমিউনিস্ট কিংবা সোশ্যালিস্ট যে কোন পার্টিকে ভোট প্রদানই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। অনেকে ভোটই দেন নি; অনেকে নিজের পছন্দের দলকে ভোট দিতে পারেন নি। যারা ফ্যাসিবাদিদের ভোট দিয়েছেন তাদের অনেকেই চাপের মুখে বা ভয়ে ভোট দিয়েছেন। অসংখ্য কমিউনিস্ট ভোট দিতে যেতে পারেন নি কারণ তারা লুকিয়ে ছিলেন। অন্যদিকে যারা হিটলারকে ভোট দিতে চাচ্ছিলেন না তাদেরকে নাৎসি সৈন্যবাহিনীর সদস্যরা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। বিরোধীদলীয় পত্রিকাগুলোকে দমন করা হচ্ছিল, তাদের প্রচারমূলক লেখাপত্র বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছিল, তাদের সভাগুলো ভাড়াটে গুন্ডার দ্বারা পণ্ড করে দেওয়া হচ্ছিল, তাদের সমর্থকদের নিজের পছন্দে ভোট দেওয়া আটকানো হচ্ছিল অথবা ভোটে বিরত রাখার চেষ্টা করা হচ্ছিল। পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থাই যেন ফ্যাসিবাদের প্রচারণা যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল।
এমতাবস্থায় একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। এই পরিবেশে অনুষ্ঠিত ‘নির্বাচনের’ ফলাফল কোনভাবেই জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায় না। এরকম লজ্জাজনক নির্বাচনও হিটলার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পায়নি। ফ্যাসিবাদীরা ৪০ শতাংশের বেশি ভোট পায় নি। এই ফলাফল আবারও সকল ভোটারদের একটি ক্ষুদ্র অংশেরই কেবল প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে ভোটারদের একটি বড় অংশই কেন ভোট দিতে পারে নি।
অন্যদিকে সীমাহীন নিপীড়ন, কঠোর পরিশ্রম, নানা প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করেও কমিউনিস্ট পার্টি সংসদে পূর্বের ১০০টির থেকে ৮০টি সিটে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ কারণে, এই বিজয়কে প্রকৃত বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় ভোট হলে তারা অনেক বেশি ভোট পেতে পারত। এ থেকে প্রমাণিত হয়, সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হিটলারের ভাগ্যে অসম্মানজনক পরাজয়েরই সম্ভবনা বেশি। তুলনামূলক স্বাধীনতায়ও কমিউনিস্ট পার্টি যে অসাধ্য সাধন করেছে তা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য, এই অসম প্রতিযোগিতায় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিও আগের থেকে ভাল ফল করেছিল। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি, সোশ্যাল-ডেমক্র্যাট এবং অন্যান্য ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছোট কতক দল মিলে নতুন সংসদের প্রায় অর্ধেক আসনে বিজয়ী হয়। বিজয়ীরা এরকম সংসদের মুখোমুখি হতে চায়নি। ফলে নতুন উদ্যমে আরও সহিংস পথ তারা বেছে নেয় ভিন্নমত দমন করতে। গণতন্ত্রের সর্বশেষ চিহ্ন বাতিল করে ‘সাংবিধানিক একনায়কত্বের’ পথ বেছে নেয়। সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত ৮০ জন জনপ্রতিনিধিকে সংসদে অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই ৮০ জন জনপ্রতিনিধি এমন ৪০ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছিল যারা সংগঠিত সন্ত্রাস মোকাবিলা করেও ভোট দিয়েছিল। আরও অনেকে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এই প্রতিনিধিদের ভোট দিতে পারেন নি। সোশ্যাল ডেমক্র্যাটদের একটা বড় অংশের প্রতিনিধিরাও নিপীড়ন থেকে বাঁচতে নিজেদের সংসদে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত রেখেছিল। ফলে যে সংসদ হিটলারকে একনায়ক ক্ষমতা প্রদান করেছিল তা ৭০ শতাংশেরও বেশি নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করে না। এমনকি নির্বাচকমণ্ডলীর যে একটি অংশ ফিরে এসেছিল তাদের অনেকেই হিটলারকে ভোট দেয়নি। ফলে, ফ্যাসিস্টরা তখনই ক্ষমতায় এসেছিল যখন কিনা তারা কোনভাবেই ৩৫ শতাংশ নির্বাচক মণ্ডলীর ভোট পায়নি। এটিই হিটলারের কাল্পনিক ‘সাংবিধানিক’-ভাবে ক্ষমতায় আসার সত্য উদঘাটন করে।
হিটলারের কাল্পনিক ‘সাংবিধানিক’ বিজয়ের সত্য আরও একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে উঠে আসে। ১৯২৮ সালের পর থেকেই নির্বাচনে ফ্যাসিস্টদের ভোট ক্রমাগত লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। কিন্তু হিটলারের ‘সাংবিধানিক একনায়কত্ব’ লাভের মাত্র কয়েক মাস আগের নির্বাচনে ফ্যাসিবাদীরা একটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হন। হঠাৎ করেই নাৎসিরা প্রায় বিশ লাখ কম ভোট পায়। এটি স্পষ্ট প্রমাণ করে কৃত্রিমভাবে শক্তিশালী করা আন্দোলন তার চূড়ান্তে রূপ লাভ করেছে এবং খাদের কিনারে পৌঁছে গেছে। অপেক্ষাকৃত প্রান্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণিও ফ্যাসিস্টদের প্রতি তাদের বিশ্বাস হারানো শুরু করেছে। তারা নাৎসিদের মিথ্যাচার এবং ধাপ্পাবাজি ধরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। পূর্ববর্তী নির্বাচনে নাৎসিরা বেশ কিছু প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়েছে। তারা মন্ত্রাণালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর ভোটারদের প্রতিশ্রুত সেবা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। অনুসরণীয় নেতাদের আত্মবিশ্বাসে ভাটা পড়েছে, পৃষ্ঠপোষকদের সহযোগিতা না পেলে চলমান আন্দোলন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে তারা এবং তাদের বেশি কথা বলা লেফট্যান্যান্টরা সমস্যা সমাধানের কোন উদ্যোগ নিতে পারছে না, অন্যদিকে বিপ্লবী শ্রমজীবীরা রাস্তায়। ফলে বুর্জোয়া বুঝতে পারে এখনি সময় তাদের নায়কদের ক্ষমতা থেকে ছুড়ে ফেলার।
বৃদ্ধ হিন্ডেনবার্গকে নির্দেশনা দেওয়া হয় তাঁর সমস্ত বংশ মর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে এমন একজনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে যে কিনা নির্বাচনে খুব বেশি ভাল করতে পারেনি, এমনকি সংসদেও খুব অল্প সংখ্যক আসনের প্রতিনিধিত্ব করছে। হিটলারের ক্ষমতায় আবির্ভাব নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জনগণের সমর্থনের মধ্য দিয়ে ঘটেনি, বরং একজন উদ্ধত ফিল্ড মার্শালের ইচ্ছায় ‘শঠ বোহেমিয়ান ড্রিল সার্জেন্টের’ অনিচ্ছাকৃত অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে ঘটেছে। অতঃপর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করে অধিকাংশের রায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে সে ক্ষমতায় গিয়েছে। হিটলার নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার নাটক মঞ্চস্থ করতে সকল ধরনের বৈধ এবং অবৈধ নিপীড়ন কৌশল ব্যবহার করেছেন। সভ্যতার ইতিহাসের সবথেকে ভয়াবহ কাজ রাজনৈতিক কারণে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়েছে সে। এই অগ্নিসংযোগ ঘটানো হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্মূল করার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য একটি প্রেক্ষাপট তৈরি করতে। কারণ সেসময় কমিউনিস্ট পার্টিই একমাত্র সংগঠিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম ছিল। নাৎসিরা রাইখস্টয়াগ ভবন পুড়িয়ে দেয়।১ অগ্নিসংযোগের এই ঘটনাটিই ছিল ‘রক্তপাতহীন বিপ্লবের’ সূচনা সংকেত।
হিটলার রাইখস্ট্যাগ পোড়ানোর ঘটনাকে ঈশ্বরের ইশারা হিসেবে স্বাগত জানিয়েছিল। ঐশ্বরিক অনুমোদনের মাধ্যমে সকল ভিন্নমত দমন করেছিল। তারপরেও, অধিকাংশ মানুষ তাকে ভোট দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ঈশ্বর হয়ত এই আধুনিক মোজেসকে সাহায্য না করতেও পারতেন, কিন্তু বুর্জোয়ারা তাদের নায়ককে মহিমান্বিত করতে পাশে ছিল। তাদের কৌশল হিসেবে যে কোন উপায়ে হিটলারকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করতে চেয়েছিল যাতে করে সে তার প্রতি অর্পিত নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনা করতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত সহিংসতার মধ্য দিয়ে ‘রক্তপাতহীন বিপ্লব’ আনা হয়েছিল এবং তার ফলাফল ছিল সবথেকে রক্তক্ষয়ী। বুর্জোয়া পৃষ্ঠপোষকতায় স্বৈরাচারী ক্ষমতা বাড়িয়ে পূর্বসূরি ইতালির মুসলিনির মতোই হিটলার তার প্রভুদের মর্জিমত চলা শুরু করে।
‘রক্তপাতহীন বিপ্লব’ মানবজাতির মহৎ অর্জন ধ্বংস করতে সংকল্পবদ্ধ ছিল। “জার্মানি একটি দুর্দান্ত এবং অবিশ্বাস্য মাত্রায় একটি ভয়ঙ্কর উদাহরণ তৈরি করছে। বিংশ শতাব্দীর জার্মানির জাতীয় সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা রক্ষার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত শিক্ষামূলক পরিবেশনার সমান্তরাল হিসেবে প্রাথমিক মধ্যযুগীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হবে”। (Robert Briffault, “The Nationalist Crazee in Culture” in the Curent History”, New York, August 1933)। একইরকমভাবে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আরেকজন বিশিষ্ট চিন্তক লিখেছেন: “সকল বিদেশি সমালোচক ফ্যাসিস্ট ইতালির অনন্য শিল্পকর্ম এবং সাহিত্যের বন্ধাত্ব নিয়ে মত প্রকাশ করেছেন”।
আধুনিক সংস্কৃতির প্রতি ফ্যাসিবাদের শ্ত্রুতা এক কথায় হিংস্র। এটি নিছক বর্বরতার দিকে ধাবিত হওয়াকেই প্রতিনিধিত্ব করে। ফ্যাসিবাদের এই চরিত্র সভ্য সমাজে চরম বিরক্তির উদ্রেক ঘটায়। এটি এমনকি তাদেরকেও হতবাক করে যারা কিনা ফ্যাসিবাদের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারেও আপত্তি জানায় না, যেমন- শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রতিহত করতে সীমাহীন সহিংসতা ঘটানো। পুঁজিবাদের নড়বড়ে কাঠামোকে মজবুত করতে এই সহিংসতাগুলোই ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল।
যারা নিজেদের ‘অতিমানব’ রূপে উপস্থাপন করে রক্তপাতহীন বিপ্লব সাধনের অলৌকিক কৃতিত্বের দাবি করে, তাদের প্রসঙ্গে পক্ষপাতহীন প্রামাণ্য উদারপন্থী মতামত উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট।
“জার্মানি বর্তমানে মাদকাসক্ত, খুনি, চোর, জালিয়াত এবং নৈতিক স্খলনযুক্ত মানুষ দ্বারা শাসিত হচ্ছে। নিছক গালাগাল করার জন্য এই পরিভাষাগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে না; এগুলো বরং নাৎসি আন্দোলনের বেশিরভাগ নেতৃবৃন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দ।” (“The Nation”, New York, August 2, 1933).
“অপরাধের মাত্রা এত বেড়ে গিয়েছিল যে প্রতিরোধ করাও সম্ভব হচ্ছিল না। সভ্য মানুষ অবিশ্বাসে হতবাক হয়ে পড়েছিল। লাখো জার্মানির পরিণতি কল্পনা করাও দুষ্কর, যারা কিনা এই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উন্মাদনার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অতি সভ্য ও অতি বুদ্ধিমান ছিলেন।” (Harrison Brown, “Six Month of Hitlerism”, Ibid)। এই ইংরেজ সাংবাদিক জার্মানিতে প্রায় চার বছর বসবাস করেছেন। তাঁর মতে, নাৎসিদের যুদ্ধ প্রচারণা মাত্রা ছাড়িয়ে এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, বৈধভাবে কোন শান্তিবাদী সংগঠনের সদস্য হওয়াও (!) শাস্তিযোগ্য অপরাধে পরিণত করা হয়েছিল—যেমন, দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড। জার্মানির বিখ্যাত লেখক কার্ল ভন ওসিয়েটজ্কি কেবল শান্তিকামী হওয়ার কারণেই নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং কারাভোগ করেছেন। এইতো গেল বছর তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কার লাভের পরেও তিনি কারান্তরীণ, প্রকাশ্য আদালতে বিচার পাওয়ার অধিকার থেকেও বঞ্চিত।
একজন উদারপন্থী আমেরিকান সাংবাদিক ভার্সাই চুক্তির ফলে জার্মানির সাধারণ জনগণের উপর চলা অন্যায় এবং দুর্দশা দেখে, সাধারণ জনগণের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে লিখেছেন: “রাইখস্ট্যাগ ঘিরে ধর্মের মত যুদ্ধ-পূর্ব সামরিকবাদ এবং নৃশংসতার উত্থান ঘটতে দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি একটি জাতিকে ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে আধা-ভৌতিকভাবে মিলিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। ধর্মান্ধ এই গোষ্ঠী অতিমানবের কাছে অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হয়। অতিমানবদের কাছে এই ধর্মান্ধ গোষ্ঠী অপ্রতিরোধ্য হিসেবে প্রতীয়মান এবং এদের কাছে ইহুদি, অধ্যাপক, শান্তিবাদী, সমাজতান্ত্রিক, র্যাডিকাল, উদারপন্থী, এবং গণতন্ত্রী প্রত্যেকেই ঊন-মানুষ।” (John Gunther, “The Nation”, New York, June 7, 1933)।
ব্যাভারিয়ার প্রাদেশিক সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. ফ্রিটজ শেয়ের, যিনি কিনা বর্তমানে একজন ফ্যাসিস্ট প্রো-কন্সুলের দ্বারা স্থানান্তরিত হয়েছেন, তিনি একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে তাঁর সাবেক সহকর্মী এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বরাবর লিখেছেন: “অধিকার এবং ন্যায়ের কিংবা আইনশৃঙ্খলার কোন চিহ্নই রাখা হয়নি। ঐশ্বরিক এবং মানবিক সকল ধরনের অধিকার পদদলিত হচ্ছে। অধঃপতিতরা নিজেদের জার্মানির নৈতিকতার পুনর্জন্মদাতা বলে দাবি করে, অথচ বাস্তবে তারা কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের উপর তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিয়েছে এবং বন্য প্রাণীর মতো তাদের অহংকারী প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেছে।” ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে দৈনন্দিন ঘটনাবলীর উপর ভিত্তি করে মত প্রকাশের জন্য, ড. শেয়েরের বিচার করা হয়েছিল এবং রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।
“এটি একেবারেই স্পষ্ট যে, বর্তমান জার্মান সরকার পাশবিক এবং প্রগতিবিরোধী মানুষের সমন্বয়ে গঠিত। তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাগাতে প্রস্তত যা কিনা জার্মান সংস্কৃতিতে স্বাভাবিক এবং মূল্যবান।” (The New Republic”, New York, April 26, 1933)। এই উদ্ধৃতিটি একটি বেনামে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। লেখক ভয়ে তার নাম প্রকাশ করতে চাননি। সত্য বলার অপরাধে বর্বর ফ্যাসিস্টদের প্রতিশোধের মুখে পড়তে পারেন এই ভয়ে বৃদ্ধ অধ্যাপক নিজের পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিলেন। সত্যকে এমন সন্ত্রাসী কায়দায় ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছিল যে সিস্টেমের নাগালের বাইরে পালিয়ে যাওয়া জার্মানরা পর্যন্ত সত্য বলতে ভয় পাচ্ছিল। কারণ তাদের অনেকের বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজন তখনও জার্মানিতে বসবাস করছে। প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে তারা এই মানুষগুলোর উপর অত্যাচার করত। সাধারণত ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রবাসীদের আত্মীয়স্বজনকে জিম্মি করে দেশের বাইরেও তাদের মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য করত।

রক্তপাতহীন বিপ্লবের বর্বর সহিংস অনুশীলন এতটাই তীব্র ছিল যে, ‘অতিমানবদের’ মধ্যেও ব্যতিক্রমী কিছু ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিবাদ উস্কে দিচ্ছিল। এদের মধ্যে কিছুটা হলেও ভদ্রতা অবশিষ্ট ছিল। কাউন্ট ভন রিভেন্টলো নামের একজন ব্যক্তিকে হিটলারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখা যায় “ট্রেড ইউনিয়নের কর্মচারীদের টেনে হিছড়ে নাৎসিদের প্রধান কার্যালয়ে নেওয়া হয়। এই কর্মচারীদের ভেতরে নারীও ছিলেন। তাদের মারধর করা হয় এবং নারীদের সাথে এমন খারাপ ব্যবহার করা হয় যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।”
আধুনালুপ্ত প্রজাতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, এটির প্রথম চ্যান্সেলর, ফিলিপ শেইডম্যান প্রাগে নির্বাসিত অবস্থায় লিখেছিলেন, “হিটলারের বার্লিন হল অগ্নিসংযোগকারী টর্চের মত যেখানে অপরাধী এবং একদল উন্মাদ গানপাওডারের পিপা নিয়ে খেলছে।” (“The Times”, London, end of June 1933)। এই মত প্রকাশের অপরাধে বেশ কয়েকজন নারীসহ শেইডেনের পরিবারের যারা তখনও জার্মানিতে অবস্থান করছিল তাদের সবাইকে গ্রেফতার করা হয়। তাদেরকে কমিউনিকেডো নামের বন্দি শিবিরে রেখে তাদের উপর মধ্যযুগীয় কায়দায় অত্যাচার চালানো হয়। বয়স কিংবা লিঙ্গের বাছ- বিচার ছাড়াই ‘অপরাধী এবং মানসিকভবে উন্মাদ’ ব্যক্তিদের দ্বারা হিটলারীয় কায়দায় এই বর্বরতা চালানো হয়েছিল।
এডলফ হিটলার জীবনীকারদের জন্য হতাশা উদ্রেককারী। একজন জীবিত রাজনৈতিক নেতার জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করা সবথেকে কঠিন। কিন্তু সেই নেতা যখন আধা-উন্মাদ, ক্ষমতাধর, সেই ক্ষমতা যখন সে অন্ধ উন্মাদনার দ্বারা আরও বাড়াতে চেষ্টা করে; যখন সে একইসাথে অস্তিত্বহীন এবং ত্রাণকর্তা; তার আচরণ যখন সাধারণ থেকে শুরু করে ভয়ঙ্কর পর্যন্ত বিস্তৃত, একইসাথে বিরক্তিকর এবং মহৎ, অর্বাচীন থেকে শুরু করে আবেগপূর্ণ; যখন সে বাইরের অন্ধকার থেকে উঠে আসা ভুতুড়ে কণ্ঠস্বর শুনতে পায় এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়, তখন জীবনীকারদের কাজ শুধু কঠিন নয় অসম্ভব হয়ে ওঠে।” (The New Republic”, New York, June 10, 1936)।
“যখন কেউ একজন নেতার বক্তব্য শোনে, সে বুঝতে পারে যে রোগাক্রান্ত মনের সান্নিধ্য অনুধাবন করতে পারে। গত জুনের ঘটনা (তাঁর একসময়ের বিশ্বস্ত লেফট্যান্যান্টদের হত্যাকাণ্ড) আমাদের ভাবতে বাধ্য করেছে যে সে নিপীড়নকারী এবং মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থ একজন মানুষ। একটি মহান এবং অতি সভ্য একটি জাতি এমন একজন ব্যক্তির করুণা প্রার্থী যে কিনা স্নায়বিক অস্থিরতাক্রান্ত, পরিকল্পিতভাবে ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। পরামর্শদাতা হিসেবে একজন ব্যক্তিই তার পাশে থেকে তাকে পরিচালিত করতে পারে, সে হল গোয়ারিং। গোয়ারিং তার নিজের রেকর্ডেই হিটলারের থেকে বেশি নিষ্ঠুর এবং আরও বেশি বেপরোয়া।” (The New Statesman and Nation”, London, August 14, 1934)।
“ফ্যাসিবাদ হল যুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; সহিংসতা, আবেগ এবং গভীর আসক্তির প্রতি আহবান। এর ফলাফল অতি আবশ্যকভাবে নিষ্ঠুরতা, উন্মাদনা এবং গুন্ডাগিরি।” (Robert Dell, “Germany Unmasked”)। বিভিন্ন অফিশিয়াল প্রকাশনার উদ্ধৃতিসমূহ ঘেঁটে লেখক এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। মি. ডেল দেখিয়েছেন কিভাবে নাৎসিরা অনেক সময় নিষ্ঠুরতাকে প্রয়োজনীয়তা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করত এবং কখনও কখনও ‘ইহুদি মিথ্যাচার’ হিসেবে নিন্দা করত। সত্যিকার অর্থে নিষ্ঠুরতার ঘটনাগুলো কোন দূর্ঘটনা তো নয়ই বরং যুক্তিসঙ্গত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে গৃহীত নাৎসি নীতিরৈ অংশ। রক্তপাতহীন বিপ্লবের সবথেকে জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি গান হল: “ছুরি থেকে যদি ইহুদির রক্ত পড়ে, তাহলে আমরা দুইবার করে মার্চ করব”।
হিটলারের জীবনীগ্রন্থে কর্তৃত্বমূলকভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, ফ্যাসিবাদের প্রধান উদ্দেশ্যই হল দূর্বলের ধবংস এবং সবলের জয়। সামাজিক ব্যাধির ফ্যাসিবাদী ঔষধ হল ইহুদিদের ধ্বংস এবং জোরপূর্বক পুঁজিবাদ টিকিয়ে রাখা। এর রাজনৈতিক কর্মসূচি হলো অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি এবং বিজয়ের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা। “উপনিবেশগুলো ক্ষমতার অধিকারে অধিগ্রহন করা হয়েছিল। ইউরোপের দরকার ছিল কাঁচামাল এবং উপনিবেশ। যেখানে জীবনের এক বীরত্বপূর্ণ ধারণা নিয়ে শ্বেতাঙ্গরাই শাসন করার জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু শাসক জাতি যদিশান্তির ধারণা প্রতিষ্ঠা করে, উপনিবেশগুলোকে নিজেদের শাসন করতে অনুমতি দেয়, তাহলে তারা বলতে পারে ‘আমাদের এখানে ইউরোপের আর কোন দরকার নেই’।’’ (Hitler at the Conference of university Students, Munich, January 26, 1936)।
নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে, হিটলার ইতিহাসে একজন দক্ষ বাগ্মী জননেতা এবং একজন সুযোগসন্ধানী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করবেন, যিনি কোন নীতি জানেন না। তার মতে, জনগনকে শাসন করার সবথেকে কার্যকর পদ্ধতি হল তাদের প্রতারিত করা। তার শাসনের নীতি হল একই স্লোগান বারবার উচ্চারণ করতে থাকা ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণে জনগণ তা বিশ্বাস করতে শুরু করে। “তার জীবনের দর্শন যুদ্ধের পূর্বে ভিয়েনায় কাটানো তার ভবঘুরে জীবনের আদর্শ দ্বারা পরিচালিত। তারপর আর কোন বিকাশ হয়নি; কেবল নতুন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে শিখেছে। প্রায় বিশ বছর ধরে তার কোন বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচর্যা হয়নি। তার রাজনীতি করার ধরন খুবই অদ্ভুত। অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা, শ্রমিক শ্রেণির মানুষদের বোকা জ্ঞান করা, তাদের বুদ্ধিমত্তাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করাটাই যেন স্বাভাবিক তার কাছে। সাধারণ রাজনীতিবিদদের যে জিনিসগুলো আক্রান্ত করে হিটলারকে তা করে না। অন্যায় কিংবা বৈষম্য নিয়ে তার কোন মাথাব্যাথা নেই। সেনাবাহিনী, পুঁজিবাদী এবং সামন্তপ্রভু এই তিন গোত্রের কাছে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। দুর্বল এবং নিপীড়িত জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে সবলের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে এরকম প্রতিটি কাঠামো সে বিলুপ্ত করতে চেয়েছিল। গণতান্ত্রিক সভ্যতার মৌলিক নীতিসমুহ প্রত্যাখ্যান করে সে জার্মানির আদি গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছিল যেখানে সবলেরা শাসক আর দুর্বলেরা প্রজা।” (Rudolf Olden, “Hitler”)।
পরিশেষে একটি সাম্প্রতিক বই থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল। বইটির লেখক ষোল মাস জার্মানিতে অবস্থান করে ‘নিরপেক্ষভাবে’ পরিস্থিতি তদন্ত করেছেন। হিটলারের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে যে গুঞ্জন ছড়িয়েছে সে ব্যাপারে সতর্ক করে তিনি লিখেছেন: “সে নিজেকে একজন ক্রুসেডার মনে করে যে কিনা গোটা মানব জাতিকে রক্ষা করতে এসেছে। ফলে সে যখন বলশেভিকদের হাত থেকে পৃথিবী রক্ষার ব্যাপার নিয়ে কথা বলে নিজেকে মহিমান্বিত মানুষ ভেবে আত্মতুষ্টি পায়।” (Stephen H. Roberts. “The House that Hitler Built”)। হিটলার জনসম্মুখে বক্তৃতা দেওয়ার সময় পাগলের মত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ত, কাঁদত অথবা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। এ ব্যাপারে বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক রবার্ট, হিটলার সম্পর্কে গোয়ারিং এর করা মন্তব্য উদ্ধৃত করেন: “কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেই আমরা হিটলারকে কাঁদতে দেখেছি।” সব ধরনের অসংযত আচরণের কথা মাথায় রেখে রবার্ট গোয়েবলসকে ইউরোপের সবথেকে বিপজ্জনক মানুষ হিসেবে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। “কারণ এই লোকটি মানবিকতাকে অগ্রাহ্য করেও সাড়ে ছয় কোটি মানুষের দায়িত্বপ্রাপ্ত। শারীরিক ত্রুটি থেকে সৃষ্ট তীব্র বিরক্তি এবং নির্যাতনের শিকার স্নায়ুতন্ত্রের অসুবিধার কারণেই হয়ত মানবতার প্রতি তার এক ধরনের অবজ্ঞা রয়েছে। সব সময়ই তার মধ্যে তিক্ততা ভর করে থাকত। পুরো জার্মানি জুড়ে কাউকেই তার ব্যাপারে মমতা নিয়ে কথা বলতে শুনিনি”। (প্রাগুক্ত)
এমন ‘অতিমানবেরাই’ আজ জার্মানির ভাগ্য বিধাতা। তাদের মত ইতালি এবং অন্য ইউরোপীয় দেশগুলোতেও শাসন চলছে। সমগ্র ইউরোপ এই বর্বর উন্মাদ ধর্মপ্রচারকদের অধীনে আসবে না, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। আজকের দিনে ফ্যাসিবাদের প্রেতাত্মা ইউরোপীয় সভ্যতাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। হিটলার সেই জঘন্য প্রেতাত্মার প্রতিনিধি। “হিটলার এমন একটি প্রপঞ্চ যাকে কেউ হত্যা করে অথবা যার দ্বারা কেউ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়।” (Konard Heiden, “Hitler”)।