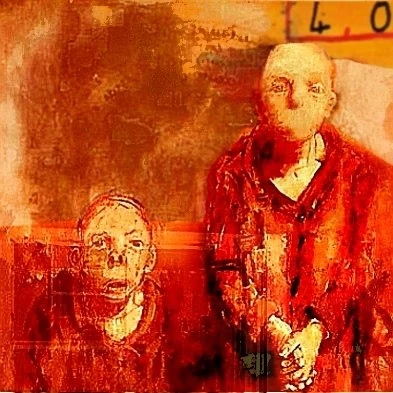- আব্দুল্লাহ হেল বুবুন
সভ্যতা কেন্দ্রিক বয়ান আবারো বৈশ্বিক রাজনীতির কেন্দ্রে ফিরে এসেছে। চায়না, ভারত, রাশিয়া, তুরস্কসহ বেশ কিছু কর্তৃত্ববাদী দেশের সরকার নিজেদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পলিসিকে বৈধতা প্রদানে সভ্যতাবাদী পরিচয়কে সামনে নিয়ে আসছে। যেমন, ২০১৯ সালে ক্রাইস্টচার্চের দুটি মসজিদে সন্ত্রাসী হামলার পর এক বার্তায় এরদোগান জানায়, “ক্রুসেডারদের অবশিষ্ট অংশ তুরস্কের উত্থান থামাতে পারবে না। ইস্তাম্বুল কখনো কন্সটান্টিনোপল হবে না।” পুতিন কখনোই এটা জানাতে ভোলেন না যে, রাশিয়া একটি সভ্যতা, কোন জাতি রাষ্ট্র নয়। এই প্রবণতার বাইরে নয় উদারবাদী গণতন্ত্রের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন বক্তব্যে সভ্যতা কেন্দ্রিক বয়ান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মার্চ মাসের চার তারিখে কংগ্রেসে দেয়া একটি ভাষণে ট্রাম্প পৃথিবীর ইতিহাসে সবথেকে শক্তিশালী “সভ্যতা” তৈরি করার ঘোষণা দেন। এতোসব সভ্যতা কেন্দ্রিক বাগড়ম্বরের মুখে অনেকেই ধারণা করছে, জাতি–রাষ্ট্র ভিত্তিক বিশ্ব ব্যাবস্থার দিন শেষ হয়ে আসছে, সভ্যতাগত রাষ্ট্রই ভবিষ্যত।
আদতে সভ্যতাগত রাষ্ট্রের ধারণাটি যতোটা না বাস্তবতা, তার থেকে বড় মিথ। সভ্যতাবাদের রেটোরিক ব্যবহার করা চীন, রাশিয়া, ভারত ও তুরস্কের ক্ষমতাসীনদের (এবং তাদের নিপীড়নমূলক পদক্ষেপের) জন্য সভ্যতাবাদ একটি ‘‘লেজিটিমাইজিং ডিস্কোর্স”, তার বেশি কিছু নয়।
অবশ্য ওই আলোচনায় যাওয়ার আগে জেনে নেয়া যাক সভ্যতাগত রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যগুলো।
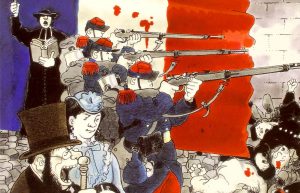
সভ্যতাগত রাষ্ট্র কী?
সভ্যতাগত রাষ্ট্র মূলত এমন একটি দেশ, যা নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ড, ভাষা বা এথনিক গোষ্ঠীর বদলে একটি সামগ্রিক সভ্যতাকে প্রতিনিধিত্ব করার দাবি জানায়। সভ্যতাগত রাষ্ট্রের ধারণা কিছু পূর্বানুমানের উপর দাঁড়ানো।
এক, পৃথিবীতে বিভিন্ন সভ্যতা রয়েছে। এবং বিভিন্ন সভ্যতার মূল্যবোধ র্যাডিকালি ভিন্ন ও বিপরীত।
দুই, একটি দেশ তখনি সফল হতে পারে, যখন সেই দেশ নিজের সভ্যতাগত পরিচয়কে ধারণ করে।
তিন, লিবারেল ওয়ার্ল্ড অর্ডার সংস্কৃতি ও সভ্যতা নিরপেক্ষ কোন সর্বজনীন মূল্যবোধকে ধারণ করে না। নিজেদের সুবিধার্থে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার নানাবিধ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার (যেমনঃ আলোকায়ন) ফসল এসব মূল্যবোধকে “সর্বজনিনতা“-র নামে সারা দুনিয়ার উপর চাপিয়ে দিয়েছে পশ্চিমা এলিটরা।
তুরস্ক, ইরান, ভারত, চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র— কোন না কোন সময় এরা “সভ্যতাগত রাষ্ট্র” বলে চিহ্নিত হয়েছে৷ তবে, চীন–রাশিয়া–তুরস্ক–ভারত এর সভ্যতাগত পরিচয় অ্যাকাডেমিয়ায় বেশ আলোড়ন তুলেছে এবং আমার আলোচনা এদেরকে নিয়েই হবে। এই চারটি রাষ্ট্রের মাঝে কেবল রাশিয়াই ন্যাশন স্টেট পরিচয়কে অস্বীকার করে নিজেকে সভ্যতাগত রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণ করেছে৷ অন্যরা সভ্যতা ও রাষ্ট্র এর মাঝে ফারাক না টেনে—উভয় শব্দকে একটি অপরটির বদলে ব্যবহার করে।
“সভ্যতাবাদ“: লেজিটিমাইজিং ডিস্কোর্স
পৃথিবীকে যে বেশ কয়টি সভ্যতায় বিভক্ত করা যায় এবং এই সভ্যতাগুলো বহুবিধ অসংগতিপূর্ণ মূল্যবোধের কারণে একে অপরের সাথে বিরোধে লিপ্ত হয়—এই ধারণাটি চীন ও রাশিয়ার অ–গণতান্ত্রিক সরকার এবং তুরস্ক ও ভারতের নির্বাচিত কর্তৃত্ববাদী সরকারের বয়ানে বেশ জোড়ালোভাবে উপস্থিত৷ জনতুষ্টিবাদ ও কর্তৃত্ববাদ এই চারটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। এসব রাষ্ট্রে সভ্যতাবাদের বয়ান দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
প্রথমত, সভ্যতাবাদ কর্তৃত্ববাদী–জনতুষ্টিবাদী সরকারকে সহজেই “জনতা“, “অভিজাত” শত্রু এবং “বিপদজনক অপর” নির্মাণে সাহায্য করে। এই সভ্যতাবাদী পরিচয় নির্মাণে ধর্ম সর্বত্র একই প্রভাব না রাখলেও তার ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তুরস্ক ও ভারতে ধর্ম কেবল ‘অপর‘ থেকে জনতাকে আলাদাই করে না; তা দেশীয় সেকুলার অভিজাতদেরও চিহ্নিত করতে সাহায্য করে, যারা নিজেদের সভ্যতার পবিত্র ধর্মকে ত্যাগ করে বিদেশীদের সাথে আতাঁত করেছে। উভয় দেশেই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আধুনিকতা ও সেকুলারিজমকে উপস্থাপন করেছে জনতার প্রধান শত্রু হিসেবে। এছাড়া, রাশিয়া ও চীনে খ্রিস্টান অর্থোডক্সি ও কনফুসিয়ানিজম সভ্যতা পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত।
সভ্যতাগত পরিচয়কে উদযাপন করা এই চারটি দেশের ক্ষমতাসীন সরকারই পাশ্চাত্য আধুনিকতা ও এর সর্বজনীন মূল্যবোধগুলোকে (যেমন: মানবাধিকার) সাম্রাজ্যবাদের অভিব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে, তাদের বিভিন্ন সময়ে অস্বীকার করেছে। একইসাথে, এই বয়ানে দেশের বিভিন্ন সমস্যার (বর্তমান বা ঐতিহাসিক) জন্য দায়ী করা হচ্ছে আধুনিকতা প্রভাবিত পশ্চিমা এলিটদের।
দ্বিতীয়ত, এসব দেশের কর্তৃত্ববাদী সরকার নিজেদের নিপীড়ন ও কর্তৃত্ববাদকে বৈধতা প্রদান করতে অনেক সময়ই সভ্যতাবাদী রেটোরিকের দারস্থ হন। মোদির ভারতে মুসলিমদের উপর সংঘটিত নিপীড়নকে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক হেজেমোনি রক্ষার বয়ান দ্বারা বৈধতা প্রদান করা হয়৷ পুতিন লৈঙ্গিক সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন এবং ইউক্রেন আক্রমণকে উপস্থাপন করেছে পশ্চিম ও এর অবক্ষয়মূলক উদারবাদী ভাবাদর্শ থেকে রাশিয়াকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে৷ তুরস্কের ক্ষমতাসীন একেপি পার্টিবিরোধী ও গুলেন আন্দোলনের সাথে জড়িতদের দমন এবং অ–সুন্নি মুসলিম, সুন্নি মুসলিম ও কেমালপন্থী সেকুলারদের প্রান্তিকীকরণকে তুলে ধরছে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র থেকে তুরস্ককে মুক্ত করার উপায় হিসেবে (এরদোগানের ভাষ্য অনুযায়ী, যা তুরস্ককে তার অতীত সমৃদ্ধিতে পৌঁছাতে সাহায্য করবে)। উল্লেখ্য, সরকারের জনপ্রিয়তা কমলে কিংবা কোন অজনপ্রিয় পলিসির জাস্টিফিকেশনে প্রায়ই সভ্যতাবাদী বয়ানকে সামনে নিয়ে আসা হয়।

উপরের আলোচনাটা থেকে এটা পরিষ্কার যে, উল্লিখিত চারটি দেশের সরকারের জন্য সভ্যতাবাদ রূপান্তরিত হয়েছে শক্তিশালী একটি ভাবাদর্শিক অস্ত্রে। তবে, ভাবাদর্শিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার মানে এই না যে, এইসব রাষ্ট্র বর্তমানে জাতি–রাষ্ট্র প্যারাডাইমের বাইরে অবস্থান করছে। কেননা, কোন সরকারই চিরস্থায়ী নয়; বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারগুলো বিভিন্নভাবে বিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে এবং যারা বিরোধিতা করছে তারা অধিকাংশ সময়ই কোন সভ্যতাগত মূল্যবোধ ধারণ করে না। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় কংগ্রেসের কথা বলা যেতে পারে। সুতরাং, চীন, রাশিয়া, তুরস্ক ও ভারতকে সভ্যতাগত রাষ্ট্র না বলে সভ্যতাগত শাসন বা সরকার (রেজিম) বলাই বোধহয় বেশি যৌক্তিক হবে।
নব্য উদারবাদ ও সভ্যতাবাদ: দি ‘আনহোলি অ্যালায়েন্স‘
উপরে আলোচিত তথাকথিত সভ্যতাগত রাষ্ট্রের সরকার নিজেদেরকে জনতার চ্যাম্পিয়ন হিসেবে (যারা বিদেশি অভিজাত ও বিদেশ প্রভাবিত দেশীয় অভিজাতদের বিপক্ষে জনতার হয়ে লড়াই করে) দাবি করলেও তাদের অর্থনৈতিক নীতিকে কোনভাবেই জনবান্ধব বলা যাবে না। চারটি দেশের সরকারই কম বেশি নব্য উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেছে, যা সবগুলো দেশেই অর্থনৈতিক অসমতার ট্রেন্ডকে বৃদ্ধি করেছে। প্রচুর মানুষকে তাদের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ বিভিন্ন মৌলিক মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এই দেশগুলোর অর্থনৈতিক অসমতার অবস্থা থেকে আমরা এ বিষয়ে ধারণা পেতে পারি। উল্লেখ্য, তুরস্কের সবথেকে ধনী ২০ শতাংশ ব্যক্তি তুরস্কের ৪৮ শতাংশ সম্পদের মালিক। ভারতের অবস্থা আরো খারাপ, সেখানকার সবথেকে ধনী ১ শতাংশ ধনী ভারতের ৪০ ভাগের বেশি সম্পদের মালিক, অন্যদিকে নিচের ৫০ শতাংশ ব্যক্তি কেবল ৩ ভাগ সম্পদের মালিক (ইনকাম অ্যান্ড ওয়েলথ ইনইকুয়ালিটি ইন ইন্ডিয়া, ২০২২–২৩: দি রাইজ অব বিলিওনেয়ার রাজ)। চীনের টপ ১০ শতাংশ ব্যক্তি সেখানকার ৬৮ ভাগ সম্পদের মালিক এবং ওয়ার্ল্ড ইকুইটি ডেটাবেজ অনুযায়ী বর্তমানে চীনে পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিলিওনেয়ার রয়েছে।
আশির দশকে খ্রিস্টান ডানপন্থা ও নব্য উদারবাদী অর্থনৈতিক ডানপন্থা রোনাল্ড রিগানের মধ্য দিয়ে মিলিত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ডিল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে। জনবান্ধব ইমেজধারণকারী রিগানের হাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েলফেয়ার অর্থনীতি পরাজিত হয়। ঠিক একইরূপে, অভিজাত শত্রুদের বিরুদ্ধে জনতার সরকার হিসেবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করা রাশিয়া, ভারত ও তুরস্কের ডানপন্থী ‘সভ্যতাগত‘ সরকারও নব্য উদারবাদকে নিজ নিজ দেশে আরো শক্তিশালী করছে। সম্প্রতি, ট্রাম্পের বিভিন্ন সংরক্ষণবাদী (প্রটেকশনিস্ট) অর্থনৈতিক পলিসির প্রতিক্রিয়ায় তারাও বেশ কিছু সমরূপ নীতি নির্ধারণ করেছে। আসলে, অর্থনীতির জায়গা থেকে চিন্তা করলে, তথাকথিত সভ্যতাগত রাষ্ট্রগুলো কোন নতুন কিছু প্রদান করছে না। তারা পুরনো অর্থনৈতিক ব্যাবস্থারই অংশ।
সভ্যতাগত রাষ্ট্র ধারণাটির সাথে আমি সর্বপ্রথম পরিচিত হই ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা ও ছাত্র উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের একটি ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে। পরবর্তীতে তার আরো ভিন্ন ভিন্ন পোস্টে সভ্যতাগত রূপান্তরের ব্যাপারটি এসেছে। সম্প্রতি করা একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, দুটি সভ্যতাগত রাষ্ট্রের (ভারত ও চীন) মাঝে টিকে থাকতে হলে সভ্যতাগত রাষ্ট্র নির্মাণ অপরিহার্য। নাহিদ ইসলামের মন্তব্যও এখানে প্রাসঙ্গিক: “‘আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, জাতীয়তাবাদের যুগ শেষ হয়ে আসছে। আমাদের জাতীয়তাবাদের নানা ধরনের সমালোচনা ও দুর্বলতা আছে।…গোটা পৃথিবীই এখন সভ্যতাগত রাজনীতির দিকে আগাচ্ছে। ভারত ও চীনও কিন্তু সভ্যতাগত পরিচয় ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পৃথিবীর বুকে দাঁড়াচ্ছে। সেই জায়গা থেকে আমাদেরও সভ্যতাগত পরিচয় অনুসন্ধান করা প্রয়োজন (সমকাল, ২০ আগস্ট ২০২৪)।”
আমাদের উপরের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, “সভ্যতাগত রাষ্ট্র” এর ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজন স্বীকৃত কোন বিষয় নয়। বরং, অনেক প্রভাবশালী পণ্ডিতদের মতে, বিভিন্ন কর্তৃত্ববাদী–জনতুষ্টিবাদী রাষ্ট্র সভ্যতাবাদের বয়ান তাদের শাসন ও নানাবিধ পলিসিকে বৈধতা প্রদানে ব্যবহার করছে।
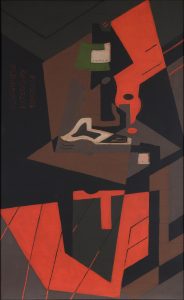
যদি আমরা তর্কের সাপেক্ষে ধরেও নেই যে, চীন ও ভারত সভ্যতাগত রাষ্ট্র। তারপরও, পার্শবর্তী চীন ও ভারত বা তুরস্ক ও রাশিয়া বাংলাদেশের জন্য আদৌ কোন রোল মডেল হতে পারে? তথাকথিত এসব “সভ্যতাবাদী রাষ্ট্র”–এর মানবাধিকার রেকর্ড অত্যন্ত বাজে এবং সরকার অনেকটাই অগণতান্ত্রিক। সংখ্যালঘু নিপীড়ন এসব রাষ্ট্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
দ্বিতীয়ত, মাহফুজ আলম ও নাহিদের সভ্যতাবাদী রাষ্ট্রপ্রকল্পের অর্থনৈতিক নীতি কী হবে? সেটা কি নব্যউদারবাদ থেকে ভিন্ন কিছু হবে?
তৃতীয়ত, বহুত্ববাদ জুলাই ২৪–এর অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি। মাহফুজ আলম একটি বহুত্ববাদী বাংলাদেশ নির্মাণের কথা বারবার বলেছেনও। তবে, সভ্যতাবাদ কি বহুত্ববাদী রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য একটি যথার্থ পন্থা হতে পারে? কেননা, আমাদের আলোচিত সকল তথাকথিত “সভ্যতাগত রাষ্ট্র”–ই এক্সক্লুশোনারি রাজনীতির ধারক।
মাহফুজ আলম কিংবা নাহিদ, উভয়ই কখনো কখনো সভ্যতাগত রাষ্ট্রপ্রকল্পের কথা বললেও, তারা কোন বিশদ পরিকল্পনা ও এর তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করেননি। তাদের যদি প্রকৃত অর্থেই সভ্যতাবাদী কোন রাষ্ট্রপ্রকল্প থেকে থাকে, তাহলেই অবশ্যই তাদেরক এই রাষ্ট্রের প্রকৃতি, অর্থনীতি ও সংখ্যালঘু অধিকার কেমন হবে, তার রূপরেখা নিয়ে সামনে আসা উচিত।