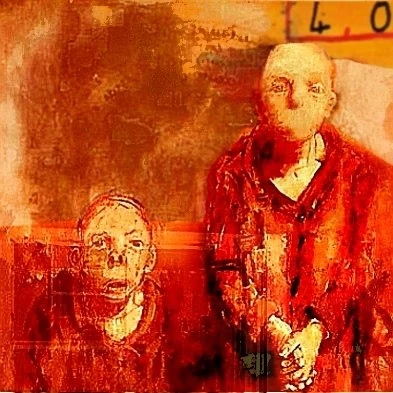- অনুবাদ: স্বদেশরঞ্জন দাস
[মানবেন্দ্র নাথ রায় বা এম এন রায়, উপমহাদেশের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী রাজনীতিবিদ ও তাত্ত্বিক। তার হাত ধরেই ম্যাক্সিকান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই এম এন রায় প্রথাগত মার্ক্সবাদী চিন্তা থেকে বের হয়ে নতুন রাস্তা অনুসন্ধানের চেষ্টায় ব্রতী হন, যার নাম দেন তিনি নয়া মানবতাবাদ। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয় তার New Humanism: A Manifesto। বর্তমান লেখাটি এ বইয়েরই অনূদিত সংস্করণের একটি অধ্যায় থেকে নেয়া হয়েছে। পুরো বইটির অনুবাদ করেন স্বদেশরঞ্জন দাস, যেখানে Radical Democracy-এর বাংলা তিনি করেন আমূল গণতন্ত্র। বর্তমান লেখাটি বই থেকেই হুবহু তুলে দেয়া হলো। – সম্পাদক]

এ যুগের মানুষকে যে-দর্শন নতুন আশা ও নতুন বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে সেই দর্শনকে অবশ্যই মুক্তির অর্থ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে হবে; মুক্তিলাভ করলে, মানুষের দাবীর কতটা কী পূরণ হবে তা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে হবে। সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ব্যক্তি মানুষকে, তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তুলতে কতখানি সাহায্য দেবে তার বিচার যদি বর্তমানের নানা পরস্পরবিরোধী মতবাদের গোঁড়ামি ও অন্ধ সংস্কার ও অনুশাসন দিয়ে করতে হয় তা হলে কেবল বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করবে এবং ইতিহাসের বৃহত্তম এই সংকট থেকে মানুষকে উদ্ধার করে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সকল মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাও সম্ভব হবে না এবং সংকট ত্রাণের আদর্শ আকাশকুসুমের মতই অলীক থেকে যাবে। সর্বজনকাম্য এক মুক্তির আদর্শের জন্যই এক সার্বজনীন প্রচেষ্টা সম্ভব হতে পারে।
মানুষের মুক্তি আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয়েছে তার জীবন সংগ্রাম থেকে। এই মুক্তি আকাঙ্ক্ষাই তাকে জীবন ধারণের প্রয়োজন মেটবার পরও প্রকৃতির ওপর নিজের আধিপত্য স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করেই চলেছে মানুষের নব নব জ্ঞানান্বেষণ প্রচেষ্টা। এর ফলেই সে প্রাকৃতিক ঘটনা, ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশের অত্যাচার ও শাসন থেকে ক্রমে ক্রমে মুক্তি পেতে পেতে এগিয়ে চলেছে। মানুষ তার জীবন সংগ্রাম চালাতে চালাতে যখন বিবর্তনের উন্নত স্তরে উঠেছে তখন সেই সংগ্রাম ক্রমে বুদ্ধি ও সুকুমার আবেগের স্তরে উন্নীত হয়েছে এবং সেটাই তখন উচ্চ মূল্যমানের পর্যায়ে এসে মানুষের এই মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় রূপ নিয়েছে। আধুনিক সমাজে ব্যক্তি মানুষকে যদি মুক্ত জীবনযাপন করতে হয় তবে তার শুধু অর্থনৈতিক প্রাচুর্য ও নিরাপত্তা থাকলেই চলবে না, তার অন্তর্নিহিত সকল বৃত্তি ও শক্তি সমূহের বিকাশ সাধনের অনুকূল এক মানসিক পরিবেশ ও এক মুক্ত আবহাওয়ার প্রয়োজন হবে, যেখানে কোন প্রকার বাঁধাধরা মতবাদের অন্ধ অনুশাসন থাকবে না। সমাজের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি মানুষ এই প্রকারের ব্যাপক অর্থে স্বাধীনতা ও মুক্ত পরিবেশ কতটা অর্জন করেছে তাই দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের গুণাগুণ বিচার হবে। “মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি” এই প্রাচীন ঋষি বাক্য অনুসরণ করে ভবিষ্যতের দর্শনকে ঘোষণা। করতে হবে, ব্যক্তি মানুষ কতখানি স্বাধীনতা পেল কিংবা পেল না, সেই মাপকাঠি দিয়েই কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের গুণাগুণ বিচার হবে।
জাতিই হোক আর শ্রেণীই হোক সব রকম সমষ্টি সত্তাই গড়ে ওঠে ব্যষ্টিরূপ ব্যক্তিকে নিয়ে। মানুষ[mfn] এখানে মানবেন্দ্রনাথ আদিম মানবকে “Man” এক বচনে ব্যবহার[/mfn] আরো অধিক মাত্রায় নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও এ সবের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার জন্যই সমাজবদ্ধ হয়েছিল সমাজ গড়েছিল। আদিম যুগে পারিবারিক মানুষ[mfn] যেহেতু মানুষ যুক্তিপরায়ণ জীবও বটে, সেইহেতু সে নিজ নিজ বুক্তি বুদ্ধি দিয়ে নিজের এবং নিজ পরিবার পরিজনের জীবন সংগ্রামের কষ্ট লাঘবের জন্যই সমাজবদ্ধ হয়েছে এবং প্রতিবেশীর ওপর কোন স্বাভাবিক আতের টান না থাকার জন্য সদব্যবহার না করলে সমাজবদ্ধতা থাকবে না সেইজন্য পরস্পরের বাঁধনের সিমেন্ট স্বরূপ সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসন প্রবর্তন করেছে, দণ্ডবিধি রচনা ক’রে সমাজে ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। “মানুষ”কে একবচনে ব্যবহার করলে পাছে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে সেইজন্য আমি Man. এর স্থানে “পারিবারিক মানুষ” লিখেছি (অনুবাদক )।[/mfn] তার পারিবারি জীবন সংগ্রামকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য নিয়েই অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সমাজ সম্পর্কের প্রবর্তন করে; এবং আদি মানুষের এই সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা সে ব্যক্তি মানুষ হিসাবেই শুরু করে। এই যে মানুষের জীবন সংগ্রামের বাধাবিপত্তি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তা কেবল তার জীবন সংগ্রামের কষ্ট লাঘবের ইচ্ছ থেকেই উদ্ভূত। কাজেই দেখা যাচ্ছে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে মানব সমাজের গতি প্রগতির মূল প্রেরণা। মানুষের অন্তর্নিহিত যুক্তিশীলতা, নীতিবোধ ও অন্যান্য সৃজনশীল সম্ভাবনাগুলি বিকাশের পথে যে সব প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাধা আছে তার ক্রমঃ করেছেন, কিন্তু তার অর্থ নয় যে আদিম মানব সমাজবদ্ধ হবার পূর্বে একা একাই থাকত। মানুষ কোনদিনই তা থাকত না। মানুষ প্রথম থেকেই পারিবারিক। কারণ মানুষের জননীকে জীবিকার্জনের কষ্টকর দায়িত্ব থেকে অবসর দিতে হয় এবং মানব শিশুকে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত মাতার ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়, সেইজন্য মানুষ প্রথম থেকেই পারিবারিক প্রাণী জগতকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যে-সব জীব একা একাই থাকে, কেবল বংশ রক্ষার সময় স্ত্রী পুরুষ ক্ষণিকের জন্য মিলিত হয়, স্ত্রী-প্রাণ সুবিধামত স্থানে ডিম পেডেই ছুটি নেয়-সন্তান পালনের দায়িত্ব থাকে না, আপনিই ডিম ফোটে – বাচ্ছারা নিজেরাই প্রকৃতি থেকে খাদ্য আহরণ করে বেঁচে থাকে; যেমন কীট পতঙ্গ জাতীয় প্রাণী। যে সব প্রাণী দল বেঁধে থাকে : যেমন পিঁপড়ে, মৌমাছি, উইপোকা।
যে সব প্রাণী পারিবারিক, স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে পরিবার বেঁধে বাস করে যেমন–সিম্পঞ্জি, ওরাং, গিবন ও মানুষ। মানুষ স্বভাবতঃ পারিবারিক জীব সেই হেতু সে পিঁপড়ে মৌমাছির মত সামাজিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন জীব নয়। তাই আতের টান নিজ নিজ স্ত্রী ও সন্তানের ওপর প্রতিবেশীর প্রতি নয়। কিন্তু অপসরণই হচ্ছে মুক্তি। সমাজের নানা আইন কানুন ও বিধি নিষেধের দ্বারা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ব্যক্তি মানুষের জন্য সর্বাধিক স্বাধীনতা লাভের ব্যবস্থা করা। সমাজের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করে তার সমষ্টি দিয়েই যে কোন সমাজ ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও প্রগতিমূলক মূল্যের বিচার করতে হবে। নতুবা সামাজিক অন্যায় অবিচার থেকে মুক্তি ও উন্নতির আদর্শ মিথ্যা হয়েই থাকবে।

কোন রাজনৈতিক দর্শন বা সামাজিক পুনর্গঠন পরিকল্পনায় ব্যক্তিব স্বাধীনতার আদর্শ যদি শূন্যগর্ভ অবাস্তব ও কাল্পনিক বলে পরিত্যক্ত হয় তবে তার বৈপ্লবিক গুরুত্ব খুবই কম না হয়ে পারে না। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় (রাষ্ট্রে) ও অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টায় রক্ত-মাংসের ব্যক্তি মানুষকে কাল্পনিক সমষ্টি সত্তাব যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়, সম্ভবতঃ ত দিয়ে ব্যক্তি মানুষের মুক্তি অর্জন করা যায় না। স্বাধীনতা কেড়ে নিলে অর্থাৎ একনায়কত্ব স্থাপন করলে মানুষ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলবে, এ কথা বলা অর্থহীন ৷ মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল প্রচেষ্টার যুক্তিসম্মত লক্ষ্য হওয়া উচিত অধিক থেকে অধিকত মাত্রায় ব্যক্তির স্বাধীনতা লাভ। একমাত্র ব্যক্তির স্বাধীনতা রূপেই স্বাধীনতা বা মুক্তির আদর্শ বাস্তব হয়ে উঠতে পারে।
কেবলমাত্র অর্থনীতির পুনর্গঠন করলেই কোন সমাজ আপন থেকেই মুক্ত সমাজ হয়ে ওঠে না; অথবা শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের দাবীদার কোন রাজনৈতিক পার্টি রাজনৈতিক ক্ষমত দখল করলেই যে সকল ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোপ, উৎপাদনের উপায় সমূহের ওপর রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠা, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্যেই শ্রমিক শোষণের অবসান বা ধনের সমবণ্টন হয় না। যন্ত্র-বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ সুযোগ নেওয়ার অজুহাতে কখনও বা কর্ম কুশলতা বাড়াবার জন্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টার দোহাই দিয়ে ব্যক্তির ভাল-মন্দকে অস্বীকার করা হয়৷ এর ফলে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য যে ব্যক্তির উন্নতি সেটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। এই জোর করে ওপর থেকে চাপানে৷. অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার দ্বার সামাজিক ন্যায়নীতি ও অর্থ নৈতিক সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত উন্নততর গণতন্ত্রের পরিবর্তে একনায়কশাসিত রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়! অর্থ নৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলেও হতে পারে কিন্তু রাজনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা একেবারেই সম্ভব নয়! অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর ধারা অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, এটা তাঁদের স্মরণ রাখা দরকার।
সর্বপ্রধান প্রশ্ন হল: কী জন্য পরিকল্পনা? ধরে নেওয়া হয়, পরিকল্পিত অর্থনীতিব দ্বারা সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হবে। অন্য কথায়, এর দ্বারা ধনের সমবণ্টনের সাহায্যে সমাজে ন্যায়-নীতির প্রতিষ্ঠা হবে। তা যদি হয় তা হলে অবশ্য ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে পরিকল্পনার সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে। আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞান যে স্তরে এসে পৌঁছেছে তাতে ব্যক্তি স্বাধীনতার সম্যক স্ফূর্তির পক্ষে যদি তা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তবে মানুষের কল্যাণের জন্য যন্ত্র-বিজ্ঞানের অধিক উন্নতি খর্ব করতে হবে। ডাঃ ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন সৃষ্ট রাক্ষস যেমন তার স্রষ্টাকেই হত্যা করেছিল, তেমন যন্ত্র যেন তার স্বষ্টা বর্তমান সভ্যতাকেই ধ্বংস না করে সেটা দেখতে হবে। যন্ত্র যখন মানুষই সৃষ্টি করেছে তখন সে মানুষেরই সেবা করবে—মানুষের মুক্তি লাভে, মনুষ্যত্বের বিকাশে সাহায্য করবে।[mfn] যন্ত্র ইতিমধ্যে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করতে শুরু করেছে। তারপর যন্ত্রের মালিকানা ব্যক্তির হাতে থাকায় এবং তা লাভ খাওয়ার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হওয়ায় ক্রমেই মানুষকে পুতুল-নাচের পুতুলে পরিণত করা হচ্ছে। আমেরিকার বর্তমান সমাজ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এবং পৃথিবীব্যাপী তারই অনুকরণ চলছে।। মানবেন্দ্রনাথ এখানে সেই বিপদের কথাই স্মরণ করিয়ে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করছেন বর্তমান নগরকে ও যন্ত্রশিল্পকে গ্রাম অঞ্চলেও বিকেন্দ্রিত করে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে যে পর্যন্ত সহায়ক হবে সে পর্যন্ত তা গ্রহণ-যোগ্য হবে, কিন্তু যখনই তা মনুষ্যত্বের পক্ষে হানিকর হয়ে উঠতে থাকবে তখনই সেখানে সীমারেখা টানতে হবে। আমূল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমবায়মূলক অর্থনীতির দ্বারা সেটা সম্ভব হবে। ( অনুবাদক)[/mfn]
একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাব অজুহাত যেমনই কেন হোক না, সমাজ উন্নয়ণের ব্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট পরিকল্পনায় তার স্থান নেই। বাজনীতি থেকে যদি ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দেওয়া হয় তবে রাজনীতির উদ্দেশ্য যে সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষ। সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। এটা অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য যে, নীতিবিরুদ্ধ অসৎ উপায়ের দ্বারা সৎ উদ্দেশ্যে পৌঁছান যায় না, অসৎ উপায়ই সম্প্রসারিত হয়ে চলতে থাকে। এই সত্য অনুসারে সোভিয়েট ইউনিয়ানে মানুষের মুক্তি আনার উপায় স্বরূপ সর্বহারার একাধিপত্যই চিরস্থায়ী ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে। এই সর্বহারার একাধিপত্যই কমিউনিজমের সঙ্গে সমার্থক হয়েছে—উপায়ই লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রের (মার্কসবাদ অনুসারে ) বিলুপ্ত হবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।” সোভিয়েট ইউনিয়ানে যদি বাস্তবিকই সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে তবে এই পরিবর্তনের জন্য যে মধ্যবর্তীকালের প্রয়োজন ছিল তার নিশ্চয় অবসান ঘটেছে। এবং এতদিনে একাধিপত্যের শেষ হওয়া উচিত ছিল। যতদিন না রুশিয়াতে একাধিপত্য শাসনের অবসান হচ্ছে এবং অন্যান্য দল ও মতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হচ্ছে, ততদিন সেখানে উচ্চ পর্যায়ের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলাও অর্থহীন।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের কাজ কর্মও তেমনি নৈরাশ্যজনক। সেই জন্য গতানুগতিক “গণতান্ত্রিক-সমাজতন্ত্রের” সাফল্য সম্পর্কেও ভরসা কর যায় না। গণতন্ত্রকে নব-রূপ গ্রহণ করতে হবে ৷ গণতন্ত্রকে মানবতাবাদী ঐতিহ্যে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমানের মত গণতন্ত্রকে কেবল মাথাগুণতির হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ-লঘিষ্ঠের মধে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বিশেষতঃ মানুষ যখন তাদের সার্বভৌম রাজক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য উপযুক্ত মর্যাদা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার কোন সুযোগ পায় না ৷ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দ্বারা বর্তমানের প্রতিনিধি মারফৎ পরোক্ষ শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তিত করতে হবে। রাজনৈতিক পার্টির চরিত্র বিচার করতে হবে তার ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচী দিয়ে ভোট ধরবার ক্ষমতা দিয়ে নয়। শুধু মাত্র মুখের কথা বা প্রতিজ্ঞার দ্বারা জনগণের নিকট ভোট ভিক্ষা করলে চলবে না, সেই পার্টির বাষ্ট্র শাসনের পূর্বতন নজির দেখিয়েই তা করতে হবে ৷ পরিচালন ব্যাপারে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশের বা মতামত জানাবার কোন ব্যবস্থা নেই, আছে কেবল ব্যালট বাক্সে মাথা গুণতির ব্যবস্থা। বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে, ব্যক্তি সত্তার পরিবর্তে এও সমষ্টিসত্তার নিকট আত্মসমর্পণ। এই ব্যবস্থার ফলে ব্যক্তিব ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানাবার বা বুদ্ধি-বিবেচনা প্রকাশের কোন সুযোগই থাকে না।[mfn] ফলে জনসাধারণের করার কিছু থাকে না বলে জনসাধারণের বুদ্ধি বৃত্তি অনুশীলনের অভাবে কোন দিনই বাড়তে পায় না। নেতাদের, পার্টির, ডেমাগগির যারাই চালিত হতে হয়। (অনুবাদক)[/mfn] পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে নীতিবোধ শুন্য বাক্যবীরেরা জনগণকে তাদের বাক্যজাল বিস্তারের দ্বারা অভিভূত করে রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে বসতে পারে। প্রজ্ঞা, সততা, জ্ঞান, নীতি ইত্যাদির কোন মূল্যই সেখানে থাকে না ৷ অথচ মানব সভ্যতার এইসব মূল্যবান গুণাবলীর সাহায্যে সমাজের রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও শাসন ব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত শোধন করার ব্যবস্থা না করলে সমাজে গণতান্ত্রিক জীবন কোন দিনই গড়ে উঠতে পারে না।
বর্তমান জগতে মানব সভ্যতার ঐ সব মূল্যবান গুণাবলীর ধারক ও বাহক নরনারীর অভাব নেই। কিন্তু যতদিন এই অবাঞ্ছিত বাক্যবীর ডেমাগগরা ক্ষমতায় বসে থাকবে ততদিন এইসব গুণীদের নেতৃত্ব লাভের কোন আশা নেই ৷ এই তো গেল পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের দিক ।
অন্যদিকে, একাধিপত্যশাসিত রাষ্ট্রও যদি একবার জেঁকে বসে—তা সে যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের ঘোষণা করলেও—তবে সেও এইরূপ গুণ সম্পন্ন নাগরিকের উদ্ভবে বাধা দেবে৷ এইভাবে পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসিতেই হোক আর একাধিপত্য শাসিত রাষ্ট্রেই হোক মানব সমাজ এই সব মুক্তবুদ্ধি ধীমান প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তির নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্রমোন্নতির পথে মুক্তির উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে পারে না।
বর্তমানের পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার তথাকথিত গণতন্ত্রে যদি এইসকল মূল্যবান গুণ-সমূহের দ্বারা রাজনীতিকে বিশুদ্ধ ও প্রভাবিত করার সুযোগ সুবিধা না থাকে, তাহলে একাধিপত্য শাসিত রাষ্ট্র এইসব মানবিক গুণসমূহ বিকাশে বাধা দেয় বলে তার নিন্দা করা এদের মুখে সাজে না। একাধিপত্যের দ্বারা সকল দুঃখের রাতারাতি সমাধানের আপাতঃ মধুর প্রলোভনের হাত থেকে জনসাধারণকে বাঁচাতে হলে গণতন্ত্রকে আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে যে মানবতাবাদী ঐতিহ্য ছিল তা পুনরাবিষ্কার করতে হবে।
পুনরায় ব্যক্তি মানুষকেই সকল উন্নতি-অবনতির মাপকাঠি করতে হবে। প্রজ্ঞা, সততা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও নীতিপরায়ণতার উৎকর্ষ দিয়েই নেতৃত্বের বিচার করতে হবে। একটা অন্তসারশূন্য আকার সর্বস্ব কাঠামোটা থাকলেই দেশে যে গণতন্ত্র আছে তা ধরে নেওয়া যাবে না। আজ প্রতিটি স্বাধীনতাকামী চিন্তাশীল ব্যক্তি এক কঠিন প্রশ্ন সমাধানের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন: গণতন্ত্র কী সম্ভব? পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করায় ধার। বিশ্বাসী, তারা একনায়কতন্ত্রকে পরিহার করেছেন বটে কিন্তু তাঁরাও আজ এই প্রশ্নটির সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। গণতন্ত্রের মূলনীতি যে, সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন, তা সম্ভব হতে পারে যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব মুক্তবুদ্ধি, বিবেকবান ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত হবে, কারণ এঁরাই নিজেদের বিবেকের নির্দেশকে সর্বাপেক্ষা বেশী মূল্য দিয়ে থাকেন।
নৈতিক প্রেরণাই মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় প্রেরণা। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে যে সু-শাসন চলবে তার নিশ্চয়তা আইন দেয় না, দেয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নীতিজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধি। ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, একনায়কতন্ত্রও ঐ নৈতিক প্রেরণা থেকেই অনুপ্রাণিত। সেই জন্যেই তারা বলে, সমগ্র জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই একনায়কতন্ত্র উপায় মাত্র। কিন্তু ক্ষমতার লোভ থেকে উর্ধ্বে উঠে সমগ্র দলটাই যে নীতিপরায়ণ থাকবে এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সৎ অসৎ মূল্যমানের প্রকাশ ব্যক্তির মাধ্যমেই ঘটে। সুতরাং একমাত্র মুক্তবুদ্ধি বিবেকবান ব্যক্তি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাতেই সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে। কারণ সর্বাগ্রে তারা তাদের নিজ নিজ বিবেকের নিকট দায়ী থাকে। বর্তমান সংকট থেকে ত্রাণ পেতে গেলে ও একনায়কতন্ত্রের প্রবল আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে গণতন্ত্রের এইরূপ দার্শনিক রূপায়ণই একান্ত প্রয়োজন।
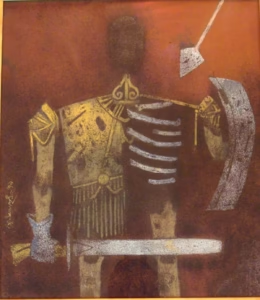
যা বলা হ’ল তার অর্থ এই নয় যে, “জ্ঞাণী-গুণী”দের রাজ প্রতিষ্ঠিত হোক। এখানে মাত্র বলা হল যে, সমাজকে এমন ভাবে পুনর্গঠিত করা হোক যাতে প্রতিটি মানুষ তার অন্তর্নিহিত সৃজনশীল শক্তিকে বিকশিত করে তোলার অফুরন্ত সুযোগ পায়। এটি সম্ভব হয়ে উঠবে তখনই যখন মানুষ সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থের প্রভাব মুক্ত হবে, যখন তার| আর লোক ক্ষ্যাপানে৷ ডেমাগগ নেতাদের জাতীয় স্বার্থ বা শ্রেণী স্বার্থের কাল্পনিক সত্তার দোহাই-পাড়া বক্তৃতায় পূর্বের মত সহজে মোহগ্রস্ত হবে না এবং এইসব মোহ-মুক্ত মানুষের হাতে বাষ্ট্রের শাসন পরিচালন ক্ষমতা ন্যস্ত হবে। কয়েক বছর অন্তর একদিন ভোটপত্র প্রদান মাত্রের মধ্যেই গণতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। নির্বাচন যদি সার্বজনীন ভোটের দ্বারাও হয়, কিংবা নির্বাচিত সদস্যের মধ্য থেকেই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, তথাপি গণতন্ত্র শূন্যগর্ভ আকার সর্বস্বই থেকে যায়। সার্বভৌম ক্ষমতার স্বত্ব ত্যাগ করে তা প্রতিনিধির হাতে তুলে দেওয়া, তা সে যত কম সময়ের জন্যই হোক, গণতন্ত্র বিরোধী এক বেকুবি ব্যবস্থা। এই হস্তান্তরিত সার্বভৌম ক্ষমতার স্বত্বে স্বত্ববান হয়ে, প্রতিনিধিরা যখন সরকার গঠন ক’রে বলে, ভ্রুন- সাধারণের “জন্য” সরকার গঠন করলাম, তখন যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলা চলে, যে-সরকার জনগণের “জন্য” ( for ) গঠিত হয়, সে-সরকারের “উপাদান” ( of ) জনগণ হতে পারে না৷ এবং তা জনগণের “দ্বারাও” ( by ) পরিচালিত হতে পারে না।
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত স্থানীয় গণ-সভা সমূহের ওপর ভিত্তি করে যদি এক পিরামিড আকারের রাষ্ট্র গড়ে তোলা হয় একমাত্র তখনই রাষ্ট্র পরিচালন ব্যাপারে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।[mfn] উলটো পিরামিড। কারণ এসব রাষ্ট্রে সব ক্ষমতা ওপরে, আর তলায় একেবারে শূন্য। মানবতন্ত্রী রাষ্ট্রকে সে তুলনায় সিধা পিরামিড বলা হচ্ছে। কারণ এখানে সকল ক্ষমতা তলায়, মাথায় একেবারে শূন্য। এখানে সার্বভৌম ক্ষমতা লোক- সভায় কেন্দ্রীভূত থাকবে না, তা গ্রামে গ্রামে ও নগরের পাড়াতে পাড়াতে ছড়িয়ে থাকবে। অনধিক ১০০০ মানুষ বাস করেন এমন অঞ্চলকে নিয়ে এক একটি গণ-সভা গঠিত হবে এবং সকল পূর্ণবয়স্ক মানুষ সেই গণ-সভার সদস্য হবে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা এই সকল গণসভা সমুহের সকল গণ-সভা সমূহের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনের (পঞ্চায়েত) থাকবে। তারা গণ-সভার দ্বারা দায়ী থাকবে ৷[/mfn]
পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র বা একাধিপত্য শাসিত রাষ্ট্রকে বলা যেতে পারে, এইসব গণ-সভা সমূহের সর্বপ্রধান কাজ হবে জন-সাধারণকে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা এবং সুবিবেচনা ও বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী সে অধিকার ব্যবহার করতে শেখান। সমগ্র সমাজ জুড়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই যে ব্যাপক ভিত্তি সেগুলি হবে জনগণকে হাতে-কলমে রাজনীতি শিক্ষা দেবার যেন এক একটি বিদ্যাপীঠ। আইনসভা সমূহের প্রতিনিধিরা অনাস্থা ভাজন হলে তাদের ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা ও আইন-কানুন সমূহের ওপর মতামত দেবার ক্ষমতা থাকার ফলে এই সব গণ-সভাগুলি সমগ্র রাষ্ট্রের ওপরই প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন করার অধিকার থাকবে একমাত্র এদেরই। এই ব্যবস্থার দ্বারা রাজনৈতিক পার্টি সমূহের দলাদলির উর্ধে গণতন্ত্রকে স্থাপন করা হবে। গুণী মানুষ তখন নিজ গুণেই জনগণের নিকট স্বীকৃতি লাভের সুযোগ পাবে। পার্টির স্বার্থরক্ষার জন্য বা পার্টির নিকট আনুগত্যের জন্য বা তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য বা অন্য কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব মূলক আচরণ পাবার প্রত্যাশায় তখন আর কাকেও চিন্তার স্বাধীনতা, নৈতিক নিষ্ঠা, নিরপেক্ষ জ্ঞানবুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হওয়ার মত অবস্থা থাকবে না ।
এই গণসভা সমূহের নিম্নলিখিত ক্ষমতা থাকবে : (১) লোকসভা ও রাজ্য বিধান সভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রার্থী মনোনয়ণ। (পল্লী অঞ্চলে নির্বাচনের সময় বা অন্য কোন কারণে মত বিরোধ দেখা দিলে সে মতবিরোধ মনোমালিন্যে দাঁড়ায় এবং বহুদিন ধরে চলতে থাকে। এই বিপদ এড়াবার জন্য বহু প্রার্থীর মধ্য থেকে ক্রমশঃ ছাঁটাই পদ্ধতিতে (process of elimination এই মনোনয়ন কার্য চলতে পারে। যথা, যিনি বা যাঁহারা শতকরা নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে কম ভোট পাবেন এবং যিনি সবচেয়ে কম ভোট পাবেন তিনি বাদ পড়বেন। তার পরে যারা থাকবেন, তাঁদের নিয়ে পুনরায় ভোট হবে। এই ভাবে বাদ পড়তে পড়তে মাত্র দু’জনের মধ্যে যিনি সর্বাধিক ভোট পাবেন তিনিই সেই অঞ্চলের সকল গণ-সভার মনোনীত প্রার্থী হবেন এবং সার্বজনীন ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন।)
(১) প্রতিনিধিগণ যাতে লোকসভায় ও রাজ্য বিধান সভায় জনগণের প্রক্ক” ইচ্ছা প্রকাশ করতে সক্ষম হয় সেই জন্য তাদের অনুক্ষণ সচেতন ও ওয়াকিবহাল রাখা;
(৩) লোকসভায় ও রাজ্যবিধান সভায় আলোচ্য আইন-কানুন সম্বন্ধে আলোচনা ও সে সম্বন্ধে মতামত জ্ঞাপন;
(৪) নির্বাচক মণ্ডলীর আদেশ অমান্যকারী প্রতিনিধিকে অপসারণ;
(৫) লোকসভা বা বিধানসভায় আলোচনার জন্য যে কোন আইনে খসড়া রচনা ও প্রেরণ;
(৬) লোকসভা, বিধানসভা বা শাসন পরিচালন বিভাগ কর্তৃক আ কোন কাজ সম্বন্ধে মতামত জ্ঞাপন;
(৭) স্থানীয় জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা (মাধ্যমিক পর্যন্ত), পথ ঘাট, উৎপাদক ক্রেতা সমবায়, নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা, ছোটখাট অপরাধের বিচার প্রভৃতি।
এই সকল গণ-সভা হবে জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং সমন্বয় সাধনের জন্য এ দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ গণ-সভার ওপর থাকবে পিরামিডের চূড়ার মত লোকস বা পার্লামেন্ট ।
গণতন্ত্রকে সম্ভব করে তোলার জন্য যে অবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন সে সম্বন্ধেই উপরি উক্ত কথাগুলি বলা হল। গণতন্ত্রকে সার্থক করে তুলতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সচেতন ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা নিজ নিজ বৃত্তি ও সম্ভাবনা সমূহকে বিকশিত ও সম্ভোগ করার জন্য ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা; এবং সেই ইচ্ছা পূরণের পথে যে সব বাধা-বন্ধন দেখা দেবে সেই সব বাধা-বন্ধন মুক্তির জন্য মানুষকে উদগ্র করে তোলা; এই সকল বাধা-বন্ধন মুক্ত হতে মানুষ যে নিজের চেষ্টাতেই পারে, মানুষ নিজেই যে নিজের জীবন ইচ্ছামত গড়ে তুলতে পারে এই প্রত্যয় জাগিয়ে তোলা; সংস্কার মুক্ত হয়ে স্বাধীন চিন্তা করার জন্য মানুষের মনে সাহস ও শক্তি সঞ্চারিত করা; এবং নিজেদের স্বাধীনতা পরের হাতে তুলে দিয়ে (পার্টি বা ডিকটেটরের হাতে ) দাসত্বের নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবনের ওপর ঘৃণা জাগিয়ে তোলা। গণতন্ত্রকে যদি মানুষের জীবনে রূপায়িত করে তুলতে হয় এবং তা প্রতিরক্ষার জন্য সামর্থ্য লাভ করতে হয়, তা হলে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও বিশ্বজনীন মানবতাবাদের ওপর ভিত্তি করে এক নতুন রেনেসাঁস আন্দোলন জাগিয়ে তুলতে হবে।[mfn] স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই দু’দশখানি গ্রাম বা মহকুমা, এমনকি জেলা পর্যায়ে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করতে হয়। সেইজন্য পরোক্ষ নির্বাচনের দ্বারা তিনটি স্তরে (অঞ্চল পঞ্চায়েত, ব্লক পঞ্চায়েত, জেলা পঞ্চায়েত) এই সংগঠনটি থাকবে। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান পঞ্চায়েত-রাজ আইন মানবেন্দ্রনাথের গণ-সভার আদর্শেই রচিত হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতা কেবলমাত্র স্বায়ত্ত শাসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। এর ফলে অতি সহজেই জনগণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করে রাষ্ট্রকে মানবতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিবর্তিত করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। (অনুবাদক) [/mfn]

এই রূপ পরিবেশ গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে যে স্বাধীন যুক্তিসঙ্গত চিন্তার স্ফুরণ হতে থাকবে তার ফলে মানুষের উচ্চতর গুণাবলীসমূহ সার্থকতার পথে পদক্ষেপ করবে। সভ্যতার আদিকাল থেকে মনুষ্য সমাজ যে সকল সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসন অনুসরণ করে আসছে সেই সব নৈতিক অনুশাসন মেনে চললেই সমাজের সংহতি ও ভারসাম্য রক্ষিত হবে এবং মানুষও সুখ শান্তি প্রগতির পথে এগিয়ে চলতে পারবে। তখন এর জন্য আর শ্রেণী বা জাতির কল্যাণে ব্যক্তিকে আত্মত্যাগ করতে বাধ্য ক’রে সমাজের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টার প্রয়োজন হবে না। যে সকল ব্যক্তি এইরূপ নৈতিক জীবন যাপনে উৎকর্ষ লাভ করতে পারবেন তাঁরাই চিন্তাশীল মানুষের নিকট সম্মানিত হতে থাকবেন এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় রূপে গণ্য হবেন। তখন লোক ক্ষ্যাপানো ডেমাগগদের দিন ফুরিয়ে যাবে। তখন কিছুদিন অন্তর নির্বাচনের সময় এক খণ্ড কাগজ ব্যালট বাক্সে ফেলেই গণতন্ত্রের সকল অধিকার ফুরিয়ে যাবে না—রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণে অধিকারও থাকবে। তখন জনগণ আর কেবল মাত্র “জনতা” মাত্রই থাকবে না—সংহত হয়ে উঠবে।
নবরূপায়িত গণতন্ত্র বাস্তবে রূপ নিয়ে গড়ে উঠতে অবশ্যই দেরী হবে। কিন্তু যতদিন না গণতন্ত্রের সে রূপায়ণ হচ্ছে ততদিন সেই পরিবর্তন কালের জন্য পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রেই এমন একটি সংবিধান রচনা করতে হবে যাতে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় দেশের সৃজনশীল প্রতিভা, মুক্ত বুদ্ধি এবং নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের স্থান হয়, যার ফলে তাঁরা মন্ত্রী প্রমুখ শাসনকার্য পরিচালকবর্গকে তাদের পরামর্শ ও প্রভাবের সাহায্যে পথ প্রদর্শন করতে পারেন। এই পরিবর্তন কালের জন্য পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র একদিকে যেমন জনগণের দ্বারা নির্বাচন ভিত্তিক হবে, অন্য দিকে তেমনি উচ্চ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে বেছে রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে স্থান দেবার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। যতদিন না সমগ্র সমাজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও নৈতিক মান যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হয়ে উঠছে ততদিন হয়তো কেবল নির্বাচনের মাধ্যমেই সমাজের গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিদের আইন সভা সমূহের মধ্যে আনা সম্ভব হবে না। অথচ জনসাধারণের বর্তমান অনগ্রসর অবস্থায় রাষ্ট্রের ওপর এ সব মুক্তবুদ্ধি ধীমান নীতি-নিষ্ঠ ব্যক্তির প্রভাব বিস্তারের ব্যবস্থা করতে না পারলে গণতন্ত্র সার্থক হয়ে উঠবে না ৷
এই পরিবর্তন কালের জন্য পার্লামেন্টে যে রাজ্য সভা (Council of State) থাকবে তা গঠিত হবে বৈজ্ঞানিক, ধীমান, চরিত্রবান, জ্ঞানী ও নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে এবং এই রাজ্যসভাই মন্ত্রীবর্গকে জরুরি সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শাসনকার্য পরিচালন ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে চলবে। খাদের নিয়ে এই রাজ্যসভা গঠিত হবে তাঁরা সাধারণত: দলগত রাজনীতির উর্ধে থাকতেই ভালবাসেন। তাই তাঁদের পেশাদার রাজনীতিকদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাদের মূল্যবান অবদান যদি পেতে হয় তা হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে: এঞ্জিনিয়ার, অর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, আইনজীবী, ঐতিহাসিক এবং দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি অন্যান্য সৃজনশীল কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংঘ তাদের প্রতিনিধি স্বরূপ নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির নাম রাজ্যসভার সদস্যপদের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি তাঁদের রাজ্যসভায় মনোনয়ন করবেন। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে এই সকল সংঘের সহিত যুক্ত নন অথচ অনুরূপ গুণের অধিকারী এইরূপ কয়েকজনকেও মনোনীত করতে পারবেন। ধনী ও কায়েমী স্বার্থের প্রভাব এড়াবার জন্য বেতনভোগী কর্মচারী ছাড়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদার হিসাবে বা অন্যভাবে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে স্বার্থজড়িত থাকবেন তাঁরা যেন এই রাজ্যসভার সদস্য হতে না পারেন, সেইরূপ ব্যবস্থা থাকবে। এই রাজ্য সভার ওপরই অর্থ নৈতিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার ভার থাকবে এবং সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করে তোলার জন্য কাজকর্ম তদারকী করার অধিকারও এদের থাকবে।
প্রারম্ভেই সমাজের অর্থ নৈতিক জীবন যেন ধনীদের দুর্নীতিপূর্ণ ও সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হয়ে উঠতে পারে সেই রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তার ফলে আরো বেশী সংখ্যক মানুষ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে সক্ষম হবে। দ্বিতীয়তঃ এই সব স্বাধীন- চিন্তাশীল ব্যক্তিদের তখন জন স্বার্থের বিশ্বস্ত রক্ষক রূপে পাওয়া সম্ভব হবে এবং তাঁরাও এই সব কায়েমী স্বার্থবানদের প্রভাবমুক্ত হয়ে জনকল্যাণকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম হবেন। গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের পূর্বে এই মধ্যবর্তী সময়ে যদি মাথা-গুণতির দ্বারাই গণতন্ত্রের প্রতিনিধি নির্বাচন চলতে থাকে তা হলে সমাজ জ্ঞানী-গুণীর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ এই সকল জ্ঞানী-গুণীরাই কেবল সমাজকে সত্যকার গণতান্ত্রিক মুক্তির দিকে পরিচালিত করে নিয়ে যেতে পারে।
র্যাডিক্যাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের অর্থনীতিকে এরূপভাবে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন যাতে মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণের সম্ভাবনা না থাকে। মানুষের মানসিক ও সুকুমার শক্তি ও বৃত্তি সমূহের বিকাশ নির্ভর করে ব্যক্তির জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব পূরণের ওপর। জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান মানের উদ্দেশ্যে রচিত পুনর্গঠিত অর্থনীতিই হবে আমূল গণতন্ত্রের ভিত্তি (র্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাসি)।
এই নতুন সমাজের অর্থনীতির ভিত্তি হবে মানুষের ব্যবহারের জন্য উৎপাদন ও প্রয়োজন অনুসারে তা বণ্টন৷[mfn]১৮শ সূত্র দ্রষ্টব্য। বর্তমানের মত কেবল বাজারে বিক্রী করে মাত্র লাভের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন হবে না; অর্থাৎ প্রত্যেক কর্মক্ষম মানুষের জীবিকার্জনের জন্য কাজ দিয়ে তাদের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকবে। (অনুবাদক)[/mfn]
এই সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনে ব্যক্তির সার্বভৌম ক্ষমতা- হস্তান্তরের ব্যবস্থা থাকবে না। কারণ তাতে জনগণকে সবপ্রকার কার্যকরী ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত কবা হয়। স্থানীয় গণ-সভা সমূহের নাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালন কার্যে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণেব ব্যবস্থাই হবে এই নতুন সমাজেব রাষ্ট্রীয় ভিত্তি।
জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিদ্যা চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা এবং বিজ্ঞান ও অন্যান্য সৃজনমূলক কাজে উৎসাহ দানই হবে এই নতুন সমাজের সাংস্কৃতিক ভিত্তি।
যে হেতু এই নতুন সমাজ যুক্তিবাদ ও জ্ঞানের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে সেই হেতু এই সমাজের সব কিছু সুপরিকল্পিতই হবে। কিন্তু এই পূর্ব-পরিকল্পনাতেও মানুষের স্বাধীনতা যাতে সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখা হবে। এই নতুন সমাজ রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সব দিক দিয়েই গণতান্ত্রিক হবে এই গণতন্ত্র প্রত্যেকটি মানুষের প্রত্যক্ষীভূত বাস্তব গণতন্ত্র হবে এবং স্বকীয় শাসনের মধুস্বাদ ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্বারাই পেতে থাকবে সেই হেতু আপৎকালে প্রত্যেকটি মানুষই এই গণতন্ত্র রক্ষার জন্য লড়বে এবং রক্ষা করতেও সমর্থ হবে।[mfn]প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র সমূহের দুর্বলতার জন্যই কমিউনিষ্ট ও ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্রকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। এখানে সেই দুর্বলতা খণ্ডনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। (অনুবাদক)[/mfn]

এই আমূল গণতন্ত্রের ( র্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাসি ) আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হবে এক নতুন মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মুক্তবুদ্ধি নর-নারীর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায়। তারা জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়ে নিয়ে তাদের ভাবী শাসক হবার উদ্দেশ্যে কাজ করবে না; তারা হবে তাদের বন্ধু, উপদেষ্টা ও পথ প্রদর্শক মাত্র। যে হেতু তাদের উদ্দেশ্য প্রত্যেকটি মানুষের মুক্তি আনা, সেই হেতু এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে তাদের আচরণ হবে যুক্তি ও নীতিসম্মত জনসাধারণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যতই বাড়বে তাদের প্রচেষ্টাও ততই শক্তিশালী হয়ে উঠবে। অবশেষে শিক্ষিত ও মার্জিত জনমতের সমর্থনে ও সুবিবেচনার সঙ্গে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানের (action of the people) দ্বারা গড়ে উঠবে র্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্র। ক্ষমতা যদি কতিপয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় তা হলে জনসাধারণের মুক্তিও দূরে সরে যায়; র্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্টদের এই বিশ্বাসের জন্য তারা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবে না।
তারা স্থানীয় গণসভা সমূহে জনগণকে সংগঠিত করে তুলবে এবং কালক্রমে এইসব গণ-সভাই গণতান্ত্রিক সার্বভৌম ক্ষমতার এক একটি যন্ত্র হয়ে উঠবে। যেহেতু র্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্র সমাজের সকল মানুষের প্রত্যক্ষ সমবায়ে গড়ে উঠবে তখন রাষ্ট্র ও সমাজ সমার্থক শব্দ হবে বা উভয়েই একাত্ম হয়ে যাবে, এবং যেহেতু তখন শাসিত জনগণ ও শাসক রাষ্ট্রের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না, সেই হেতু তখন বাষ্ট্র আর দমন-পীড়নের যন্ত্র থাকবে না। কেবল তখনই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনগণের উপাদানে (of) গঠিত এবং জনগণের দ্বারাই (by) পরিচালিত হওয়া সম্ভব হবে।
শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব ও খণ্ডিত না করে সমগ্র সমাজের প্রগতি ও প্রাচুর্যের জন্য সমাজকে পুনর্গঠিত করা একমাত্র গণশিক্ষার দ্বারাই সম্ভব। স্থানীয় গণসভাগুলি হবে জনগণের রাজনীতি ও সমাজনীতি শিক্ষার বিদ্যাপীঠ। এই র্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যপ্রণালী এমনই হবে যে যার ফলে স্বার্থশূন্য অনাসক্ত মানুষদের সমাজের পুরোভাগে আনবার সুযোগ করে দেবে। এরূপ মানুষদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র তখন আর বিশালকায় ভয়ঙ্কর জন্তু লেভিয়াথানের মত সন্দেহ ও ভয়ের বস্তু থাকবে না।[mfn] একনায়কতন্ত্রের দ্বারা জোর করে ওপর থেকে জনসাধারণের ওপর ভাল ব্যবস্থা চাপিয়ে দিলেই ভাল হয় না, কারণ মূল্য-value জোর করে সৃষ্টি করা যায় না। তা শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। (অনুবাদক)[/mfn]
মানুষ চিন্তাশীল জীব; এই চিন্তাশীলতার জন্যই মানুষ এই পৃথিবীকে নিত্য নতুন ভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে, এবং এই চিন্তা কার্য মানুষ ব্যক্তিগত ভাবেই করতে পারে, সমষ্টিগত ভাবে পারে না। বৈপ্লবিক ও মুক্তিকামী সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের কর্তব্য হল, এই ঐতিহাসিক সত্যটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া। মানুষের মস্তিষ্ক একটি উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ এবং তাতে উৎপন্ন হয় সব চেয়ে বড় বৈপ্লবিক জিনিষ। সকল বিপ্লবেরই মূলে আছে পুরাতনের পরিবর্তে নতুন গড়ে তোলার জন্য সৃজনাত্মক চিন্তা। নিজেদের সৃজনীশক্তি সম্বন্ধে সচেতন, নতুন সমাজ গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দুঃসাহসিক ভাব ও ভাবনায় অনুপ্রাণিত এবং মুক্ত মানুষের সহযোগিতায় সৃষ্ট এক মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠবে এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ। নিষ্কাম মুক্তবুদ্ধি মানুষরা যখন সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসন কার্যে ব্রতী হবেন একমাত্র তখনই মানুষের দাসত্ব শৃঙ্খল চূর্ণ হয়ে সকলের জন্য মুক্তি আসবে।